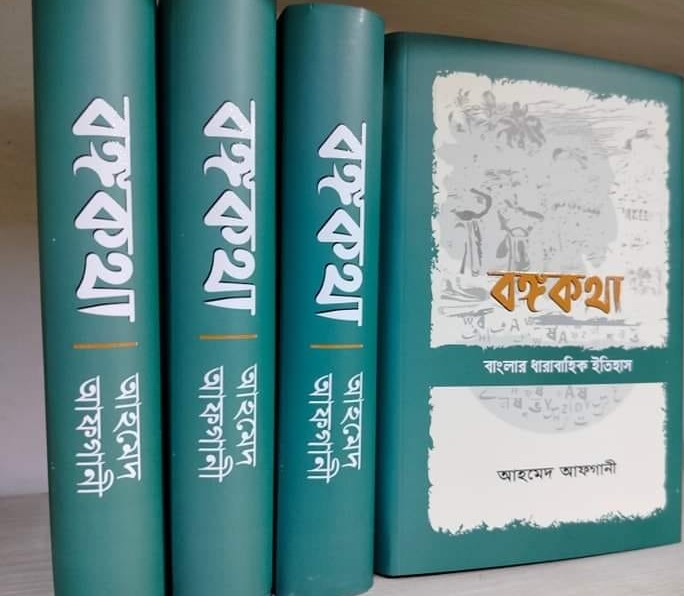মক্কা :
উসমান ইবনু আফফানের শাহাদাতবরণের সময় খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস রা. ছিলেন মক্কার গভর্নর। তিনি উসমান রা.-এর রক্তের বদলা নিতে আলী রা. বিরুদ্ধে গণজমায়েত তৈরি করেছিলেন। আলি রা. তাঁকে প্রত্যাহার করে আবু কাতাদা আনসারি রা.-কে মক্কার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। তবে তাঁর গভর্নরির মেয়াদ ছিল সংক্ষিপ্ত। কারণ, আলি রা. যখন দারুল খিলাফত তথা রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন, তখন কুসাম ইবনু আব্বাস রা.-কে মক্কার গভর্নর বানানো হয় এবং আবু কাতাদা আনসারি রা.-কে প্রত্যাহার করে সেনা কমান্ডার করা হয়। কুসাম রা.-এর সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা সামনে আসেনি। আলি রা. তাঁকে একই সময়ে মক্কার পাশাপাশি তায়েফেরও দায়িত্ব অর্পণ করেন।
৩৯ হিজরিতে মুআবিয়া রা. সিরীয় নেতাদের একজনকে সিরিয়ার হাজিদের সঙ্গে পাঠান। তাঁকে নির্দেশ দেন মক্কায় পৌঁছে সকলের নেতৃত্ব দিতে। তিনি মক্কায় পৌঁছালে তাঁর এবং কুসাম ইবনু আব্বাস রা.-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ব্যাপারটি এতদূর গড়ায় যে, কিছু সাহাবি যদি এতে হস্তক্ষেপ করে মীমাংসা করে না দিতেন তাহলে যুদ্ধ বেধে যেত। বুসরা ইবনু আরতাআহ রা.-এর নেতৃত্বে মুআবিয়া রা.-এর বাহিনী মক্কায় অভিযান পরিচালনা করে। কুসাম রা. যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পিছু হটেন। এভাবে সমাপ্তি ঘটে কুসাম রা.-এর গভর্নরির। মক্কার কর্তৃত্ব আলী রা.-এর হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর মক্কা পুনরুদ্ধারে আলী রা. তাঁর বাহিনী পাঠান। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।
মদিনা মুনাওয়ারা :
নববি যুগ এবং তাঁর পরবর্তী তিন খলিফার শাসনামলে মদিনা ছিল ইসলামি সালতানাতের দারুল খিলাফাহ তথা রাজধানী। খলিফা এখানেই অবস্থান করতেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রের সব কাজ নিজেই সামাল দিতেন। কোথাও সফরে গেলে কাউকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করে যেতেন, যিনি সার্বিক অবস্থা দেখভাল করতেন; কিন্তু আলী রা.-এর শাসনামলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা—বিশেষত তালহা, জুবায়ের ও আয়েশা সিদ্দিকার উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে ইরাকগমন—আলী রা.-কে ইরাকে দারুল খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে।
আলী রা. মদিনা ছাড়ার সময় সাহল ইবনু হুনাইফ আনসারি রা.-কে এখানে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করে যান। এখানে তাঁর গভর্নরির মেয়াদ এক বছরের কিছু বেশি ছিল বলে ধারণা করা হয়। এরপর তাঁকে অপসারণ করে তাম্মাম ইবনু আব্বাস রা.-কে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর তাঁকেও অপসারণ করে আবু আইয়ুব আনসারি রা.-কে গভর্নর বানানো হয়। আবু আইয়ুব আনসারি ৪০ হিজরি পর্যন্ত মদিনার গভর্নর ছিলেন। বুসর ইবনু আরতাআহ রা.-এর নেতৃত্বে মুআবিয়ার সিরীয় বাহিনী আক্রমণ করলে আবু আইয়ুব আনসারি মদিনা ছেড়ে কুফায় কাছে চলে যান। এভাবে মদিনাও আলীর শাসনক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যায়।
বাহরাইন ও আম্মান :
উসমান রা. শাহাদাতের সময় বাহরাইন ছিল বসরার ইমারতের অধীনে। ইবনু আমির রা. সেখানে তাঁর কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে কাউকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করতেন। আলী রা.-এর শাসনকাল এলে তিনি বাহরাইনে কয়েকজন আমির নিযুক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন উমর ইবনু আবি সালামা রা.। যিনি মদিনা থেকে ইরাক সফরের সময় আলির সঙ্গে ছিলেন। আলি সেখানে পৌঁছে তাঁকে গভর্নর হিসেবে কিছুদিনের জন্য বাহরাইন পাঠান। এরপর নিজের কাছে রাখার জন্য তাঁকে ইরাকে ডেকে আনেন।
আলী রা.-এর পক্ষ থেকে বাহরাইনে নিযুক্ত অন্য গভর্নরদের মধ্যে রয়েছেন কুদামা ইবনু আজলান আনসারি, নুমান ইবনু আজলান আনসারি ও উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.। উল্লেখ্য যে, উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. প্রকৃতপক্ষে ইয়ামেনের গভর্নর ছিলেন। এখানে তাঁর গভর্নরির দায়িত্ব পালনকালে সম্ভবত বাহরাইন, আম্মান ও নাজদ ইয়ামেনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।
ইয়েমেন :
আলী রা. খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার পর ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে দায়িত্ব দেন। উবায়দুল্লাহ তখনো ইয়ামেনে পৌঁছুতে পারেননি, এমন সময়ে উসমানের গভর্নরও সেখান থেকে বের হয়ে যান। তাঁরা তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ ও জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইয়ামেনের রাজধানী সানআয় পৌঁছে উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস গভর্নরের দায়িত্ব সামাল দেন। ইয়ামেনের সেনা-অধিনায়ক সায়িদ ইবনু সাআদ ইবনু উবাদা আনসারি রা. সহযোগী হিসেবে তাঁকে সঙ্গ দেন। উসমানের শাহাদাতে ইয়ামেনের অধিবাসীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও শোক দানা বাঁধে। হত্যাকারীদের এহেন অন্যায় তাঁদের জন্য ছিল কষ্টদায়ক। এ কারণে এখানকার কিছু লোক আলী রা.-এর খিলাফতে বায়আত করেনি। তারা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ চাচ্ছিল।
যখন তারা আলির বিচার-কার্যক্রমে বিলম্ব দেখতে পাচ্ছিল, তখন সে-সকল লোক মুআবিয়া রা. সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু করে দিলো। এর জবাবে মুআবিয়া বুসর ইবনু আরতাআহকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাঠান। পরে ইয়ামেনের অভ্যন্তরের বিদ্রোহীদের সাহায্যে বুসর ইয়ামেনের ওপর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পান। তবে এই নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব অল্প সময়ের জন্য। এর কিছুদিন পর আলী রা. মুআবিয়া রা. নিয়ন্ত্রণ থেকে ইয়ামেন মুক্ত করতে সক্ষম হন। উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে পুনরায় গভর্নর হিসেবে সেখানে পাঠান। এরপর আলী রা.-এর শাহাদাতের পূর্বপর্যন্ত তিনি সেখানে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করে যান।
সিরিয়া
মুআবিয়া রা. উমর রা. ও উসমান রা.-এর সময় হতে সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। আলী রা. যখন খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হলেন তখন তিনি উসমান রা.-এর হত্যার বদলা না নেওয়া বাইয়াত নিতে অস্বীকার করলেন। আলী রা. তাকে পত্র লিখলেন। কিন্তু সেগুলো কোনটাই কাজে আসেনি। বরং মুয়াবিয়া রা. আলী রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করলেন। উটের যুদ্ধের আগে আলী রা. সিরিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়িশা রা. বসরায় দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করায় আলী রা. সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বসরায় গেলেন। উটের যুদ্ধের পর মুয়াবিয়া রা.-কে বরখাস্ত করে তাঁর পরিবর্তে আবদুল্লাহ ইবনু উমরকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. সিরিয়ার গভর্নর-পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ও শ্বশুরালয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করে অপারগতা প্রকাশ করেন। আলী রা.-ও জোর না করে তাঁর অপারগতার বিষয়টি মেনে নেন।
আলী রা.-এর গোটা খিলাফতকালে মুআবিয়াই ছিলেন সিরিয়ার শাসক। আলী রা. কোনোভাবেই সিরিয়া তাঁর থেকে মুক্ত করতে কিংবা কোনো গভর্নর সেখানে নিযুক্ত করতে পারেননি। সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় সীমানায় উভয়পক্ষের বাহিনীর মধ্যে বেশকিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ৩৭ হিজরিতে সংঘটিত আলী ও মুআবিয়ার মধ্যকার সিফফিনযুদ্ধ।
জাজিরা
উসমান রা.-এর খিলাফতকালে জাজিরা সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ছিল। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের পর যখন সিরিয়া মুআবিয়ার কর্তৃত্বে এবং ইরাক আলির কর্তৃত্বে চলে গেল, তখন মধ্যখানে থাকা জাজিরা হয়ে গেল উভয় পক্ষের বিরোধপূর্ণ স্থান। কারণ, ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাজিরার এক প্রান্তে ছিল সিরিয়া অপর প্রান্তে ইরাক। ফলে উভয় পক্ষের জন্য জাজিরার নিয়ন্ত্রণ ছিল বাহ্যত সহজ। সেটার নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে উভয় দলের সেনাদের মধ্যেই বেশ কয়েক বার তুমুল যুদ্ধও সংঘটিত হয়। আলী রা. সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং আশতার নাখয়িকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।
আশতারই এখানকার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গভর্নর। কারণ, আলী রা. তাঁকে কয়েক বার সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি জাজিরার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে ৩৮ হিজরিতে আলী তাঁকে মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব দেন। এরপর জাজিরায় আবারও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুআবিয়ার অনুসারীরা জাজিরার নিয়ন্ত্রণের জন্য তৎপর হয়ে উঠলে উভয় দলের মাঝে বেশকিছু যুদ্ধও সংঘটিত হয়। ৩৯ হিজরির শেষ দিকে মুআবিয়া রা. একটি সীমানা পর্যন্ত জাজিরায় কর্তৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হন। আলী রা. অভিযান চালিয়ে সেখানে আবারো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
যারা আলী ও মুআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইতেন, তারাও জাজিরায় আশ্রয় নিতেন। তাঁরা ছিলেন সে-সকল লোক, যাঁরা উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে আলীর নিকট বায়আত গ্রহণ করেননি। যেহেতু জায়গাটি উভয় পক্ষের মধ্যখানে অবস্থিত, তাই তাঁরা জাজিরাকেই আবাসস্থল হিসেবে মনোনীত করেন। কতেক বর্ণনায় জাজিরায় নিযুক্ত আলির দুজন গভর্নরের নাম রয়েছে। তাঁরা হলেন, আমির" এবং কামিল ইবনু জিয়াদ। সিরিয়া বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে তাঁরা উভয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনকি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়ে জাজিরার পক্ষ থেকে শামের ওপর আক্রমণেও তাঁরা বেশ সফল হন।
মিসর
উসমানের শাহাদাতকালে মিসরে জোরপূর্বক ক্ষমতায় ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হুজায়ফা। উসমান তাঁকে সেখানে নিয়োগ দেননি। উসমানের শাহাদাতের পর আলী রা. তাঁকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গভর্নর হিসেবে সেখানে বহাল রাখেন; কিন্তু মুআবিয়া মিসর অভিমুখে সেনা-অভিযান পরিচালনা করে মুহাম্মাদ ইবনু আবি হুজায়ফাকে গ্রেফতার করেন। এরপর তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর আলী রা. কায়েস ইবনু সাআদ আনসারিকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন।
কায়েস ইবনু সাআদ ফুসতাতে পৌঁছে মিম্বারে দাঁড়িয়ে মিসরবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি আলী রা. চিঠি পড়ে তাদের সামনে আলির পক্ষ থেকে বায়আতের দাবি করলেন। কিন্তু এই ভাষণের পর মিসরবাসী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল কায়েসের হাতে বায়আত হয়ে আলীর আনুগত্য প্রকাশ করে। আরেক দল বায়আত থেকে দূরে সরে থাকে। কায়েস ইবনু সাআদ উভয় দলের সঙ্গেই দূরদর্শী আচরণ করেন। যারা বায়আত হয়নি তাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেননি। শুধু তাই নয়, তাদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও যেসব জায়গায় তারা অবস্থান করছিল সেসব স্থানে তাদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার পাঠান। তাদের একটি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে এলে তাদেরও অনেক সম্মান জানান এবং দয়ার্দ্র আচরণ করেন।
কায়েস এই উত্তম আচরণ দ্বারা বিরোধীদের সঙ্গে যাবতীয় সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে সক্ষম হন। এতে করে মিসরে স্থিতিশীলতা ও শান্তি ফিরে আসে। তিনি মিসরকে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর ব্যবস্থাপনায় সাজিয়ে তোলেন। বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। কর ও পুলিশ বিভাগের নিয়োগকার্যও সম্পন্ন করেন। এভাবেই তিনি মিসরের শাসনব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে এবং সবার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হন।
অন্যদিকে কায়েস ইবনু সাআদের এমন অবস্থান সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুআবিয়া রা. জন্য ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কেননা, একে তো সিরিয়া হলো মিসরের নিকটবর্তী এলাকা, অন্যদিকে কায়েসের মাধ্যমে মিসরের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রভূত উন্নতি করতে সক্ষম হন তিনি। এ ছাড়া কায়েস ইবনু সাআদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার খ্যাতি তো ছিলই। তা ছাড়া মিসরীয় বাহিনীর প্রতিরোধমূলক সামরিক পদক্ষেপও মুআবিয়ার ভয়ের কারণ ছিল। এ জন্য তিনি কায়েস ইবনু সাআদকে হুমকিসংবলিত পত্র পাঠাতে থাকেন এবং পাশাপাশি তাঁকে নিজের দলে ভেড়াতে প্ররোচিত করেন। কায়েস ইবনু সাআদ এসব চিঠির এমন বুদ্ধিদীপ্ত জবাব প্রদান করতে থাকেন যাতে মুয়াবিয়া রা. তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য না করেন।
এতে কায়েসের বিরুদ্ধে প্রোপ্যাগান্ডা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আলির কয়েকজন উপদেষ্টাও এ ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত প্রোপাগান্ডা সত্য মনে করেন। ফলে আলী রা. কায়েসের কাছে চিঠি লিখলেন, ‘আমি তোমাকে আমার কাছে রাখতে চাচ্ছি। সুতরাং তোমার অনুপস্থিতিতে আরেকজনকে নিয়োগ দিয়ে আমার নিকট চলে এসো। এরপর আলি তাঁর স্থানে আশতার নাখয়িকে মিসরের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আলী রা. মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর রা.-কে মিসরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর বাকী সময় মিসরের গভর্নর ছিলেন। তাঁর সময়ে মুয়াবিয়া রা. বেশ কয়েকবার মিসরে আক্রমণ করেন। কিন্তু তা অধিকার করতে পারেন নি।
বসরা
আমিরুল মুমিনিন আলি রা. তাঁর শাসনামলে বসরার সাবেক গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনু আমির রা.-কে বরখাস্ত করেন। তিনি বসরা ছেড়ে চলে যান মক্কায়। তাঁর পরিবর্তে উসমান ইবনু হুনাইফ আনসারি রা.-কে বসরার গভর্নর হিসেবে পাঠান। উসমান ইবনু হুনাইফ সেই এলাকা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা ও দক্ষতা রাখতেন। কেননা, উমর রা. তাঁকে ভূমি জরিপ ও খারাজ উসুলের কাজে ইতিপূর্বে বসরায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। উসমান ইবনু হুনাইফ বসরার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। বসরাবাসী তখন তিন দলে বিভক্ত। একদল বায়আত হয়ে গোটা জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, আরেক দল—মদিনাবাসী কী করে, সেই ভাবনায় ছিল। আর তৃতীয় দল বায়আতকে সরাসরি অস্বীকৃতি জানাল।
উসমান ইবনু হুনাইফও বেশিদিন বসরার গভর্নর হিসেবে থাকতে পারেননি। উষ্ট্রের যুদ্ধের আগে তালহা, জুবায়ের ও আয়েশা সিদ্দিকার সৈন্যবাহিনী বসরায় প্রবেশ করে। পরিস্থিতি বিবর্তিত হতে হতে একপর্যায়ে যা যুদ্ধে গিয়ে পৌঁছায়। উসমান ইবনু হুনাইফও চলে আসেন আলীর কাছে। উষ্ট্রের যুদ্ধের কদিন পূর্বেই বসরার পথে আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এভাবে শেষ হয় উসমান ইবনু হুনাইফের শাসনকাল। আলি রা. এ সময় বসরায় প্রবেশ করে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। উটের যুদ্ধের পর তিনি বসরা ত্যাগের মনস্থ করলে বিখ্যাত তাফসীরকারক আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তাঁর সঙ্গে জিয়াদ ইবনু আবিহের হাতে খারাজ বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আলী রা. জিয়াদ ইবনু আবিহের কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ব্যাপারটি জানতেন। তাই ইবনু আব্বাসকে বলেন, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেন।
কুফা
উসমান রা.-এর শাহাদাতের সময় আবু মুসা আশআরি রা. তাঁর পক্ষ থেকে কুফার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আলী রা. খলিফার পদে আসীন হলে তাঁকে সে পদেই বহাল রাখা হয়। তিনি আলির পক্ষ থেকে কুফাবাসীর কাছে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন এবং বায়আতের ব্যাপারে তাদের অবস্থান ও অধিকাংশের বায়আত কবুলের কথা জানিয়ে চিঠি পাঠান। আলি রা. ইরাকের উদ্দেশে মদিনাত্যাগের সময় আবু মুসা আশআরি সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আলি তার থেকে আবু মুসা আশআরি সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে সে বলল, ‘যদি আপনি সন্ধি ও মীমাংসা চান, তাহলে আবু মুসা আপনাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবেন।
আর আপনি যদি যুদ্ধ করতে চান, তাহলে এ ব্যাপারে তিনি উপযুক্ত নন। এ কথা শুনে আলি বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমি তো কেবল সংশোধন চাই— যদি না কেউ আমাদের পথ আগলে না রাখে। শান্তি স্থাপন, সন্ধি এবং মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধে না জড়ানোর প্রতি আবু মুসা আশআরির অভিরুচি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর হলে কুফার গভর্নরের পদ বিলুপ্ত হয়। আলী রা. নিজেই কুফার শাসক ছিলেন।
পারস্য
আলি রা. সাহল ইবনু হুনাইফ আনসারি রা.-কে পারস্যের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। একটি মেয়াদ তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন; কিন্তু এমন একটা সময় এলো যে, পারস্যবাসী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। তারা ৩৭ হিজরির দিকে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়। আলি এই পরিস্থিতি দেখে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পারস্য ইস্যুতে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করে তাঁর অন্যতম সহযোগী জিয়াদ ইবনু আবি সুফিয়ানকে সেখানকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, কেন্দ্রীয় রাজ্য বসরা এবং তাঁর অধীনস্থ রাজ্য পারস্যের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া ইস্পাহানের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এটি পারস্যের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। মুহাম্মাদ ইবনু সালিম ছিলেন এ অঞ্চলে আলীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসক। তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইস্পাহানের আরও একজন প্রসিদ্ধ শাসক হলেন উমর ইবনু সালামা। তিনি ইস্পাহান থেকে প্রচুর খাদ্য ও সম্পদ খিলাফতের রাজধানীতে নিয়ে আসেন। ২৯ হিজরিতে আলির শাসনামলে পারস্যের এই এলাকায় দিরহামের প্রচলন শুরু হয়। ইরাকের মিউজিয়ামে আরবিভাষ্য খুদাই করা সেই দিরহাম এখনো সংরক্ষিত আছে।
খোরাসান
খোরাসান ছিল পারস্যের একটি রাজ্য। খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনকালে খোরাসান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বসরার সঙ্গে কেন্দ্রীভূত ছিল। আলী রা.-এর খিলাফতকালে গভর্নর ও প্রশাসনিক বিষয়সহ এখানে সংঘটিত হয় বেশকিছু ঘটনা। এ ছাড়া কয়েকজন গভর্নর ও শহরের আমিরের নামও পাওয়া যায়। আবদুর রহমান ইবনু আবজা ছিলেন আলীর পক্ষ থেকে খোরাসানের প্রথম গভর্নর। এ ছাড়াও জাদাহ ইবনু হুবাইরা ইবনু আবি ওয়াহহাবও খোরাসানের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আলী ৩৭ হিজরিতে সিফফিন থেকে ফেরার পর তাঁকে খোরাসানের গভর্নর বানিয়ে পাঠান।
আজারবাইজান
উসমানের শাহাদাতের সময় আশআস ইবনু কায়েস রা. ছিলেন আজারবাইজানের গভর্নর। তিনি ভালো যোদ্ধা ছিলেন। আলী রা. যুদ্ধের প্রয়োজনে আশআস ইবনু কায়েসকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তিনি কুফায় এসে আলীর সঙ্গে মিলিত হন। সিফফিনযুদ্ধ এবং খারেজি দমন- অভিযানসহ বিভিন্ন ঘটনায় তিনি আলীর সঙ্গে ছিলেন। এ সময় তিনি সায়িদ ইবনু সারিয়া খুজায়িকে আজারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত করেন আলী রা.। এরপর পুনরায় আশআসকে আজারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত করে আর্মেনিয়াকেও তাঁর অধীন করে দেন। আজারবাইজানের গভর্নর থাকাকালে আশআস ইবনু কায়েস সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। এর মধ্যে একটি হলো, তিনি আরদাবিলায় আরবদের জন্য বসতি স্থাপন এবং এটিকে মুসলিম নগরীতে রূপান্তর করেন। ইসলামের প্রসারের পর সেখানে নির্মাণ করা হয় বিশাল মসজিদ।
আলী রা.-এর ৫ বছরের শাসনামল প্রায় পুরোটায় গৃহযুদ্ধে কেটে গেছে। তাই এসময় নতুন অঞ্চল বিজয় করা সম্ভব হয়নি।