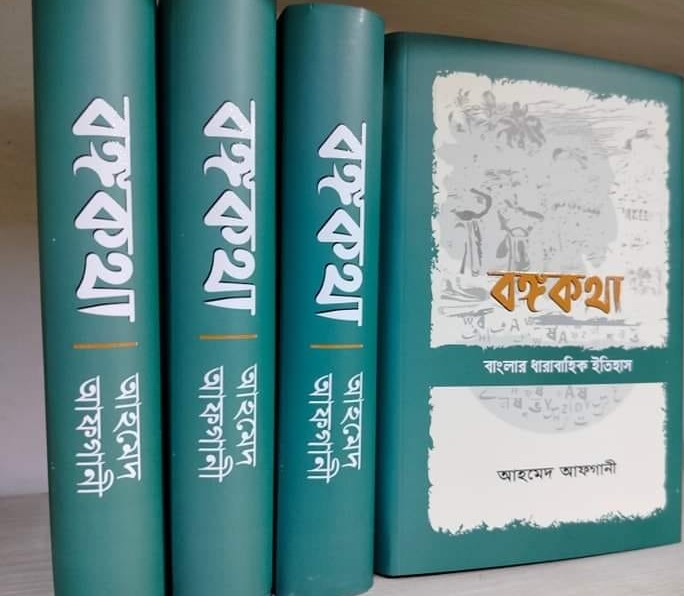১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও অনেক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে ১৫ দল থেকে পাঁচটি বামদল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জাতীয় পার্টি ১৫৩ আসনে, আওয়ামী লীগ ৭৬ আসনে ও জামায়াত ১০ আসনে বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনে এরশাদ ঢালাওভাবে ডাকাতি না করে জেনারেল জিয়াকে অনুসরণ করেছিলেন। কোন কোন আসন জাতীয় পার্টিকে জয়ী করা হবে তা আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে। জামায়াতের রংপুরের এক প্রার্থী শাহ রুহুল ইসলামকে জোরপূর্বক হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই আসনের সকল ব্যালট বাক্স সেনাবাহিনী সেনানিবাসে নিয়ে এসে ফলাফল ঘোষণা দেয়।
জামায়াত নির্বাচনে সন্তুষ্ট না হলেও রাজনৈতিক টার্গেট পূরণ হয়। পার্লামেন্টারিয়ান দলে পরিণত হয়। মার্কা হিসেবে দাড়িপাল্লাও বৈধতা পায়। নির্বাচনের শুরুতে এই নিয়ে ঝামেলা হয়। এটা সুপ্রিম কোর্টের প্রতীক হিসেবে জামায়াতকে পাল্লা মার্কার বরাদ্দ দিতে চায়নি নির্বাচন কমিশন। পরে ১৯৭০ এর নির্বাচনের নথিপত্র দেখিয়ে এই বৈধতা অর্জন করে।
১৯৮৭ সালে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আবার যুগপৎ আন্দোলন গড়ে উঠে। '৮৬ এর সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় তারাই এ আন্দোলনে অধিকতর সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দলগুলো সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে সংসদ থেকে গণ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ৬ই ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ সদস্য- বিশিষ্ট সংসদীয় দল তাদের নেতা অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের নেতৃত্বে স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর নিকট যেয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।
আওয়ামী লীগ বিবিসি'কে পদত্যাগ করবেন বলে জানানো সত্ত্বেও বিদেশে অবস্থানকারী নেত্রীর সম্মতির অভাবে দোদুল্যমান থাকা অবস্থায় তিন দিন পর সরকার সংসদ ভেঙ্গে দেয়। আওয়ামী লীগ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়। এরশাদ সরকার সংসদ ভেঙ্গে দেয়।
প্রধান দুই দলের সমন্বয়ের অভাবে যুগপৎ আন্দোলন জোরদার না হওয়ায় ঐ অনুকূল পরিবেশটিকেও কাজে লাগনো গেল না। ফলে এরশাদ '৮৮ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনে আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে কয়েকটি বাম দল ছাড়া যুগপৎ আন্দোলনের সকল দলই ঐ নির্বাচন বয়কট করে । প্রহসনমূলক এবং ভোটার বিহীন নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিত্বহীন সংসদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো সোচ্চার হতে থাকে। এরশাদের পদত্যাগ ও সংসদ ভেঙ্গে দেবার দাবীতে আন্দোলন ঢিমে তালে চলতে থাকে ।
১৯৮৯ সালের অক্টোবরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ জামায়াত প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারে সম্মত হয়। এবার সব বিরোধী দল কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অভিন্ন দাবীর কারণে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চাংগা হয়ে উঠে। কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুনির্দিষ্ট দাবী সর্বমহলে সহজে বোধগম্য হওয়ায় স্বৈরশাসনের অবসানের পথ সুগম হয়।
কীভাবে সরকার পরিবর্তন করা হবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দাবী উত্থাপিত হওয়ায় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার হয়। কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর দেওয়া ফর্মূলা অনুযায়ীই ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের নামে একটা রূপরেখা পেশ করা হয়। এতে বলা হয় যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত (মন্ত্রীর মর্যাদায়) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। এ নবগঠিত সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।
এবার সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন জোরদার হলো এবং জনগণ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলো। ঠিক ঐ পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। সরকারের ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে জনগণ ময়দানে নেমে এলো। সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে এরশাদ সরকারের পক্ষে ভূমিকা রাখতে অস্বীকার করলো। বাধ্য হয়ে এরশাদ ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯০) পদত্যাগ করলো।
কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলন সফল হলো। প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হাতে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হলেন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে জেনারেল এরশাদের সংলাপের সময় যদি কেয়ারটেকার সরকার দাবীটি সবাই একসাথে পেশ করতে সক্ষম হতো তাহলে স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি '৯০ সাল পর্যন্ত বিলম্বিত হতো না ।
প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল নিরপেক্ষ নির্বাচনে কোন দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনে সমস্যা দেখা দিল। ঘটনাক্রমে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ১৮টি আসনের অধিকারী জামায়াতে ইসলামীর হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' এসে পড়লো। জামায়াত ক্ষমতায় অংশীদার না হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে বিএনপি'কে সরকার গঠনে সাহায্য করলো। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন।
জুন মাসে বাজেট সেশনেই জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্যে সংসদে পেশ করার জন্য একটি বিল জমা দেন। পরে ঐ বছরই আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি পৃথকভাবে এ উদ্দেশ্যে বিল জমা দেয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বিএনপি এ বিষয়ে মোটেই গ্রাহ্য করলো না।
১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন যদি জেনারেল এরশাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হতো তাহলে নিশ্চয়ই বিএনপি ক্ষমতাসীন হতে পারতো না। বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকারেরই ফসল। ভবিষ্যতে যাতে এ পদ্ধতিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য দেশের শাসনতন্ত্রে এ বিষয়ে একটি আইনের সংযোজন করাই সবচাইতে যুক্তিসংগত। এ পদ্ধতিতেই জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নিশ্চিত হয়।
দুঃখের বিষয় খালেদা জিয়া সংসদে 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' সম্পর্কিত বিল আলোচনার সুযোগই দিতে রাজি হলো না। জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার দাবী নিয়ে ১০ বছর (১৯৮০ থেকে ১৯৯০) আন্দোলন করেছে। '৯০ সালে বিএনপিও এ আন্দোলনে শরীক ছিল। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সুবাদেই তাঁরা ক্ষমতায় গেলেন। অথচ এ পদ্ধতিটি সংসদে আলোচনা পর্যন্ত করতে দিলেন না। তাঁরা ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন করে ক্ষমতায় স্থায়ী হবার অবৈধ উদ্দেশ্য না থাকলে এমন স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারতো না।
১৯৯১ সালের আগে বাংলাদেশে ৪ টি সাধারণ নির্বাচন হয় মুজিব, জিয়া ও এরশাদের আমলে। প্রত্যেকটি নির্বাচন ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার' সিস্টেমে। ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। ২০২৫ সালে এখন যেমন বিএনপি'ই সরকার গঠন করবে এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছে তেমনি ১৯৯০ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে যাবে এমন একটি আবহ তৈরি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আওয়ামী নেতাদের কে কোন মন্ত্রী হবে তা নিয়ে দর কষাকষি তৈরি হয়। কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা জিতে গেল বিএনপি।
স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আহত নিহত হওয়া শত শত মানুষের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে খালেদা জিয়া কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি মেনে নিতে রাজি হয় নাই। তদুপরি ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে মাগুরা জেলার একটি আসনে উপনির্বাচন হয়। এটি আওয়ামী লীগের আসন ছিল। বিএনপি'র খালেদা সরকার মুজিব মডেল অনুসরণ করে একচেটিয়াভাবে সন্ত্রাসী দিয়ে সকল কেন্দ্র করে নেয়। এভাবে নির্বাচনে কেন্দ্র দখল করে নেবার পর আওয়ামী লীগ ঘোষণা করল যে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি সরকারের পরিচালনায় কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না। নতুন করে আবার শুরু হলো কেয়ারটেকার সরকারের আন্দোলন।
চলবে...