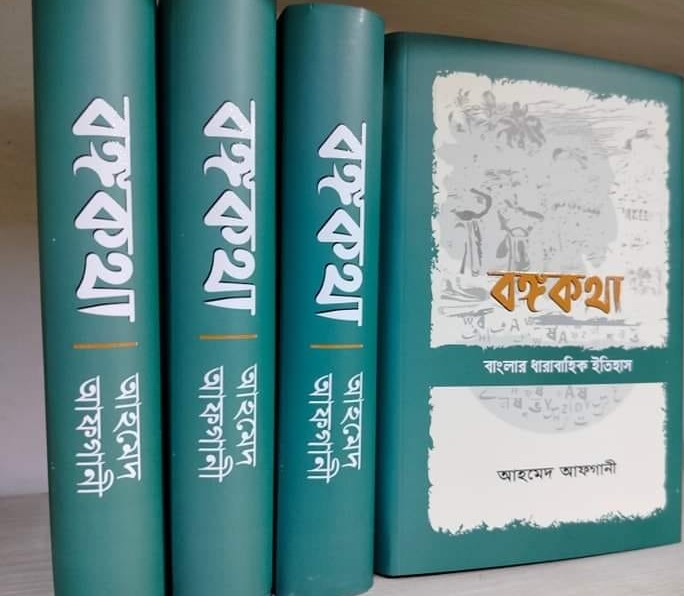১৭ মে, ২০২৫
২৩ ফেব, ২০২১
ফতওয়ার কিতাবের শেষ পাতা
৭ ফেব, ২০২১
ইসলামী ছাত্রশিবিরে আমার অভিজ্ঞতা
৩ নভে, ২০২০
হাসাসিন : এক ভয়ংকর গুপ্তহত্যাকারী বাহিনী
১১৭৬ সালের সালের কথা। অপরাজেয় সেনানায়ক সালাউদ্দিন আইয়ুবি। একের পর এক ক্রুসেডে ইউরোপিয়ানদের পরাজিত করে এবার নিজ দেশের দিকে মনযোগ দিয়েছেন। প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে মিশর থেকে সিরিয়ার পথে রওনা করলেন সালাউদ্দিন আইয়ুবি। ঝড়ের মতো ঢুকে পড়লেন সিরিয়ার আন-নুসারিয়া পার্বত্য অঞ্চলে। গোটা এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন ১৫/২০ দিনে। কিন্তু একটা দূর্গও দখল করতে পারলেন না। প্রত্যেকটা দূর্গ পাহাড়ের মাথায়, চারদিক থেকে আক্রমণ সম্ভব না, অবরোধ না করে উপায় নেই। আর ৯ টা দূর্গ আলাদা আলাদা করে অবরোধ করতে হবে। মাসিয়াফ দূর্গ অবরোধ করতে হবে আগে, খবর আছে ওদের নেতা, রাশিদ আদ-দিন সিনান মাসিয়াফেই আছে।
মাসিয়াফ দূর্গটা খুব বিশাল না, কিন্তু দুর্ভেদ্য। কারণ পেছনে খাড়াই, দুপাশে খাদ, শুধু সামনে থেকে আক্রমণ করা যাবে। চতুর্দিক আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর চারপাশে শুকনো পাতা বিছানো, শব্দ গোপন করে কারো আসার কোন সুযোগ নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন সালাউদ্দিন। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো, আচমকা। পেশাদার যোদ্ধার প্রশিক্ষিত সতর্কতা সালাউদ্দিনের। চোখ মেলেই দেখলেন, একটা ছায়ামূর্তি তাঁবুর পাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মাথার পাশে বালিশে ছুরি দিয়ে গাঁথা একটা ত্রিকোন প্রতীক, হাসাসিনদের প্রতীক, মানে ওটা বিষাক্ত ছুরি। তাতে একটা চিঠি আটকানো:
//মহামান্য খলিফা, ইচ্ছা করলেই ছুরিটা বিছানায় না গেঁথে, আরো নরম কোথাও গাঁথা যেত। কিন্তু আপনাকে বোঝানোটাই জরুরি ছিলো। আপনাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দিন, নিজেও সুস্থ থাকুন। আমরা আপনার বন্ধু না হলেও শত্রু নই। আমি নিজে না এসে অন্য কাউকেও পাঠাতে পারতাম। কিন্তু আপনার সম্মানার্থে, আমি নিজেই প্রস্তাব রেখে গেলাম। চলে যান এখান থেকে, আমাদের তরফ থেকে আপনার উপরে আর কোন হামলা হবে না।
– রাশিদ আদ-দিন সিনান, আমির-ই-হাসাসিন, সিরিয়া//
সালাউদ্দিন দুদিন পরেই মিশরের পথে ফিরতি যাত্রা করেন। ১১৭৬ সাল ছিলো ৩০০ বছরেরও বেশি আতঙ্ক সৃষ্টি করা হাসাসিনদের যৌবনকাল বলা যায়। ১১৭৩ থেকে ৩ বছরে সালাউদ্দিনকে অন্তত ৫ বার খুন করার চেষ্টা করেছিলো তারা। এই ৩০০ বছরের মধ্যে ওরা অন্তত দুই জন খলিফা, আর অসংখ্য উজির, সুলতান আর ক্রুসেড নেতাদের খুন করেছে। আর ছোটখাটো গুপ্তহত্যা তো ছিলোই। গুপ্তঘাতকের ল্যাটিন পরিভাষা, Assassin, এই হাসাসিনদের থেকেই এসেছে।
এই গুপ্তহত্যাকারী বাহিনীর শুরু ১০৭০ এর দিকে। মিশর এবং আরব তখন শিয়া ফাতিমিয় খিলাফত এবং খলিফা ছিলেন একজন ইসমাইলি শিয়া, আল-মুস্তান। পারস্য, ইরাক ও সিরিয়া তখন সুন্নী সেলজুকদের দখলে। পারস্য শাসন করছে প্রধান উজির নিজাম-উল-মুলক, চরম শিয়া বিদ্বেষী। পারস্যের (ইরান) ১৭ বছরের তরুণ স্কলার হাসান-ই-সাব্বাহ একজন ইসমাইলি শিয়া। সে ফাতিমিয় খলিফার আনুগত্য স্বীকার করলো। কয়েক বছরেই ফিদাই (সাধারণ সমর্থক) থেকে দায়িই (আদর্শ প্রচারক) তে পদোন্নতি হলো। সে শিয়া মতবাদের প্রচার করে যাচ্ছিল এবং মুসলিমদের মিশরের খলিফা আল মুস্তানের আনুগত্য করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। পারস্যের মানুষ অনেকে হাসানের অনুসারী হচ্ছিলেন। ক্রমান্বয়ে হাসানের দল ভারি হচ্ছিল। মুসলিমরা তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল।
এই অবস্থায় হাসান নিজাম-উল-মুলকের কোপানলে পড়ে গেলো। তার সমাবেশগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। শিয়াদের এরেস্ট করা হচ্ছিল। হাসানকে আটক করার জন্য তার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান চালানো হয়। পালিয়ে থেকে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছিলেন হাসান। নিজাম উল মুলক শক্তি দিয়ে হাসানের অগ্রযাত্রা থামাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইরানে যুবক হাসানের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। সরকারের বিরূপ আচরণ তাকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। এক পর্যায়ে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয় রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে। আর টিকতে পারলেন না হাসান। হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
হাসান ফাতিমিয় শাসনের কেন্দ্র কায়রোতে হিজরত করার প্ল্যান করলেন। কায়রো তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের এক বড় কেন্দ্র। তিনি ভাবলেন সেখানে জ্ঞানও অর্জন হবে, খলিফাকেও দেখা হবে। আর কায়রোর খলিফাই তো শিয়াদের ইমাম। ১০৭৬ এ রওনা দিয়েও পারস্য থেকে কায়রো যেতে দুই বছরের বেশি লেগে গেলো হাসানের। কারণ পথে যতগুলো বড় শহর পড়েছে সবখানেই কিছুদিন থেকে মানুষের চিন্তাভাবনা, পলিটিকাল ধারণা, ধর্মীয় নেতাদের ভাবনা, এগুলো স্টাডি করছিলো হাসান। অবশেষে হাসান যখন ১০৭৮ এ কায়রো পৌঁছালো, সেখানে তখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চলছে। মুস্তানের বড় ছেলে নাজির, স্বাভাবিকভাবেই পিতার মৃত্যুর পরে তার খলিফা হবার কথা। কিন্তু প্রধান সেনাপতি বদর আল-জামালির ইচ্ছা পুরোই ভিন্ন কিছু।
হাসানের খবর সবাই আগেই জানতো। তার পাণ্ডিত্যের সাথে শিয়ারা আগেই পরিচিত ছিল। তাই মিশরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলো হাসান। কিন্তু মিশরেও ভালো অবস্থান হয়নি হাসানের। খলিফা আল মুস্তানের ছেলে নাজিরকে সমর্থন দেওয়ার কারণে সেনাপতি বদর তাকে এরেস্ট করলো। নিজাম উল মুলকের আসামীকে তার হাতে তুলে দিয়ে সেনাপতি বদর নিজামের সাথে সুসম্পর্ক করতে চেয়েছে। যাতে পরবর্তীতে শাসক হতে পারলে নিজামের সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো থাকে। হাসানকে বন্দী হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে পারস্যের জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া হলো।
জাহাজ যখন দামাস্কাস বন্দরের কাছাকাছি তখন ঝড়ে পড়ে জাহাজ বিদ্ধস্ত হয় এবং হাসান সিরিয়ার কোন এক উপকূলে ভেসে যায়। সিরিয়ায় নিজেকে মুক্ত অবস্থায় পায় হাসান। আগে হাসান চেষ্টা করেছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভালো পণ্ডিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারলো, শক্তি না থাকলে জ্ঞান-বিজ্ঞান কাজে আসছে না। হাসান নিজের জীবন বিপন্ন দেখে নতুন সিদ্ধান্ত নিল। পরের ১০ বছরে হাসানের একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, শিয়াদের মধ্যে যারা তার অনুসারী তাদের সংগঠিত করা এবং একটি দক্ষ ও দুর্দান্ত সেনাবাহিনী তৈরি করা। সিরিয়া পারস্য আর ইরাকের সমস্ত এলাকা ঘুরে ডেডিকেটেড লোকদের নিয়ে বড় আকারে হাসাসিন (কোড অফ হাসান) নামে একটা বাহিনী তৈরি করে এবং তাদেরকে যোগ্যতা অনুসারে তিনটে ইউনিটে ভাগ করে।
১) দায়ি (প্রচারক)
২) রফিক (সঙ্গী)
৩) লাসিক (অনুগত নির্বাহক)।
এবার নিজাম উল মুলকের টনক নড়েছে, তার মাথা খারাপ হবার দশা। একা হাসানই যথেষ্ট মাথা ব্যাথার কারণ ছিলো ১২ বছর আগে, এবারে সে দলবল নিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সেনাবাহিনী পাঠায় নিজাম, হাসানকে দলবলসহ চিরতরে বিনাশ করতে। হাসান তার দল নিয়ে আল বুর্জ পার্বত্য অঞ্চলের এত গভীরে ঢুকে যায়, যে গোটা পারস্য ফোর্স দিয়েও হয়তো ওদের খুঁজে বের করা সম্ভব না। ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকা অবস্থায় হাসান ভাবতে থাকে, নিজেদের একটা শক্তিশালী আস্তানা দরকার, যেখান থেকে নিজেদের কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা যাবে। তার মনে পড়ে বেশ কিছুদিন আগে দেখা, আলামুত নামে একটা পার্বত্য দূর্গের কথা।
তৎকালীন পারস্যের রুদবার নামে পার্বত্য এলাকায়, পর্বতশ্রেণীর মাঝে ৫০ কিলোমিটার লম্বা ও ৫ কিলোমিটার চওড়া একটা উপত্যকার মাথায় অবস্থিত আলামুত দূর্গ, প্রাকৃতিক সুরক্ষায় সুরক্ষিত। জানা যায়, প্রায় বিনা রক্তপাতে দখল করেছিলো আলামুত। প্রথমে ঐ এলাকায় দাইই এবং রফিকদের পাঠানো হয়, যারা আলামুত উপত্যকার সাধারণ মানুষের মন জয় করে তাদের ইসমাইলি আদর্শে দীক্ষিত করে। এরপরে ১০৯০ এর দিকে সাধারণের সাথে ভিড়িয়ে দেয়া হয় লাসিকদের এবং লাসিকরা দূর্গে অনুপ্রবেশ করেই দূর্গাধিপতি এবং তার কাছের লোকজনকে জিম্মি করে ফেলে। ফলাফল, প্রায় বিনা রক্তপাতে দূর্গ দখল। এরপরে আরো ৩৫ বছর জীবিত ছিলো হাসান-ই-সাব্বাহ, কিন্তু একদিনের জন্যেও আলামুত ছেড়ে বের হয় নি। ব্যস্ত ছিলো দর্শন, স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, এলকেমি, চিকিৎসা শাস্ত্র ও গণিত নিয়ে গবেষনায় এবং অবশ্যই হাসাসিনদের প্রশিক্ষন ও ইসমাইলি দর্শন প্রচার, প্রসার এবং নীতি নির্ধারণে।
হাসাসিনিদের প্রশিক্ষন শুরু হতো ১০/১২ বছর বয়স থেকে। ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচরণ এবং পাশাপাশি অস্ত্রকৌশল বিশেষ করে নাইফ ফাইটিং, ছদ্মবেশ, আত্ম নিয়ন্ত্রণ এবং সমরকৌশলের শিক্ষা দেয়া হতো। ৭/৮ বছরের মধ্যেই ওরা হয়ে উঠতো লিভিং উইপন, ফিদায়ান (আত্ম নিবেদিত যোদ্ধা)। যে কোনো মূল্যে সিভিলিয়ানদের উপরে কোন আঘাত নয়, এই ছিলো ওদের কৌশল। যে কোনো নতুন এলাকায় গেলে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে একদম মিশে যেত একজন হাসাসিন। টার্গেটের সাইকোলজি স্টাডিও ওদের কৌশলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। শোনা যায় একটা এসাসিনেশন প্রচেষ্টার শারীরিক ও মানসিক শক্তিবৃদ্ধি ও স্থিরতার জন্য শেষ ধাপের আগ মুহুর্তে ওরা হাশিশ (গাঁজা) ব্যবহার করতো। যদিও এটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা, নিশ্চিত নয়। খুন করার জন্য তারা সচরাচর বিষ মাখানো ছুরিই ব্যবহার করতো এবং খুনগুলো করা হতো সর্বসম্মুখে, যেন লোকে বোঝে এটা হাসাসিনদের কাজ। আতঙ্ক সৃষ্টি করা হাসাসিনদের রাজনৈতিক কৌশল। পারস্য এবং সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের আলাদা আলাদা এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠে ইসমাইলি রাষ্ট্র এবং পুরোটাই হাসাই-ই-সাব্বাহ'র জীবনকালে।
হাসাসিন রাষ্ট্র গঠনের প্রধান পদক্ষেপ ছিলো নিজাম-উল-মুলক'কে হত্যা এবং হত্যাকান্ড ঘটানো হয় প্রকাশ্য দরবারে। নিজাম-উল-মুলকই প্রথম হাই প্রোফাইল খুন। সেলজুকেরা প্রথম থেকেই হাসাসিনদের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালায়, ফলশ্রুতিতে ওদের অন্তত ৫ জন সুলতান খুন হয় এদের হাতে। মিশরের ফাতিমিয় খিলাফতকে উচ্ছেদ করার পরে সুন্নি খলিফারা ইসমাইলিদের উপরে অত্যাচার শুরু করে, সে সময় অন্তত দুই জন খলিফা খুন হয় হাসাসিনদের হাতে। গ্রান্ড মাস্টার রাশিদ আদ-দিন সিনানের সময়ে হাসাসিন এবং ইসমাইলিদের কমন শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ক্রুসেডাররা। শোনা যায়, কিং রিচার্ডের সাথেও একটা সময় সন্ধি চুক্তি হয় রাশিদের। রাশিদের মধ্যস্ততায়ই সালাউদ্দিন ও রিচার্ড সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে।
সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ারও হাসাসিনদের পছন্দের কৌশল ছিলো, খুন করার ঝামেলায় না গিয়ে ভয় দেখিয়ে সাবমিশনে বাধ্য করা। সেলজুক সুলতান মোহাম্মদ তাপারকে খুন করার পরে ওর ছেলে আহমেদ সাঞ্জার যখন সুলতান। সে হাসাসিন দূতকে তার দরবার থেকে চাবুক মেরে বের করে দেয়। পরে সাঞ্জারকে সালাউদ্দিন আইয়ুবির মতো ভয় দেখানো হয়। সাঞ্জার ভয় পেয়ে শুধু হাসাসিন এলাকার কর আদায় বন্ধ করেনি, ঐ এলাকার সমস্ত কর আদায়ের অধিকারও হাসাসিনদের দিয়ে দেয়। পারস্য থেকে তুরস্ক, সিরিয়া থেকে মিশর, যখনই যেখানে শিয়াদের উপরে আঘাত এসেছে, হাসাসিনরা সেখানেই অপারেট করে গেছে প্রায় দুইশ বছরেরও বেশি সময় ধরে।
১২৫০ এর দিকে হাসাসিনরা একটা মারাত্মক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে বসে। ভয়ংকর মোঙ্গল শাসক মোংকে খানকে খুন করে তারা। তার ভাই হালাকু খান ছিলো আরো বেশি ভয়ংকর। ক্ষমতায় বসেই প্রধান সেনাপতি কিতুবাকে নিযুক্ত করে হাসাসিনদের সমূলে বিনাশ করতে। ১২৫৩ থেকে কিতুবা হাসাসিনদের ৯ টা দূর্গে উপর্যুপরি হামলা চালায়। হাসাসিনরা তাদের অঞ্চলে নিরাপত্তা খুবই শক্তিশালী করে রাখে। হাসাসিনরা তাই সংখ্যায় কম হলেও কেউ তাদের দুর্গ দখলে নিতে পারেনি। মোঙ্গল সেনানায়ক কিতুবা লক্ষাধিক সৈন্য নিয়েও সুবিধা করতে পারলো না। উপরন্তু বহু সৈন্য হারাতে হয়েছে।
অবশেষে হালাকু খান স্বয়ং তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসে। সে নিজেই হাসাসিনদের দুর্গ আক্রমণের নেতৃত্ব দিতে আসে ১২৫৬ সালে। মরণপণ যুদ্ধ করার পর অবশেষে ১২৫৬ সালের ডিসেম্বরে আলামুত দূর্গ অবরোধ করে মোঙ্গলরা। হাসাসিনরা দুর্গের ভেতরে চলে যায়। প্রায় ৩/৪ মাসের অবরোধে থাকার পরে হাসাসিনরা গোপন পথে আলামুত ছেড়ে চলে যায়। এই সময় হাসাসিনদের নেতা ছিলো রুকন উদ্দিন। হালাকু খান দুর্গ দখল করে। এই প্রথম ১৬৬ বছর পর আলমুত দুর্গ হাসাসিনদের হাতছাড়া হয়ে গেল। তবে ১৯ বছর পর রুকন উদ্দিনের ছেলে শামসুদ্দিনের নেতৃত্বে ১২৭৫ সালে ফের আলামুত দখল করে হাসাসিনরা। তবে দুর্গ উদ্ধার হলেও তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কিংবা কর আদায় করার মতো পরিস্থিতিতে যেতে পারে নি। তবে তাদের মূল কাজ ছিল শিয়াদের শত্রুদের তটস্থ রাখা। সেই কাজ তারা আরো প্রায় একশ বছর চালিয়ে গেছে। এসময় তারা ভাড়াটে খুনি হিসেবে নিজেদের ব্যবহার করতো।
মামলুকরা হাসাসিনদের নিজেদের কাজে লাগাতো। শামসুদ্দিনের পর হাসাসিনরা আর কোনো ভালো নেতা না পাওয়ায় ধীরে ধীরে তাদের শক্তি খর্ব হতে থাকে। তাদের অনেকেই অপেক্ষা করতে থাকে, কবে তাদের মধ্য থেকে একজন গ্রান্ড মাস্টার উঠে আসবে এবং ফের তারা পূর্বের গৌরবে ফিরবে। এভাবেই মোটামুটি ৩০০ বছরের মধ্যেই সে যুগের সব থেকে দুধর্ষ ও আতঙ্ক জাগানিয়া হাসাসিন গোষ্ঠী ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে।
১২ মে, ২০২০
আব্দুল লতিফ নেজামী এবং নেজামে ইসলামী পার্টি
৯ ফেব, ২০২০
জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার আদ্যোপান্ত
১৫ মে, ২০১৯
নারী নির্যাতন রোধে করণীয়
জেলখানায় আলাদা আলাদা পরিভাষা ছিল প্রায় সবগুলো বিষয়ের। যেমন রান্নাঘরকে বলা হত 'চৌকা'। মামলাগুলোর নামও ছিল আলাদা আলাদা। যেমন আমাদের সংগঠনের যে কেউ ভাংচুর, বিস্ফোরক, অস্ত্র যে মামলায় এরেস্ট হোক না কেন তার মামলার নাম ছিল শিবির মামলা।
এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শাস্তি দেয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইনশাআল্লাহ।