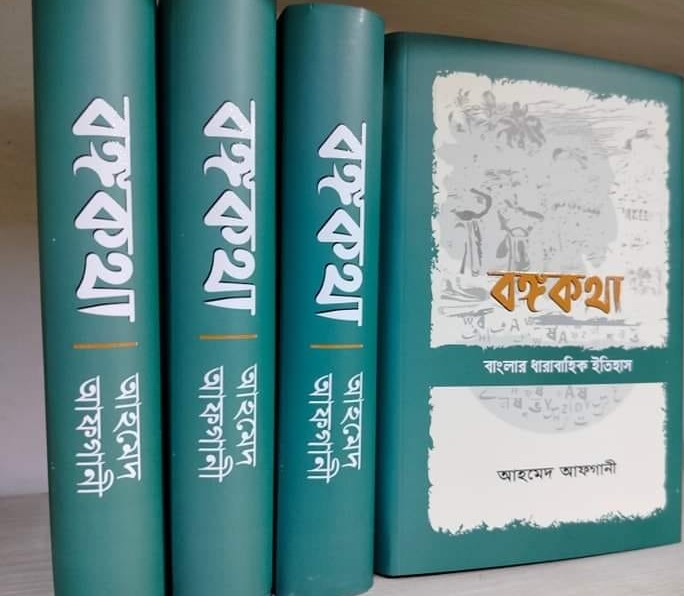মাওলানা নিজামী কেমন ছিলেন এই ব্যাপারে আমি আমার পূর্বের পোস্টে উল্লেখ করেছি। তাই এখানে কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি। ২০১২ সালের ২৮ মে মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এই জামায়াত নেতার বিচার শুরু হয়। মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে মোট ১৬টি অভিযোগ আনা হয়। এর মধ্যে ট্রাইব্যুনাল ৪টি অভিযোগে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। আপীলের রায়ে সেখান থেকে একটি অভিযোগে খালাস দিয়ে বাকী তিনটিতে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। আর্টিকেলের আকার বড় হয়ে যাওয়াতে এখানে আমরা শুধু তিনটি অভিযোগ, যে অভিযোগগুলোতে মাওলানাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে সে অভিযোগগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবো।
অভিযোগ-১: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালানোর কারণে একাত্তরের ৪ জুন পাকিস্তানি সেনারা পাবনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাওলানা কছিমুদ্দিনকে অপহরণ করে নূরপুর পাওয়ার হাউস ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিজামীর উপস্থিতিতে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। ১০ জুন তাকে ইছামতী নদীর পাড়ে আরো কয়েকজনের সঙ্গে হত্যা করা হয়।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-২: একাত্তরের ১০ মে বেলা ১১টার দিকে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বাউশগাড়ি গ্রামের রূপসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সভা হয়। স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের উপস্থিতিতে ওই সভায় নিজামী বলেন, শিগগিরই পাকিস্তানি সেনারা শান্তি রক্ষার জন্য আসবে। ওই সভার পরিকল্পনা অনুসারে পরে ১৪ মে ভোর সাড়ে ৬টার দিকে বাউশগাড়ি, ডেমরা ও রূপসী গ্রামের প্রায় সাড়ে ৪০০ মানুষকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। প্রায় ৩০-৪০ জন নারীকে সেদিন ধর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা।
রায়ঃ মৃত্যুদণ্ড
অভিযোগ-৩: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মে মাসের শুরু থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ব্যবহৃত হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প হিসাবে। রাজাকার ও আলবদর বাহিনীও সেখানে ক্যাম্প খুলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। নিজামী ওই ক্যাম্পে নিয়মিত যাতায়াত ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র করতেন বলে প্রসিকিউশনের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-৪: নিজামীর নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় রাজাকার বাহিনী পাবনার করমজা গ্রামে হাবিবুর রহমান নামে একজনকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ৮ মে নিজামীর রাজাকার ও আলবদর বাহিনী ওই গ্রাম ঘিরে ফেলে নয়জনকে হত্যা করে। রাজাকার বাহিনী একজনকে ধর্ষণসহ বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-৫: ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল বেলা ১১টার দিকে নিজামীর সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনারা পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার আড়পাড়া ও ভূতেরবাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে ২১ জন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। সেখানে বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগও করা হয়।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-৬: নিজামীর নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর পাবনার ধুলাউড়ি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে যায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের ডা. আব্দুল আউয়াল ও তার আশেপাশের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৫২ জনকে হত্যা করে।
রায়ঃ মৃত্যুদণ্ড
অভিযোগ-৭: একাত্তর সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে নিজামীর দেওয়া তথ্যে রাজাকার বাহিনীকে নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী পাবনার বৃশালিখা গ্রাম ঘিরে ফেলে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ সেলিমের বাবা সোহরাব আলীকে আটক করে। তাকে রাস্তায় নিয়ে নির্মম নির্যাতনের পর স্ত্রী ও সন্তানদের সামনেই হত্যা করা হয়।
রায়ঃ যাবজ্জীবন
অভিযোগ-৮: একাত্তরের ৩০ আগস্ট ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ও আলবদর বাহিনীর প্রধান নিজামী তার সংগঠনের তখনকার সেক্রেটারি আলী আহসান মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে নাখালপাড়ার পুরোনো এমপি হোস্টেলে যান এবং সেখানে আটক মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন বিচ্ছু জালাল, বদি, রুমি (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে), জুয়েল ও আজাদকে দেখে তাদের গালিগালাজ করেন। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনকে নিজামী বলেন, রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আদেশের আগেই তাদের হত্যা করতে হবে। নিজামীর পরামর্শ অনুযায়ী পরে জালাল ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়।
রায়ঃ যাবজ্জীবন
অভিযোগ-৯: নিজামী ও রাজাকার বাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানি বাহিনী পাবনার বৃশালিখা গ্রাম ঘিরে ফেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রফুল্ল, ভাদু, মানু, স্বস্তি প্রামানিক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাওলাদার ও পুতুলসহ ৭০ জনকে হত্যা ও ৭২টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করে।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১০: মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পাবনার সোনাতলা গ্রামের অনিল চন্দ্র কুণ্ডু নিরাপত্তার জন্য ভাই-বোনদের নিয়ে ভারতে চলে যান। পরে অগাস্টে তিনি এলাকায় ফিরে আসেন। নিজামীর নির্দেশে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা তার এবং আশেপাশের বহু মানুষের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১১: একাত্তরের ৩ অগাস্ট চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউটে ইসলামী ছাত্রসংঘের এক সভায় নিজামী বলেন, পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তিনি প্রিয় ভূমির হেফাজত করছেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না। সেদিন তার উপস্থিতিতেই নিরীহ বাঙালিদের ওপর হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য ইসলামী ছাত্র সংঘ, আলবদর, রাজাকারদের মতো সহযোগী বাহিনীগুলোকে উসকানি দেওয়া হয়।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১২: একাত্তরের ২২ অগাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক একাডেমি হলে আল মাদানীর স্মরণসভায় নিজামী বলেন, যারা পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়, তারা ইসলামের শত্রু। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে ইসলামের শত্রুরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে মন্তব্য করে পাকিস্তানের শত্রুদের নির্মূল করার আহ্বান জানান তিনি।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১৩: ওই বছর ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ইসলামী ছাত্রসংঘের সভায় নিজামী বলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডটা রক্ষায় হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতে রাজাকার, আলবদর সদস্যরা প্রস্তুত। উসকানিমূলক ওই বক্তব্যে মুক্তিকামী বাঙালিকে ভারতের সহযোগী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১৪: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১০ সেপ্টেম্বর যশোরে রাজাকারদের প্রধান কার্যালয়ে এক সুধী সমাবেশে নিজামী প্রত্যেক রাজাকারকে ইমানদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১৫: একাত্তরের মে মাস থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজাকার ক্যাম্প ছিল। নিজামী প্রায়ই ওই ক্যাম্পে গিয়ে রাজাকার সামাদ মিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়।
রায়ঃ খালাস
অভিযোগ-১৬: মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের ঊষালগ্নে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে আলবদর বাহিনী। দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে আলবদর সদস্যরা ওই গণহত্যা ঘটায়। জামায়াতের তৎকালীন ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ ও আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে ওই গণহত্যার দায় নিজামীর ওপর পড়ে।
রায়ঃ মৃত্যুদণ্ড
২ নং অভিযোগের পর্যালোচনাঃ
অভিযোগ-২: একাত্তরের ১০ মে বেলা ১১টার দিকে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বাউশগাড়ি গ্রামের রূপসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সভা হয়। স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের উপস্থিতিতে ওই সভায় নিজামী বলেন, শিগগিরই পাকিস্তানি সেনারা শান্তি রক্ষার জন্য আসবে। ওই সভার পরিকল্পনা অনুসারে পরে ১৪ মে ভোর সাড়ে ৬টার দিকে বাউশগাড়ি, ডেমরা ও রূপসী গ্রামের প্রায় সাড়ে ৪০০ মানুষকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। প্রায় ৩০-৪০ জন নারীকে সেদিন ধর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা।
এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের চারজন সাক্ষী ছিলেন। যাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মাওলানা নিজামীকে ফাঁসী দেয়া হয়। আসুন দেখি সাক্ষীদের অবস্থা কেমন ছিল।
১- রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী মোঃ আইনুল হক একাত্তরের ১৪ মে কথিত হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় মাওলানা নিজামী উপস্থিত ছিলেন- এ ধরণের কোনো বর্ণনা দেননি। তিনি ঘটনার দিন শান্তি কমিটি গঠনের বিষয়ে মাওলানা নিজামীকে জড়িয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বলেননি। তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেছেন এক কথা, কোর্টে এসে বলেছেন আরেক কথা। কাজেই মতিউর রহমান নিজামী সাহেব সম্পর্কে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।
২- রাষ্ট্রপক্ষের আরেক সাক্ষী শামসুল হক নান্নু এতো বেশি অসত্য তথ্য ট্রাইব্যুনাল এবং তার বাইরে প্রদান করেছেন তাকে বিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। উপরন্তু তার বক্তব্য যে কতটা অসাড় তার প্রমাণ হলো তার নিজের বক্তব্য- ‘২৪ মার্চ পাবনা আলিয়া মাদরাসার নিকটবর্তী দোকানদার সেকেন্দার আলীর নিকট থেকে জানতে পারি যে, ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আব্দুস সোবহান, মাওলানা ইছহাক, রফিকুন নবী ওরফে বাবলু পাবনা আলিয়া মাদরাসায় বসে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য একটি স্বাধীনতা বিরোধী সেল গঠন করে’ অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই স্বাধীনতা বিরোধী সেল গঠনের কথা তিনি বলেছেন, এটি হাস্যকর বক্তব্য। আর দুই বছর বয়সে মাওলানা নিজামীকে বোয়াইলমারী মাদরাসায় পড়তে দেখা।
৩- শামসুল হক নান্নু তার তার এক ভিডিও বক্তব্যে সে বর্ণনা করেছে সে বাধ্য হয়ে নিজামীর বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। তার ছেলেকে বিসিএস ক্যাডার বানানোর জন্য স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। সে তার ভিডিও বক্তব্যে আরো বলেছে হত্যাকাণ্ড যা হয়েছে পাকিস্তানীরা করেছে নিজামীকে আমদা দেখি নাই, তার নামও শুনি নাই। এই ব্যাপারে আমি আর বিস্তারিত বলছি না, দয়া করে তার বক্তব্য শুনুন।
৪- প্রসিকিউশনের সাক্ষী জামাল উদ্দিন-এর এই ঘটনা সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তিনি সাক্ষী মো.আইনুল হক ও শামসুল হক নান্নুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। এই দু’জনের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তাকেও বিশ্বাস করা যায় না।
৫- সাক্ষী জহুরুল হক এই মামলার তদন্ত সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রসিকিউশনের সাজানো সাক্ষী হিসেবে হাজির করায় তাকে বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তদুপরি তিনি দাবি করেন ঘটনার রাতে তিনি বাউশগাড়ি শহীদ আব্দুল জব্বারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অথচ তদন্তকারী কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক খানকে জেরা করার সময় তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন বাউশগাড়ী গ্রামে আব্দুল জব্বার নামে ঐদিন শহীদ কোনো ব্যক্তির নাম তিনি পান নাই। সাক্ষী জহুরুল হক তদন্ত কর্মকর্তার সাথে তার দেখা হওয়ার বিষয়েও মিথ্যাচার করেছেন। কারণ তার মতে ১৭ মে, ২০১৩ তারিখের আগে তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে দেখা হয় নাই, দেখা যায় তিনি মূল তদন্তের সময় ২০১০ এর ৬ নভেম্বর তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে দেখা করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা সেটা স্বীকার করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন মিথ্যাবাদী ও সাজানো সাক্ষী।
৬- আরেকজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী আযহার প্রামানিক যিনি ঐ দিন ঐ ঘটনায় আর্মীর গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে মাওলানা নিজামী সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেন। তাকে দিয়ে মিথ্যা বলাতে না পারায় শেষ পর্যন্ত তাকে কোর্টে হাজির করা হয়নি।
৬ নং অভিযোগের পর্যালোচনাঃ
অভিযোগ-৬: নিজামীর নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর পাবনার ধুলাউড়ি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে যায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের ডা. আব্দুল আউয়াল ও তার আশেপাশের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৫২ জনকে হত্যা করে।
এই অভিযোগের তিনজন সাক্ষী ছিলেন। যাদের কথার উপর ভিত্তি করে আদালত মাওলানা নিজামীকে ফাঁসীর আদেশ দেয়। আসুন তাদের সাক্ষ্যের নমুনা দেখি।
১- উক্ত চার্জের সাক্ষী মোঃ শাহজাহান আলী মাওলানা নিজামীকে জড়িয়ে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ তিনি বলেছেন, ‘১৯৭১ সালের ২৮ নবেম্বরের আগে মাওলানা নিজামীকে আমি দেখেছি, আনোয়ারুল হকের নির্বাচনী জনসভায়। নির্বাচনী জনসভা গৌরী গ্রামে হয়েছিল। গৌরী গ্রামটি সাথিয়া থানাধীন, আমার গ্রাম থেকে ৫ মাইল দূরে। এই জনসভা শুনতে আমি যাই নাই।’ তিনি যদি জনসভায় না-ই যান তবে সেই জনসভায় মাওলানা নিজামীকে কিভাবে দেখলেন? সতরাং তিনি জেরায় অসত্য তথ্য দিয়েছেন।
২- তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি টিভি চ্যানেলে অনেকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তবে তিনি দিগন্ত টি.ভি, চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন কিনা মনে করতে পারেন নাই। দু’বার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার স্মরণশক্তি কমে গিয়েছে, কখন কি বলেন তা মনে থাকে না বলে তিনি দাবি করেন। তবে তিনি সেই সাক্ষাৎকার সমূহে ‘১৯৮৬ সালের নির্বাচনের আগে মাওলানা নিজামীকে দেখেননি’ বলে বলেছিলেন সেটা অস্বীকার করেন। ডিফেন্স সেই সাক্ষাৎকার সমূহের ভিডিও সমূহ প্রদর্শন করেছে। সেখানে দেখা যায় যে, তিনি মাওলানা নিজামীকে ১৯৭১ সালে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। এই সাক্ষী শপথ করে কাঠগড়ায় এসে তার পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলায় তার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কোনো কারণ নেই।
৩- উপরন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তার স্মরণশক্তি কমে গেছে তিনি কখন কি বলেন তা মনে থাকে না। সুতরাং ৪৩ বছর আগের বিষয়ে এ ধরণের স্মৃতিশক্তিহীন ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি জেরার জবাবে বলছেন, তিনি পাবনা সাঁথিয়ার মিয়াপুর হাজী জসিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে এসএসসি পাশ করেছেন। অথচ তিনি তার জবানবন্দীতে বলেছেন, তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর ঢাকা মেডিকেলে চার বছর চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পর সর্বপ্রথম পাবনায় ১৯৭৫ সালে যান। অতএব তিনি হয় ১৯৭২ সালে পাবনার একটি স্কুল থেকে এসএসসি পাস করার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছেন অথবা চিকিৎসার জন্য ঢাকায় ৪ বছর অবস্থান শেষে ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম পাবনা যাওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছেন। সুতরাং এই স্ব-বিরোধী ও সাংঘর্ষিক বক্তব্য প্রদানকারী সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তার জবানবন্দী গ্রহণযোগ্য নয়।
৪- এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ব্যাংক ডাকাতিতে সহযোগী তার অভিযোগে সোনালী ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুত হন। তিনি এই চাকরিচ্যুতির আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করেননি। সুতরাং এই সাক্ষী অসৎ এবং তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।
৫- তিনি তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, তার সাথে যেসকল মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের মধ্যে তাকে ছাড়া তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। অথচ সাক্ষী তার জবানবন্দীতে বলেন, শাহজাহান ছাড়াও আরও একজন বেঁচে যান তার নাম মাজেদ। সাক্ষী শাহজাহান আলী পরে স্বীকার করেন যে, মাজেদ এখনও জীবিত আছেন। এই ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি অসত্য তথ্য দেয়ায় তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।
৬- উক্ত অভিযোগের আরেক সাক্ষী মোঃ খলিলুর রহমানের মাওলানা নিজামীকে জড়িয়ে দেয়া বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ তিনি বলেছেন, ২৭ নবেম্বর দিবাগত রাতে রাত সাড়ে ৩টায় চাঁদের আলোয় তিনি মাওলানা নিজামীকে দেখেছেন। অথচ ঐদিন বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী চন্দ্র অস্ত গিয়েছিল রাত ১টা ২৩ মি. ৫৪ সেকেন্ডে। সুতরাং তার চাঁদের আলোয় মাওলানা নিজামীকে দেখার বিষয়টি অসত্য।
৭- তার বক্তব্য অনুযায়ী তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে ২ জন (শাহজাহান ও মাজেদ) বাদে সকলে ঐদিন নিহত হন। পরে তিনি জেরায় বলেন, উক্ত ২ জন এবং কুদ্দুস ছাড়া তার গ্রুপের বাকী সবাই নিহত হন। পরে তিনি আবার স্বীকার করেন, উক্ত তিন জন ছাড়াও তার গ্রুপের সালাম ঐদিন বেঁচে যায়। একই সাথে তার তিন ধরণের বক্তব্য প্রদান থেকেই বুঝা যায় তিনি অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন।
৭- তিনি বলেছেন, ঘটনাস্থল ধুলাউড়ি গ্রামে তার আত্মীয় গফুর সাহেবের বাড়িতে তিনি ১৯৭১ সালে যাতায়াত করতেন। কিন্তু তিনি একই সাথে উক্ত গফুর ঐ সময় বিবাহিত নাকি অবিবাহিত ছিলেন বলতে ব্যর্থ হন। তিনি যদি ঐ সময়ে তার উক্ত আত্মীয়ের বাড়িতে সত্যই বেড়াতে যেতেন তবে তিনি অবশ্যই বলতে পারতেন উক্ত আত্মীয় ঐ সময়ে বিবাহিত না অবিবাহিত ছিলেন। সুতরাং বলা যায় ঐ সময়ে তার ঘটনাস্থলে যাতায়াতের বিষয়ে তিনি মিথ্যা বলেছেন।
৮- তিনি দাবি করেছেন যে, মাওলানা নিজামী তার পাশের গ্রামের লোক হওয়ায় এবং তার গ্রামে মাওলানা নিজামীর বোন বিয়ে দেয়ায় তিনি ১৯৭১ সালের আগে থেকেই তিনি তাকে চিনতেন এবং তিনি শুনতে পেয়েছেন যে, নিজামী ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন। তিনি দাবী করেছেন তিনি নিজামী সাহেবকে পারিবারিকভাবে চিনতেন অথচ জেরার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মাওলানা নিজামীদের কতজন ভাই-বোন বা মাওলানা নিজামী কোথায় কোথায় লেখাপড়া করেছিলেন তা বলতে ব্যর্থ হন। তিনি মাওলানা নিজামীর পিতার ব্যাপারেও কিছু বলতে ব্যর্থ হন। সুতরাং এতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রসিকিউশনের শেখানো মতে তিনি নিজামীকে জড়িয়ে কথাগুলো বলেছেন, বাস্তবে আদৌ তিনি নিজামী সাহেবকে চিনতেন না।
৯- তিনি স্বীকার করেছেন যে, রেজাউল করিম নামে সাঁথিয়ার একজন সাঁথিয়ার মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে একটি বই লিখেছেন, উক্ত বই ডিফেন্স পক্ষ দাখিল করেছে। উক্ত বইয়ের ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় ধুলাউড়ি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু মাওলানা নিজামী সেখানে উপস্থিত ছিলেন মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা নিজামী সাহেব উক্ত ঘটনার সাথে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নন। তিনি তার জবানবন্দীতে প্রদত্ত ‘ঐদিন রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটার দিকে হঠাৎ করে আর্মীদের পায়ের বুটের শব্দ শুনতে পাই। তখন আমি ঐ বাড়ির ঘরের পূর্ব দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দেখতে পাই যে, মাওলানা নিজামী এবং কিছু দখলদার বাহিনী এবং কিছু রাজাকারসহ আমাদের ঘরের দিকে আসছে।’ বক্তব্যটি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বলেছেন বলে দাবি করেন। অথচ তদন্তকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দীতে অস্বীকার করেন যে, উক্ত সাক্ষী তার নিকট উক্ত কথাগুলি বলেছেন। যে ব্যক্তি মাত্র কয়েক বছর আগে প্রদত্ত জবানবন্দীর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলতে পারে, তিনি ৪২ বছর আগের ঘটনা সম্পর্কেও মিথ্যা কথা বলতে পারেন। সুতরাং এই সাক্ষীকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না।
১০- সাক্ষী মোঃ জামাল উদ্দিন এর বক্তব্যও এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন এবং এ ঘটনা তিনি সাক্ষী মো.শাহজাহান আলীর কাছ থেকে শুনেছেন। যেহেতু সাক্ষী মো.শাহজাহান আলীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং তার কাছ থেকে শোনা সাক্ষী জামালউদ্দিনের বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
১১- প্রসিকিউশনের প্রদর্শিত বই এবং ডিফেন্স পক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত বইতে ধুলাউড়ি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা আছে, অথচ কোথাও মাওলানা নিজামীর সংশ্লিষ্টতার কথা আসেনি। অর্থাৎ প্রসিকিউশনের প্রদর্শিত দলিলেই ঘটনার সাথে মাওলানা নিজামীর সংশ্লিষ্টতার কথা আসেনি, সুতরাং মাওলানা নিজামী এই ঘটনার সাথে অপরাধী সাব্যস্থ করা জুলুমের নামান্তর।
১৬ নং অভিযোগের পর্যালোচনাঃ
অভিযোগ-১৬: মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের ঊষালগ্নে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে আলবদর বাহিনী। দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে আলবদর সদস্যরা ওই গণহত্যা ঘটায়। জামায়াতের তৎকালীন ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ ও আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে ওই গণহত্যার দায় নিজামীর ওপর পড়ে।
১- তদন্তকারী কর্মকর্তার জবানবন্দীসহ অন্যান্য প্রমাণপত্র হতে দেখা যায়, তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের সময় মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়নি। পরবর্তীকালে ফরমায়েশী সাক্ষী সংগ্রহের মাধ্যমে অনেককেই এই অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষী মান্য করা হলেও শুধুমাত্র উল্লেখিত দুজন সাক্ষী ছাড়া প্রসিকিউশন পক্ষ কোনো সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করতে পারেন নাই।
২- অপরাধের সময়কাল: চার্জ গঠনের আদেশে উক্ত অপরাধ সংঘটনের সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলেও বলা হয়েছে প্রধানত: অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়েছে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ অথবা এর আশেপাশের সময়ে। প্রসিকিউশনের দাবি অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে। এর সমর্থনে প্রসিকিউশন একটি বই দাখিল করেছে। এই চার্জের সমর্থনে প্রসিকিউশনের দুইজন মাত্র সাক্ষী যে দু’টি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাদের ভাষ্য অনুযায়ী সে দু’টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ১৫ নভেম্বর এবং ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১। এখন বিচার্য বিষয় হলো উক্ত সময়ে মাওলানা নিজামী ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসেবে আলবদরের প্রধান ছিলেন কি না?
৩- ছাত্রসংঘ প্রধান: প্রসিকিউশনের দাবী মতে মাওলানা নিজামী সাহেব ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন। ডিফেন্সের প্রদর্শিত ডকুমেন্ট থেকে দেখা যায় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এর পরে মাওলানা নিজামী নন বরং তাসনীম আলম মানজার ছাত্র সংঘের প্রধান ছিলেন। সুতরাং ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসেবে পদাধিকার বলে আলবদর প্রধান হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বরের পরে সংঘটিত অপরাধের সাথে মাওলানা নিজামীকে জড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।
৪- আলবদর প্রধান: প্রসিকিউশনের প্রদর্শিত ডকুমেন্ট অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বরের একটি সভায় আলবদর প্রধান হিসেবে মতিউর রহমান নিজামী নন বরং অন্য একজন উপস্থিত আছেন মর্মে দেখা যায়। সুতরাং প্রসিকিউশন ডকুমেন্টের থেকেই একথা প্রমাণিত যে মাওলানা নিজামী আলবদর প্রধান ছিলেন না। প্রসিকিউশনের দাবি অনুযায়ী আলবদর একটি সশস্ত্র অক্সিলারি বাহিনী যার স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামো, মিলিটারি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, বেতনভাতা ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল। একজন বেসামরিক ব্যক্তির এরকম একটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রসিকিউশনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মাওলানা নিজামী ১৯৭১ সালের পুরো সময়েই একজন বেসামরিক ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং নিজামী সাহেবের আলবদর বাহিনীর প্রধান হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এ সংক্রান্তে যুগোশ্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আপিল বিভাগেProsecutor VS Timohir Blaskic, Case No. IT-95-14-A para-114 মামলায় একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, একই ব্যক্তি একই সাথে বেসামরিক নাগরিক এবং সামরিক কর্মকর্তা হতে পারেন না।
৫- মতিউর রহমান নিজামী সাহেব আলবদরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন মর্মে প্রসিকিউশন ৪টি বই দাখিল করেছে। উক্ত বইসমূহের আলোচনায় স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে রেফারেন্স বিকৃত করে অথবা রেফারেন্স ছাড়াই আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসাবে মাওলানা নিজামীকে চিত্রিত করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রসিকিউশন প্রদর্শিত দুটি বইতে মাওলানা নিজামীকে আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা দাবি করা হয়েছে। উক্ত বই দুটির আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, একটিতে ভুল রেফারেন্সে এবং অন্যটিতে রেফারেন্স ছাড়াই এ দাবিটি করা হয়েছে এবং বই দুটির লেখকদের ১৯৭১ সালের ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। উল্লেখিত ৬টি বইই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালের পরে লিখিত। সুতরাং নি:সন্দেহে বলা যায়, মাওলানা নিজামীর সাথে আলবদরের কোনো দূরতম সম্পর্ক ছিল একথা প্রমাণে প্রসিকিউশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।
৬- আলবদরের পরিচয়পত্র হিসেবে প্রসিকিউশন এই মামলায় ১১টি প্রদর্শন করেছে। উক্ত কার্ডগুলি প্রদর্শনকারী তদন্ত কর্মকর্তা জেরায় স্বীকার করেন উক্ত পরিচয়পত্রসমূহ ইস্যু করেছেন একজন ক্যাপ্টেন। এর ইস্যুকারী এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী উভয়েই পাকিস্তানী আর্মি অফিসার। নিজামী সাহেব যদি আলবদর প্রধান হতেন এবং এর উপর যদি তার কমান্ড এবং কন্ট্রোল থাকতো তাহলে অবশ্যই তার স্বাক্ষর থাকতো। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আলবদরের প্রধান ছিলেন না এবং আলবদর বাহিনী তার কমান্ড এবং কন্ট্রোলে ছিল না।
৭- আলবদরের প্রতিষ্ঠা এবং এর কমান্ড ও কন্ট্রোল: প্রসিকিউশনের তথ্য অনুযায়ী আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একাত্তরের ১৬ মে ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তরুণ মেজর রিয়াদ হোসাইন মালিক এবং এর প্রথম কমান্ডারের নাম ছিল কামরান। সুতরাং প্রসিকিউশনের ডকুমেন্ট দ্বারাই প্রমাণিত যে, মাওলানা নিজামী আলবদরের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন না এবং প্রধানও ছিলেন না। ডিফেন্সপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত তৎকালীন পাক বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল নিয়াজি কর্তৃক লিখিত বই The Betrayal of East Pakistan। উক্ত বইয়ের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় জেনারেল নিয়াজি স্পষ্টভাবে বলেছেন, আলবদর বাহিনী ছিল রাজাকার বাহিনীর একটি শাখা যার প্রতিষ্ঠা এবং কমান্ড ও কন্ট্রোলে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ডিফেন্সপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত THE VANQUISHED GENERALS AND THE LIBERATION WAR OF BANGLADESH একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক বই, যেখানে ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে জেনারেল রাও ফরমান আলী ও জেনারেল নিয়াজির সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ আছে। বইটির ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠায় জেনারেল রাও ফরমান আলী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, রাজাকার আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং কমান্ড ও কন্ট্রোলে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বিশেষভাবে জেনারেল নিয়াজি। জেনারেল নিয়াজি তার সাক্ষাৎকারে ১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, অনেকে বলে রাজাকার আলবদর জামায়াতে ইসলামীর। এটা সত্য নয়। আমিই রাজাকার-আলবদর বাহিনী প্রতিষ্ঠা করি এবং আমিই এটা নিয়ন্ত্রণ করতাম, আমি রাজনীতিবিদদের ঘৃণা করতাম এবং জামায়াতের লোকদেরকে আমার কাছে ঘেষতে দিতাম না। এখান থেকেই পরিষ্কার হয় যে, মাওলানা নিজামী নন বরং পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিশেষভাবে জেনারেল নিয়াজি ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং নিয়ন্ত্রক।
৮- প্রসিকিউশন ১৯৭১ সালে মাওলানা নিজামীর খবর সম্বলিত ২১টি পেপার কাটিং এবং ৬টি গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রদর্শন করেছে। এর কোন একটিতেও বলা হয়নি যে, মাওলানা নিজামী আলবদর বাহিনীর সাথে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অথবা তিনি আলবদরের কোনো বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। অথচ এ সমস্ত পত্র-পত্রিকা ও গোয়েন্দা রিপোর্ট সমূহে আল বদরের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যা চুড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, নিজামী সাহেব আলবদরের সাথে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।
৯- বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিষয়ে ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত পর্যন্ত ৪২টি মামলা হয়েছে। যদিও তদন্তকারী কর্মকর্তা ৪২টি মামলা হওয়ার বিষয়ে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার প্রদর্শিত বই “একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়” হতে দেখা যায়, বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের বিষয়ে ৪২টি মামলা ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত দায়ের হয়েছে। তার প্রদর্শিত বই থেকে আরও দেখা যায় যে, বুদ্ধিজীবি হত্যাকাণ্ডটির পরিকল্পনা হামিদুল হকের মালিকানাধীন অবজারভার পত্রিকার অফিসে হামিদুল হকের কক্ষেই সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ভিডিও ডকুমেন্ট “রণাঙ্গনের দিনগুলি” হতে দেখা যায়, খান এ সবুরের বাড়ি থেকে মিরপুর মুক্ত হওয়ার পর বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের নীল নকশা উদ্ধার করা হয়েছিল। ঐ নীল নকশার বিবরণ বা নীল নকশাটি তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট আবেদন করেও পান নাই অর্থাৎ তা আটকে রাখা হয়েছে। অন্যান্য দলিলপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের বিষয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক জহির রায়হানকে আহবায়ক করে একটি বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল যার অন্যতম সদস্য ছিলেন ব্যারিস্টার মওদূদ আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। ঐ কমিটির নথিপত্র জহির রায়হান সাহেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম একটি দেশের একজন সাংবাদিকের হাতে তুলে দেয়া হয়, যা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সংগ্রহের কোনো প্রচেষ্টা করেন নাই বা ঐ কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদূদ আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথেও যোগাযোগ করেননি। এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠনের কথা আমরা বিভিন্ন দলিলপত্র হতে দেখতে পাই কিন্তু এ বিষয়ে ঐ কমিটি কি রিপোর্ট দিয়েছিল বা কি কি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন সে বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনো বক্তব্য দেন নাই। তদন্ত সংস্থা কর্তৃক সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকা তদন্ত সংস্থায় প্রেরিত হলেও তিনি তা সংগ্রহ করেননি বা বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের মামলা সমূহে কি বর্ণনা ছিল তা তিনি জানারও চেষ্টা করেননি। এরপরও যে ২ জন ব্যক্তিকে এই মামলায় সাক্ষী হিসেবে আনা হয়েছে অর্থাৎ শহীদ ডা. আলীম চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী এবং শহীদ ডা. আজহারের স্ত্রী সালমা হক তাদের স্বামীদের হত্যাকান্ডের বিষয়ে মামলা হওয়ার কথা স্বীকার করলেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ মামলার আসামী সম্পর্কে কোনো বক্তব্য দিতে চাননি তবে শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেছেন যে, ডা. আলীম চৌধুরীর মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে।
১০- এই দু’টি হত্যাকান্ডের বিষয়ে তদন্তে দালাল আইনে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিল। ঐ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে নিশ্চিতভাবে এই দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু তখন তারা মাওলানা নিজামীকে জড়িয়ে কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়। সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণে আমরা আরও দেখতে পাই, ঐ দুই হত্যাকাণ্ড সংক্রান্তে স্বাধীনতার পরপরই দুজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাদেরকে ছেড়েও দেয়া হয়েছিল। তারা মাওলানা নিজামী সাহেবের অনুগত ব্যক্তি ছিলেন এই মর্মে কোনো প্রমাণ নাই। উপরন্তু ঐ দুই সাক্ষী যেভাবে মাওলানা নিজামীকে জড়িয়ে ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কোনো কারণ নাই। কেননা তাদের এই বক্তব্যসমূহ তারা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট দেয়া জবানবন্দীর সময় বলেননি। তদন্তকারী কর্মকর্তা এই চার্জের তদন্ত ও সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পর্কে যে বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তা মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কারণ তদন্তকারী কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরে তিনি এই মামলার তদন্ত অব্যহত রাখেন অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই তদন্তের ধারাবাহিকতাতেই ১৩ তম সাক্ষী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে সাক্ষী মান্য করেন যে বিষয়ে তিনি চীফ প্রসিকিউটর বরাবরে ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারির স্মারক নং- আন্ত: অপ: ট্রাই:/তদন্ত সংস্থা/৮৮ মূলে প্রেরিত চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি ৩০ অক্টোবর উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। অথচ তিনি তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, তার সহযোগী তদন্তকারী কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগম উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন ২০১১ সালের ১০ মার্চ। দেখা যাচ্ছে যে, তদন্তের ধারাবাহিকতাতেই এই সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের কথা বললেও এই তদন্তের কয়েক মাস পূর্বেই উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে যা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। ইতিহাস পিছন দিকে ঘুরলেই ২০১১ সালের ১০ মার্চ তারিখটি ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর হওয়া সম্ভব। কাজেই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সংক্রান্তে মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগটি ফরমায়েশী এবং সাক্ষ্য প্রমাণও অনুরূপভাবে গৃহিত।
১১- সাক্ষী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী তার জেরায় যে সমস্ত বিষয়ে স্বীকার করেছেন তাতে খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আদালতে অসত্য জবানবন্দী দিয়েছেন। সাক্ষী সালমা হক তার মামাতো ভাই ইকবাল আর্সালান বর্তমানে কি করেন তা বর্ণনা করতে পারেন, তার খালার স্বামী অর্থাৎ খালু ১৯৭১ সালে কিভাবে নিহত হয়েছেন তার বর্ণনা দিতে পারেন, কিন্তু তার মামা ডা. আসজাদ কোনো সময় জামায়াতে ইসলামী থেকে এম পি নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা বা আদৌ কোনো সময় এম পি নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা তা জানেন না বলায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ট্রাইব্যুনালে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করে অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন। সর্বশেষ ফরমাল চার্জের অসংলগ্ন ও অসত্য বক্তব্য, সে অনুযায়ী চার্জ গঠন, সাক্ষীদের অসংখ্য অসত্য তথ্য প্রদান, মিথ্যাচার, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে গাফিলতি, তথ্য গোপন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত না করা এবং জেরা ও জবানবন্দীতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, পক্ষাশ্রিত ঘোষিত মিথ্যাচারী ব্যক্তিদের বই পুস্তককে সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাখিলি দলিলপত্র ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন না করা প্রমাণ করে যে, মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।
আমার বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে কিছু প্রামাণ্য চিত্র।
১ নং ডকুমেন্টারি
২ নং ডকুমেন্টারি
৩ নং ডকুমেন্টারি
৪ নং ডকুমেন্টারি
আমার বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে কিছু প্রামাণ্য চিত্র।
১ নং ডকুমেন্টারি
২ নং ডকুমেন্টারি
৩ নং ডকুমেন্টারি
৪ নং ডকুমেন্টারি
এত বিশাল আলোচনার পর আমি বিচারবিভাগ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাইনা। কেবল মহান বিচার দিনের জন্য অপেক্ষা। সেদিন নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তায়ালা সুবিচার করবেন।