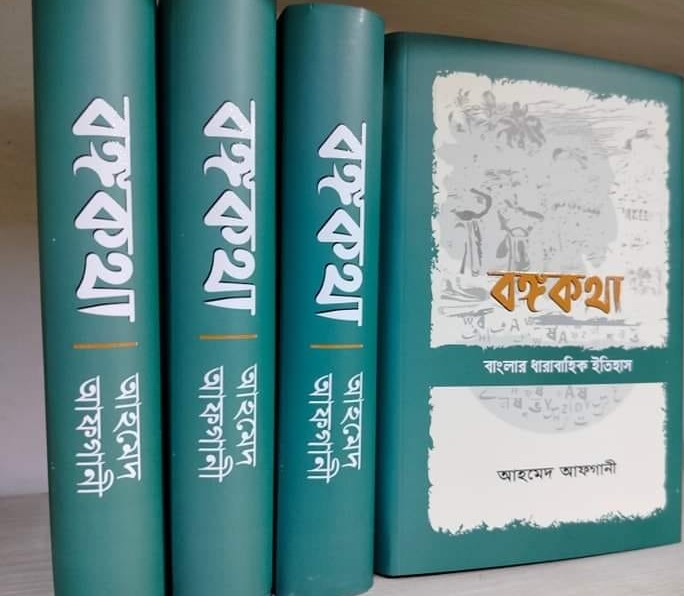ইসলাম মানবজীবনের জন্য আশির্বাদ। যখন আরবে দাসদের সাথে এবং গরীব শ্রমিকদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো তখন আল্লাহর রাসূল সঃ নিয়ে এসেছেন মানবতার বার্তা। যাতে সমাজের প্রত্যেক মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সকল প্রকার জুলুমবাজি বন্ধ করা হয়েছে। ইসলাম মানবতাকে সামনে এনে মানুষকে করেছে সম্মানিত। আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,
“আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিজিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি”।
-(সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)
-(সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)
শ্রমনীতি প্রণয়নের কাজটা সর্বপ্রথম ইসলামই করেছে। ইসলামই প্রথম শ্রমিকের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি দিয়েছে। তাকে দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদা আর শ্রমের স্বীকৃতি। আল্লাহর রাসূল সঃ যখন এই নীতি চালু করেন তখন সমাজে শ্রমিকদের মানুষই মনে করা হতো না, অধিকারতো অনেক পরের ব্যাপার। ইসলাম সমাজের আর দশজন সদস্যের মতো নাগরিক হিসেবে তাদের প্রাকৃতিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রমিক হিসেবে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে অনেক মূলনীতি ও বিধিও প্রবর্তন করেছে। যাতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়।
মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাঁতী কাপড় বুনেন, কুমার পাতিল বানান, নৌকার মাঝি মানুষ পারাপার করেন। এসব কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না কাউকে অবশ্যই কাজগুলো করতে হবে। কেউ যদি এসব কাজ করতে এগিয়ে না আসতেন, তা হলে মানবজীবন অচল হয়ে পড়ত। কোনো কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব কাজ করেন, তারাও হীন বা ঘৃণ্য নন।
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি অর্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।" (বায়হাকী) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেছেন, "তিনি তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক থেকে আহার কর।" (সূরা: মুলক, আয়াত-১৫)
আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি লাগিয়েছেন, মাঠে মেষ চরায়েছেন। নবীজী ব্যবসা পরিচালনাও করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন। বাড়িতে আগত মুসাফির কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে যাওয়া কাপড় ধৌত করে মানবতা ও শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, "শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।" (বায়হাকী) মহানবী এ ব্যাপারে আরো বলেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।" (বুখারী)
কুরআন-হাদিস, ইসলামের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, নবী-রাসূলগণ শ্রমিকদের কত মর্যাদা দিয়েছেন। অনেক নবী ছাগল চরিয়ে নিজে শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া হযরত আদম আ. কৃষক ছিলেন। হযরত নুহ আ. কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। হযরত দাউদ আ. কর্মকার ছিলেন। হযরত ইদ্রিস আ. দর্জি ছিলেন। মালিক হযরত শোয়াইব (আঃ) তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্রমিক নবী মূসাকে (আঃ) জামাই বানিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিক যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে আপন ফুফাতো বোন জয়নবের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বনবী (সা.) যায়েদকে (রাঃ) মুতারের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন বানানো হয়েছিল শ্রমিক হযরত বিলালকে (রাঃ)। মক্কা বিজয় করে কাবা ঘরে প্রথম প্রবেশের সময় মহানবী (সা.) শ্রমিক বেলাল (রাঃ) ও শ্রমিক খাব্বাবকে (রাঃ ) সাথে রেখে ছিলেন। নবীজী কখনো নিজ খাদেম আনাসকে (রাঃ) ধমক দেননি এবং কখনো কোনো প্রকার কটুবাক্য ও কৈফিয়ত তলব করেননি। নবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) নিজ হাতে যাঁতা ঘুরাতেন। আর এজন্য তার হাতে জাঁতা ঘোরানোর দাগ পড়েছিল। তিনি নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন, এতে তাঁর বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল।
কোদাল চালাতে চালাতে একজন সাহাবীর হাতে কালো দাগ পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাত দেখে বললেন, "তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছ ? সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এগুলো কালো দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদাল চালাতে গিয়ে হাতে এ কালো দাগগুলো পড়েছে। নবীজী (সা.) এ কথা শুনে ওই সাহাবীর হাতের মধ্যে আলতো করে গভীর মমতা ও মর্যাদার সাথে চুমু খেলেন। এভাবে অসংখ্য কর্ম ও ঘটনার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।
একইভাবে ইসলাম শ্রমগ্রহীতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে শ্রমিকের সঙ্গে মানবিক ও সম্মানজনক আচরণ করতে। তার প্রতি মমতা দেখাতে। তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাকে বারণ করেছে তার সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ প্রদান থেকে। এমনবিধ নানা অধিকার সুযোগ নিশ্চিত করেছে ইসলাম শ্রমিকের জন্য।
রাসূল সঃ শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে বলেন- তারা তোমাদের ভাই আল্লাহ্ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের উপর এরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো তারা যে রকম খাবার খাবে তাদেরকেও সেরকম খাবার দেবে, তারা যা পরিধান করবে তাদেরকে তা পরাবার ব্যবস্থা করবে। যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ও সাধ্যতীত তা করার জন্যে তাদেরকে কখনও বাধ্য করবে না। যদি সে কাজ তাদের দিয়েই করাতে হয় তা হলে সে জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই করতে হবে। (বুখারী)
ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তির অধিকার :
একজন শ্রমিকের প্রথম অধিকার তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির অধিকার। তাই ইসলাম এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন “মহান আল্লাহ বলেন, আমি তিনজনের বিপক্ষে থাকব কিয়ামতের দিন, তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন, যাকে আমার জন্য প্রদান করার পর সে তার সাথে গাদ্দারী করেছে, আর একজন হচ্ছেন, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর একজন হচ্ছে সে ব্যক্তি যে কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করার পর তার থেকে তার কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ সে তাকে তার প্রাপ্য দেয় নি।”- সহীহ বুখারী
শ্রমগ্রহীতার জন্য জরুরী হলো শ্রমিককে সেই অধিকারগুলো প্রদান করা যার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। তাতে হ্রাস বা বিয়োগের চেষ্টা না করা। কারণ, তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনার মতো জুলুম। সেহেতু শ্রমগ্রহীতার জন্য আরও জরুরী শ্রমিকের কাজের তীব্র প্রয়োজনের সুযোগের অসৎ ব্যবহার করত তাকে তার অধিকারে না ঠকানো এবং একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রাপ্য মজুরির তুলনায় তাকে ধোঁকা দিয়ে কম নির্ধারণ না করা। কেননা ইসলাম সর্বপ্রকার ধোঁকা ও প্রতারণাকে হারাম ঘোষণা করেছে। বাস্তবায়ন করেছে ‘লা দ্বারারা ওয়ালা দ্বিরারা’ তথা ‘ক্ষতি করব না আবার ক্ষতির শিকারও হব না’ নীতি।
একইভাবে তার জন্য আরও জরুরী, শ্রমিকের পাওনা হেফাযত করা যখন সে অনুপস্থিত থাকে কিংবা এর কথা ভুলে যায়। এবং কাজ শেষ কিংবা নির্ধারিত মেয়াদ পূরণ হবার পর মজুরি দিতে টালবাহানা বা বিলম্ব না করা। তেমনি চুক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশি কাজ করলে তার (অতিরিক্ত) বিনিময় প্রদানে ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ না হওয়া। কেননা আল্লাহ আমাদেরকে প্রত্যেক শ্রমের মর্যাদা দিতে বলেছেন। সব কাজের প্রতিদান দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর”। (সূরা আল-মায়িদাহ: ১)
হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
“ধনী ব্যক্তির (পক্ষ থেকে কারও পাওনা প্রদানে) টাল-বাহানা করা জুলুম; আর যখন তোমাদেরকে কোনো আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত করা হয়, তখন সে যেন তার অনুসরণ করে”।
অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
“শ্রমিককে তার শ্রমের প্রাপ্য তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই প্রদান কর”।
স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য না করার অধিকার :
শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিংবা কাজে অক্ষম বানানোর মতো কাজে তাকে বাধ্য না করা শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সে যুগে দাসদের যাই আদেশ করা করা হতো তাই তারা পালন করতে বাধ্য থাকতো। আল্লাহর রাসূল সঃ তার শ্রমনীতিতে এই ধরণের প্রথা বন্ধ করে দেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা যাবে না।
শ্রমগ্রহীতা যখন তার প্রতি এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয় এবং যার ফলে পরবর্তীতে তার স্বাস্থ্য বা ভবিষ্যতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তবে তার অধিকার রয়েছে চুক্তি বাতিল কিংবা বিষয়টি বিচারকের কাছে উত্থাপন করার। যাতে করে তারা তার ওপর থেকে শ্রমগ্রহীতার অনিষ্ট রোধ করেন।
রাসূলে করীম সাঃ শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন, শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদেরকে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে। (তিরমিযি)
তাদের উপর ততখানি চাপ দেওয়া যেতে পারে, যতখানি তাদের সামর্থ্যে কুলায়। সাধ্যাতীত কোন কাজের নির্দেশ কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না। (মুয়াত্তা, মুসলিম)
শ্রমিকের আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার :
শ্রমগ্রহীতার আরেকটি কর্তব্য হলো, শ্রমিকের সম্মান রক্ষা করা। অতএব তাকে কোনো অবমাননা বা লাঞ্ছনাকর কিংবা দাসসুলভ কাজে খাটানো যাবে না। ইসলাম এবং ইসলামের মহান ব্যক্তিদের জীবনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে সমানাধিকারের মূলনীতিকে সমর্থন করে।
যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিক ও কাজের লোকের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন। তার কাজের বোঝা লাঘবে সরাসরি সহযোগিতা করতেন। তেমনি শ্রমিককে প্রহার বা তার ওপর সীমালঙ্ঘনেরও অনুমতি নেই। যদি তাকে প্রহার করে তবে তাকে এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
শ্রমিকের ওপর আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা আদায়ের অধিকার :
শ্রম গ্রহীতার আরেকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো, শ্রমিককে তার ওপর আল্লাহর ফরযকৃত যাবতীয় ইবাদত যেমন সালাত ও সিয়াম ইত্যাদি সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করা। মনে রাখবেন একজন দীনদার বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কিন্তু অন্য যে কারও চেয়ে নিজ দায়িত্ব পালনে বেশি আন্তরিক। কারণ, সে সবার জন্য মঙ্গল সাধন করতে সচেষ্ট থাকে। তার নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি এবং চুক্তি রক্ষার প্রচেষ্টা সঙ্গত কারণেই বেশি হয়।
আপনার অবস্থান যেন আল্লাহর ইবাদত কিংবা ইসলামের প্রতীক রক্ষার কাজে বাধা প্রদানকারীরদের পক্ষে না হয়। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩)
সৎ কাজে বাধা না দিয়ে বরং তাতে ব্রতী হতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা আরও ইরশাদ করেন, তুমি কি দেখেছ, যদি সে হিদায়াতের উপর থাকে, অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? যদি সে মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন? (সূরা আল-আলাক, আয়াত : ১১-১৪)
তাছাড়া শ্রমগ্রহীতা শ্রমিকদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। সুন্দর উপায়ে তাদেরকে নিজ ধর্মীয় শিষ্টাচারাবলি আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করবেন। কেননা, শ্রমিকরা হলেন শ্রমগ্রহীতার আহল। তাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানো তার উপর দায়িত্ব। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আত তাহরীমের ৬ নং আয়াতে বলেন, “তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের আহলকে আগুন থেকে বাঁচাও।” এছাড়াও শ্রমিকদের দীনদারির অনুভূতির লালন-অনুশীলনের মাধ্যমে কাজে তাদের মনোযোগ বাড়বে। এটি তাদেরকে আপন কাজে আরও বেশি নিষ্ঠাবান এবং কাজের স্বার্থ রক্ষায় অধিক যত্নবান বানাবে।
শ্রমিকের অভিযোগ করা এবং বিচার প্রার্থনার অধিকার :
শ্রম বা কর্ম সম্পর্কিত ইসলামী বিধানগুলো কেবল শ্রমিকদের অধিকার সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি প্রবর্তনেই সীমিত থাকে নি; বরং এসব বিধান পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক বিধিগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা শ্রমিকের অভিযোগ ও বিচার চাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে।
সেহেতু ইসলাম চুক্তির পক্ষগুলোকে একেবারে ছেড়ে দেয় নি। বরং তাদের জন্য নিজেদের অধিকারগুলো সহজে পাবার পথ প্রশস্ত করেছে। হোক তা স্বেচ্ছায় কিংবা আদালতের ফয়সালায়। পাশাপাশি তাদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণে অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছে এবং এসব অধিকার রক্ষায় সর্বপ্রকার উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।
আর এই উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের মাঝে অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। কেননা অধিকার ও ইনসাফ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল প্রশান্তি ছড়ায়। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজে একে অপরের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আস্থা মজবুত হয়। সম্পদ উন্নত হয়। স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়। ফলে কেউ অস্থিরতার মধ্যে পতিত হয় না। সর্বোপরি শ্রম ও উৎপাদনে মালিক ও শ্রমিক প্রত্যেকেই নিজ নিজ লক্ষ্যে ধাবিত হয়। পথপরিক্রমায় এমন কিছুর সৃষ্টি হয় না যা শ্রমিকের কর্মস্পৃহাকে ভোঁতা কিংবা মালিকের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে।
বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ইনসাফ ও ন্যায়ানুগতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। জুলুম ও বঞ্চিত করার মানসিকতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা কোনো মানুষের প্রতি জুলুম করেন না; বরং তিনি কোনো প্রকার জুলুম প্রত্যাশাও করেন না। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন যুলম করতে চান না। (সূরা আল-মু’মিন, আয়াত : ৩১)
আবূ যর গিফারী রাদিআল্লাহ আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, ‘হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না’। আর পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল তাদের জুলুম ও অত্যাচারী আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, ‘আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলুম করেছে।’ (সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৩)
আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়ীঘর, যা তাদের যুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে’। (সূরা আন-নামল, আয়াত : ৫২)। আল্লাহ তা’আলা আরও ইরশাদ করেন, ‘আর তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায়। যালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে। (সূরা আল-মু’মিন, আয়াত : ১৮)
আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন, ‘আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল-হাজ, আয়াত : ৭১)। অন্য হাদীসে রয়েছে, জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।’ আবূ মূসা আশ’আরী রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ জালেমকে অবকাশ দেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার পলায়নের অবকাশ থাকে না”।
ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার :
কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে অবশ্যই তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ক্ষতিপূরণের এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন যা মূলত ইসলামী আইন-আদালতের প্রথম উৎস- সামাজিক দায়িত্বের ধারণাকে সমর্থন করে। যেমন আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,
‘আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৯২)
তেমনি নানা উপলক্ষে পবিত্র সুন্নাহও একে সমর্থন করেছে, যা ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। সরাসরি ক্ষতি পূরণে একে সমর্থন করেছে। যেমন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কাছে তাঁর কোনো এক স্ত্রী একটি থালায় আহার হাদিয়া পাঠান। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাতে আঘাত করেন। ফলে থালায় যা ছিল তা পড়ে যায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আহারের বদলে আহার এবং একটি পাত্রের বদলে আরেকটি পাত্র।
তাই শ্রমিকের জন্য শ্রমগ্রহীতার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করার সুযোগ রয়েছে। তার জন্য আরও সুযোগ রয়েছে তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণে বিচার বা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার। এসব হলো শ্রমিকের অধিকারগুলোর সবচে গুরুত্বপূর্ণগুলো। এভাবেই ইসলাম শ্রমিকের অধিকার, সম্মান রক্ষা করেছে। তার সম্মানিত জীবন নিশ্চিত করেছে। সর্বোপরি সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে।
এই কথা অনস্বীকার্য আমাদের সভ্যতা নির্মিত হচ্ছে শ্রমিকের ঘামের উপর। মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। সব ধরনের শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয়, আমাদের দেশে সেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় না। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।