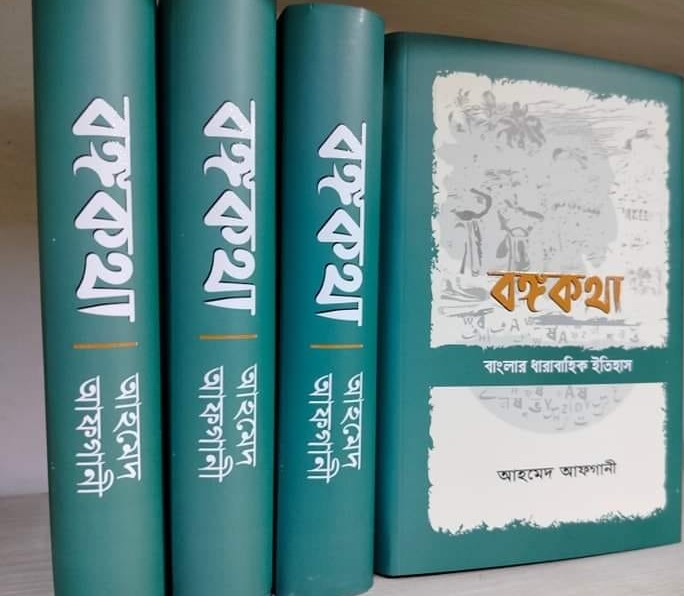|
| রমজান কাদিরভ, চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট |
আমি যখন ছোট ছিলাম, প্রাইমারিতে পড়তাম তখন খবর পেতাম চেচনিয়ায় মুসলিম নির্যাতনের। যে কয়টি এলাকায় মুসলিম নির্যাতনের জন্য আমাদের কাছে পরিচিত ছিল এর মধ্যে চেচনিয়া অন্যতম।
বহুদিন হলো সেখানের খবর আর পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগে খবরে দেখলাম মিশরের সালাহকে নাগরিকত্ব দিয়েছে চেচেন নেতা রমজান কাদিরভ। আজকের লিখা চেচনিয়াকে নিয়ে।
চেচনিয়া বর্তমানে রুশ ফেডারেশনের অন্তর্গত একটি মুসলিম স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল। এটি রাশিয়ার উত্তর ককেশাস অঞ্চলে অবস্থিত। চেচনিয়ার আয়তন ১ লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। চেচনিয়ার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম। চেচনিয়া বহু বছর ধরে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে আসছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসনের ইতিহাস প্রায় চারশ' বছরের।
ককেশাস অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য প্রথম লড়াই মনসুর উসুরমা। তিনি একজন মুসলিম নেতা। তার নেতৃত্বে ১৭৮৫ থেকে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলেন। বিফল হয়ে ১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ইমাম শামাইলের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলো স্বাধীনতার জন্য। অল্প কিছু সাফল্য থাকলেও চূড়ান্ত সফলতা আসে নি।
শেখ নাজমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিমরা আবারো সংঘবদ্ধ হয় এবং ১৯১৭ সালে উত্তর ককেশাস ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। এটা টিকিয়ে রাখতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে মুসলিমদেরকে। ১৯৪২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার সমগ্র ককেশাস দখলে নিতে সক্ষম হয়।
২য় বিশ্বযুদ্ধে চেচেনদেরকে বাধ্য করা হয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুদ্ধে সৈনিকদের জন্য রশদ পরিবহন, যুদ্ধাস্ত্র পরিবহন, বাংকার তৈরি, ব্রিজ কালভার্ট মেরামত ইত্যাদি কাজে চেচেনদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করানো হয়। বেশিরভাগ চেচেন সুযোগ পেলেই যুদ্ধ থেকে পালাতো।
বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, নাজিদের সহায়তা করা ইত্যাদি অভিযোগে বহু চেচেনকে হত্যা করে রুশ কমিউনিস্টরা। ১৯৪৪ সালে স্টালিন প্রায় ৫ লাখ মানুষকে সাইবেরিয়া, কাজাখাস্তান ও কিরগিজস্তানে নির্বাসন দেয়। এতে বহু মানুষ নিহত হয়। কারণ যেসব স্থানে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো এগুলো আদতে বসবাসের উপযোগী ছিল না।
চেচনিয়ার মূল শহর গ্রোজনী সবসময় মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার একটি ভালো স্থান ছিল। মুসলিমদের নির্বাসনে পাঠানোর পর রুশরা মুসলিমদের সব স্থাপনা ধ্বংস করে, লাইব্রেরীগুলো জ্বালিয়ে দেয়। পরিত্যাক্ত এই নগরীতে স্থান দেয় ইহুদী ও মেসখেতিয়ান তুর্কিদের।
৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যু হয়, ৫৭ সালে এই অধ্যাদেশের ফলে মুসলিমরা আবার তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে আসার সুযোগ পায়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চেচেনিয়া ভাষার কোন স্কুল করতে দেওয়া হয় নি যাতে মুসলমানেরা জ্ঞানের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েন।
১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে দীর্ঘকালের রুশ দুঃশাসনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় চেচেনরা ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে গণভোটের আয়োজন করে। গণভোটে চেচনিয়ার অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তৎকালীন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন চেচনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং চেচনিয়ায় প্রেসিডেন্টের শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।
১ম চেচেন যুদ্ধঃ
কিন্তু চেচেন স্বাধীনতাকামীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে আগ্রাসী রুশ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯৯১ সালের ২৯ অক্টোবর চেচনিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে সোভিয়েত বাহিনীর সাবেক জেনারেল জওহর দুদায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি ২৪ নবেম্বর ১৯৯১ আনুষ্ঠানিকভাবে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুদায়েভের এ পদক্ষেপ রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি।
১৯৯৪ সালের ২৬ নবেম্বরের পর রাশিয়া চেচনিয়ায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। আসলান মাশখাদভ নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা গেরিলা অপারেশন চালাতে থাকে। তবে অল্প কিছুদিন পরই গ্রোজনী দখল করে রুশরা। গ্রোজনী দখলের দু'বছর পর ১৯৯৬ সালে দুদায়েভকে রুশ বাহিনী হত্যা করলে ১ম চেচেন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
২য় চেচেন যুদ্ধঃ
১৯৯৯ সালের আগস্টে চেচেন ও আরবীয়ান বিদ্রোহীগণ শামিল বাসায়েভ ও আমির খত্তাবের নেতৃত্বে যুদ্ধ-বাহিনী গঠন করেন। চেচেন বিদ্রোহীদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে তৎকালীন রাশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন তাদের বিরুদ্ধে ১৯৯৯ সালের ১লা অক্টোবর কঠোর সামরিক অভিযান চালায়। রাশিয়ান বাহিনী চেচনিয়াতে ঢুকে পড়ে।
২০০০ সালে সরাসরি বিদ্রোহীদের মধ্যে এক নেতা আখমাদ কাদিরভকে পুতিন তার নিজের দলে টেনে নিতে সক্ষম হয়। এরপর তাকে নেতা বানিয়ে সেখানে ডিরেক্ট রুল শুরু করে রাশিয়া। আখমাদ কাদিরভেরও অনেক সমর্থক ছিল। ফলে বিদ্রোহীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং রুশরা সেখানে সহজে জয়লাভ করে।
আখমাদ কাদিরভ ২০০৪ সালে বিদ্রোহীদের একটি আত্মঘাতী হামলায় নিহত হলে তার ছেলে রমজান কাদিরভ এখন চেচনিয়ার নেতা হন। তার নেতৃত্বে অনেকটাই শান্তি ফিরে এসেছে রাশিয়ায়।
তিনি চেচনিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। এর একটি জোরালো কারণ হচ্ছে চেচনিয়ায় ইসলামী আইন বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছে পুতিন। বিনিময়ে শুধু অনুগত থাকতে হবে। ২০০৭ সাল থেকে রমজান কাদিরভ একই সাথে মুসলিম ও রুশ স্বার্থ দেখার পর চেচনিয়ায় শান্তি ফিরে আসে।
রমজান কাদিরভ তার এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, স্বাধীনতা আমাদের জন্য সমস্যা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করেনি। রাশিয়ার কাছ থেকে চেচনিয়া স্বাধীন হোক তা আমি চাই না। আমরা শান্তি চাই।