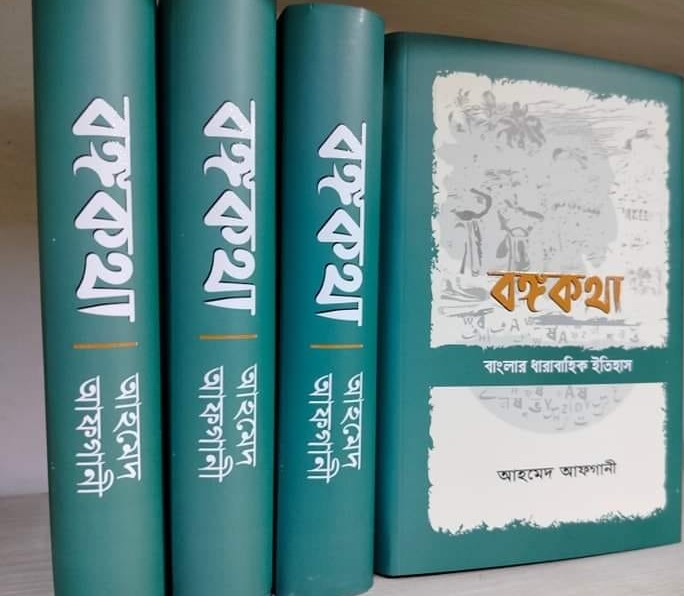ভিডিওটা দেখে আমি অবাকই হয়েছি। সেটা যতটা না মসজিদের স্থাপত্যনকশা দেখে তার চাইতে বেশি এর স্থপতিকে দেখে। বলছি ঢাকার দক্ষিণখানের একটি মসজিদের কথা। নাম বাইতুর রউফ। স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। অবাক হওয়ার কারণ দু'টি। প্রথমত বাংলাদেশে মসজিদ পরিচালনায় মহিলাদের দেখা যায় না। মহিলা আর্কিটেক্ট তো আরো দূরের কথা। দ্বিতীয়ত মেরিনা তাবাসসুমের চাল-চলন পুরোটাই ওয়েস্টার্ন। ইসলামিক তো দূরের ব্যাপার, সাধারণ বাঙালি মহিলার মতোও না। অথচ তার হাতেই প্রতিষ্ঠিত হলো অসাধারণ এক মসজিদ।
হপ্তাখানেক আগে একদিন সকালে একটি নোটিফিকেশনের সূত্র ধরে বাইতুর রউফ মসজিদের ভিডিওটি আমার সামনে আসে। গত বছর মসজিদ ভ্রমণের একটি পরিকল্পনা মাথায় আসে। চেষ্টা করতাম শুক্রবার অফিস বন্ধের সুযোগটা কাজে লাগাতে। কিন্তু এই বছর শুক্রবারগুলোতেই যেনো বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সঙ্গী সাথীরা তাড়া দেয়, কিন্তু সময় সুযোগ হয়ে উঠে না। শুধু আমিই যে ব্যস্ত তা নয় যাদের সাথে যাবো তারাওতো কম ব্যস্ত নয়।
মসজিদের প্রোমো ভিডিও দেখার পর চিন্তা করলাম শুক্রবারের জন্য বসে থাকা উচিত হবে না। বরং সেদিনই বিকেলে রওনা হয়ে যাবো। চিন্তা অনুসারে সঙ্গী সাথীদের মেসেজ পাঠানো শুরু করি। মাত্র একজনকে পাওয়া গেলো। লাঞ্চের পর অফিসকে নিজ দায়িত্বে ছুটি দিয়ে রওনা হয়ে গেলাম বাইতুর রউফ মসজিদের উদ্দেশ্যে। অবশ্য এর আগে সারাদিনের কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলাম।
মসজিদ বলতেই আমরা বুঝি আর্চ, গম্বুজ, মিনার ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া অসাধারণ মসজিদ হতে পারে আমার ধারণা ছিলো না। সুলতানি আমলের স্থাপত্যের অনুপ্রেরণা আর সঙ্গে মেরিনার নিজস্ব স্বকীয়তা এ দুয়ে মিলে তৈরি মসজিদটি। ৭৫৪ বর্গমিটারের ‘বাইতুর রউফ’ মসজিদটির বিশেষত্ব হলো পরিচিত আর্চ, ডোম বা মিনার নেই। কেননা ইট এখানে প্রধান কাঠামো ধারক নয়, কাঠামোটি চতুর্দিকে আটটি কলামের ওপর বসানো।
সূর্যের আলো ছাড়াও পর্যাপ্ত দিবালোক নিশ্চিত করতে ৪টি আলোক স্থল (light courts) আছে। ৮টি পেরিফেরাল কলামের উপর ভর করে মসজিদটি দাঁড়িয়ে। ছাদ থেকে এলোপাতাড়ি ও বৃত্তাকার দিনের আলো প্রবেশ পথ মেঝেতে অসাধারণ ও নান্দনিক প্যাটার্ন তৈরি করে।
মসজিদের প্ল্যানটিতে একটি স্কোয়ারের ভেতর একটি সার্কেল, তার ভেতর আরেকটি ৫০ ফুট X ৫০ ফুটের স্কোয়ার। আবার এ কক্ষটির চতুর্দিকে উপর থেকে আনা হয়েছে সূর্যের আলো। অনেকটা দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তের সঙ্গে আলোর তীব্রতা আর বিচ্ছুরণ যেন খেলা করে ইটের বৃত্তাকার প্রকোষ্ঠে।
মসজিদের বাইরের দেয়ালে ব্যবহার করেছেন ইটের জালি, যেন বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারে। প্রার্থনা কক্ষটির ফ্লোরে ব্যবহার করেছেন পাথরের গুঁড়ার মোজাইক, কাচের বিভাজন রেখার সমন্বয়ে। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এ মসজিদে যেমন ঝকঝকে রোদের দেখা মেলে, তেমনি ঝম ঝম বৃষ্টি এখানে দারুণ বর্ষার আবহ তৈরি হয়। বিশেষ বাতাস চলাচল ব্যবস্থা এখানকার তাপমাত্রা রাখে নিয়ন্ত্রিত। প্রাকৃতিক আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় দিনে বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির পানি সরে যাওয়ার জন্য রয়েছে সুন্দর ড্রেনেজ সিস্টেম।
শুধু কি দিনের আলো! নক্ষত্র সমৃদ্ধ চাঁদের আলো থেকেও বঞ্চিত হননা এখানকার মুসল্লিরা। এই মসজিদ শুধুই স্থাপনা নয়। প্রকৃতিক পরিবেশ ও আধুনিক স্থাপত্যকলা মিলে এক অসাধারণ আবহ। এমন পরিবেশে মহান প্রভুর ইবাদত সত্যিই মনকে প্রশান্ত করে। স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম ইট আর কংক্রিটের ভবনে প্রাণের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।
বাইতুর রউফ মসজিদের গল্পটা কীভাবে শুরু হয়েছে এই নিয়ে কথা আমরা সরাসরি স্থপতি মেরিনা থেকেই শুনি। ২০১৮ সালে ৫ নভেম্বর প্রথম আলোতে তিনি বলেন,
"বাইতুর রউফ মসজিদের গল্পের শুরু ২০০৫ সালে। আমার নানি তখন খুবই অসুস্থ। একদিন আমাকে চায়ের দাওয়াত দিলেন। দুই মেয়েকে পরপর হারিয়ে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। ২০০২ সালে মা মারা যান, পরের বছর এক খালা। আর নানা মারা গেছেন ১৯৭১ সালে। সাত মেয়ে, তিন ছেলেকে প্রায় একা হাতেই মানুষ করেছেন নানি।
তুরাগ নদের ধারে নানার কিছু জমি ছিল। নানি বললেন, এলাকায় ভালো কোনো মসজিদ নেই। তিনি জমি দিতে চান। আমি যেন মসজিদের নকশা করি।
সবাই মিলে জমি নির্বাচন করা হলো। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা মিলাদ পড়িয়ে ১০ কাঠা জমির ওপর মসজিদের কাজ শুরু করি। সে বছরই নানি মারা গেলেন; ডিসেম্বরে।
জরিপ, নকশা তৈরি, অর্থ জোগাড়ের কাজ চলতে থাকল। সুলতানি আমলের নকশা বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যশৈলী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে নকশা হলো। ২০০৮ সালে শুরু হলো মসজিদ নির্মাণের মূল কাজ। সবাই জানত আমার নানি মসজিদের জমি দিয়েছেন। তাই কখনো কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হইনি। ইমাম সাহেব, স্থানীয় লোকজন—সবাই খুব সাহায্য করেছেন।"
‘আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার-২০১৬’ লাভ করে মসজিদটি। ‘আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার’ যে কোন স্থপতির জন্য স্বপ্ন। পুরষ্কারের মূল্যমান এ অ্যাওয়ার্ডের গুরুত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা দেয় (আগা খান অ্যাওয়ার্ডের মূল্যমান $১০০০,০০০ এবং নোবেল প্রাইজের মূল্যমান $১৫০০,০০০)।
আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) প্রতি তিন বছর পরপর ‘আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার’ পুরষ্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারটিতে স্থাপত্যে শ্রেষ্ঠত্ব, পরিকল্পনা এবং ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি স্থাপত্যের মাধ্যমে সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়।
২০১৬ সালের আগ পর্যন্ত তিনটি স্থাপনা জাতীয় সংসদ ভবন, গ্রামীণ ব্যাংক হাউজিং প্রকল্প ও রুদ্রপুর মেটিস্কুল ‘আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার’ লাভ করে, যেখানে তিনজনই ছিলেন বিদেশী স্থপতি। বাংলাদেশের প্রথম দুজন স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী স্থাপত্যে অনন্য সম্মান ‘আগা খান স্থাপত্য’ লাভ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩৪৮টি প্রকল্পের মধ্য থেকে ১৯টি প্রকল্পকে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য বাছাই করা হয়, যেখানে স্থাপত্যের স্বকীয়তায় স্থান করে নেয় স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমের ঢাকার ‘বায়তুর রউফ মসজিদ’ এবং স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর গাইবান্ধার ‘ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার’।
আমরা যখন আসর নামাজ শেষ করলাম তখন মসজিদের একপাশে দেখলাম জিলাপির প্যাকেট। বুঝলাম মিলাদ হবে এবং শেষে তবারক হিসেবে জিলাপি দেয়া হবে। সঙ্গীকে বললাম আজকে কিন্তু তবারক খেয়েই যাবো। অতএব বিদআত বলে যাতে সে মিলাদ থেকে বেশি দূরে না থাকে। সে আমাকে ইশারা দিয়ে বুঝালো তার খুব একটা সমস্যা নেই। নামাজ শেষে বসে রইলাম। ইমাম সাহেব যার উদ্দেশ্যে দোয়া করা হবে তার সম্পর্কে বললেন। এরপর সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে মুনাজাত করলেন। বুঝলাম ইমাম সাহেব মিলাদ-কিয়ামের লোক নন।
 |
| স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম |
যাই হোক আমি তবারক খুবই উচ্ছসিত হলাম। আসলেই ভালো ছিলো জিলাপিটি। মসজিদের বারান্দায় বসে ঠাণ্ডা বাতাসে জিলাপি খাচ্ছিলাম। এমন সময়ে একটি ছোট বাবু তার মায়ের হাত ধরে কোথাও যাচ্ছিল। আমি ভেংচি কাটলাম, সেও প্রতিউত্তর করলো। এভাবে চলছিলো। আমার সহযাত্রী আমাকে কড়াভাবে সতর্ক করলো। বললো, এটা অচেনা যায়গা। মানুষ ছেলেধরা বলে পিটুনি দিলে কিছু করার থাকবে না। সাথে সাথে অসুস্থ বাংলাদেশের কথা ভেবে চুপসে গেলাম।
কীভাবে যাবেন?
এখনতো লোকেশন চিনা কোনো ব্যাপার না। বাইতুর রউফ বলে গুগোল ম্যাপে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। তারপরও সহজে লোকেশন বলে দিচ্ছি। উত্তরা আব্দুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ডে যাবেন। সেখানে গিয়ে কোনো রিকশাকে বললেই নিয়ে যাবে ফয়দাবাদ লাল মসজিদ। স্থানীয়রা একে লাল মসজিদ বলে জানে। আব্দুল্লাহপুর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে মসজিদটি।
মসজিদ থেকে বের হয়ে চাপের বাপ নামে একটি কাবাব হাউজে উদরপূর্তি করে বাসার দিকে রওনা হলাম।