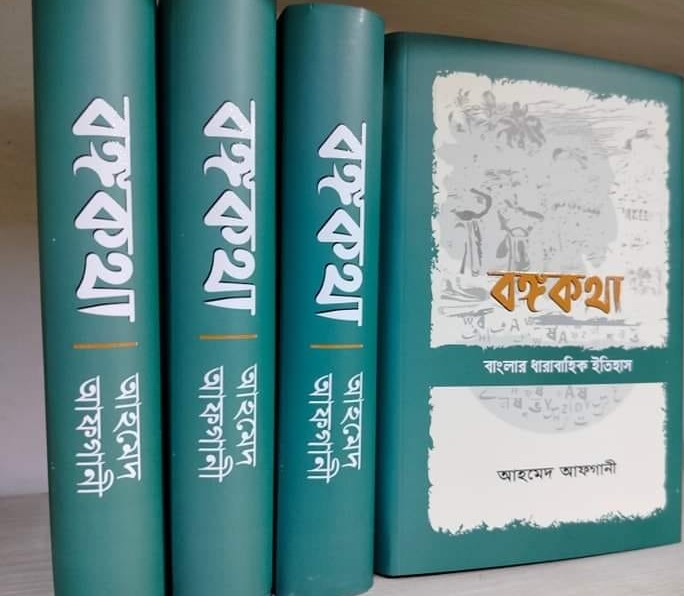১৯৫৪ সালের আগে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলা দরকার। তাহলে সে সময়ের পরিস্থিতি কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে এবং যুক্তফ্রন্টের প্রেক্ষাপট বুঝা যাবে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার কালে মোটাদাগে বাংলায় রাজনৈতিক দল ছিল দুইটি। এক মুসলিম লীগ, দুই কৃষক প্রজা পার্টি। ১৯৪৫-৪৬ সালের পরিস্থিতিতে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি অস্তিত্ব হারিয়েছে হিন্দুদের সাথে মিলিত হওয়ার দায়ে। একইসাথে বাংলার মানুষের কাছে ফজলুল হক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর তিনি রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে আইন পেশায় সময় দিতে থাকেন।
এছাড়া জামায়াতে ইসলামী তখন একেবারে ক্ষুদ্র একটি দল। রাজনীতিতে যাদের খুব একটা প্রভাব নেই। এছাড়াও আরেকটি দলের অস্তিত্ব তখন ছিল তারা হলো জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। এটা হলো আলিয়া ও দেওবন্দি আলেমদের একটি বিচ্ছিন্ন দল যারা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ থেকে আলাদা হয়েছেন। আলেমদের মধ্যে যারা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছেন তারা হুসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে আলাদা দল গঠন করেন। এদের নেতা ছিলেন শাব্বির আহমদ উসমানী। এই দলের উতপত্তিই হয়েছিল মুসলিম লীগকে সাপোর্ট করার জন্য।
সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে নবগঠিত পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ছাড়া আর কারো প্রভাব ধর্তব্য ছিল না। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকায় মুসলিম লীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন মাওলানা আকরম খাঁ এবং খাজা নাজিমুদ্দিন। তাদের প্রভাবে দলের মধ্যে প্রায় কোণঠাসা ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনুসারীরা। তারা মূলত ইসলামী চেতনা ধারণ করতেন না। তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদটাকেই বেশি ধারণ করতেন। তারা মোঘলটুলিতে ১৫০ নম্বর বাড়িতে একটি কর্মী শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার কথা চিন্তা করছিলেন। সোহরাওয়ার্দির নির্দেশে তার অনুগত শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে এসে তাদের সাথে যুক্ত হন।
এদিকে ভাসানী এবং তার অনুসারীরা মুসলিম লীগকে সমাজতান্ত্রিক বামধারায় রূপান্তর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইসলামী চেতনাধারীদের তোপের মুখে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। ভাসানী টাঙ্গাইলের আরেক নেতা শামসুল হককে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বুঝান এবং তার সাথে রাখেন। ভাসানী আদর্শিক বিষয় গোপন রেখে বাঙালিদের নিয়ে আলাদা দল গঠনের উদ্যোগ নিতে থাকেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে সোহরাওয়ার্দির সাথে যোগাযোগ করেন। তারা একটি সভা ডাকেন। সেই সভা ডাকার প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান।
১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলীর কেএম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন টাঙ্গাইলের আবদুল হামিদ খান ভাসানী আর সেক্রেটারি শামসুল হক। ঘটনাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু'জনেই টাঙ্গাইলের। সহ-সভাপতি হন আতাউর রহমান খান, শাখাওয়াত হোসেন ও আলী আহমদ। শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ কে রফিকুল হোসেনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোষাধ্যক্ষ হন ইয়ার মোহাম্মদ খান। এসময় শেখ মুজিব কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। অন্যদিকে, পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংগঠনটির নাম রাখা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। আর এর সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
নিখিল পাকিস্তানে এই দলটি আসলে কার্যকর ছিল না। এটা মূলত বাঙালিদের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠেছে।
ভাসানী এই দলটিকে মুসলিম লীগ বিরোধী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বাঙালিদের মধ্যে মুসলিম লীগ বিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরি করে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে আওয়ামী যুবলীগ সকল বিরোধীদলের ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরুতেই ‘গণতান্ত্রিক দল’ ও ‘আওয়ামী লীগ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দও মুসলিম লীগ বিরোধী জোটের জন্য কাজ করতে থাকে।
এর সূত্র ধরে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিশেন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের উদ্দেশে সমমনা দলসমূহ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাসানী শেরে বাংলাকে আবারো রাজনীতিতে আসার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারির সঙ্গে সঙ্গে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে তার দলের ভরাডুবি ঘটলে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন নূরুল আমিন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হককে পূর্ববাংলার এটর্নি জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পুনরায় রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তার ১৯৩০ এর দশকের নিজস্ব দল কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নাম পরিবর্তন করে এর নতুন নামকরণ করেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি (KSP)।
আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন। যুক্তফ্রন্টের আরেকটি শরিকদল- নেজামে ইসলাম যাদের পূর্ব নাম ‘জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দের ওয়াদা ভঙ্গের ফলে নবগঠিত পাকিস্তানে 'নেজামে ইসলাম' তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূর পরাহত দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়েন। এক প্রকার প্রতারিত হয়েই ১৯৫২ সালে নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের সঙ্গ ত্যাগ করে 'নেজামে ইসলাম পাটি' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় দলটির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনেই মাওলানা আতহার আলীকে সভাপতি, মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক এবং মাওলানা আশরাফ আলীকে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত করে 'নেজামে ইসলাম পার্টি'র কার্যক্রম শুরু হয়। যেকোন মূল্যে পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে এই পার্টির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়। মুসলিম লীগের তুলনায় এই দলের নেতৃতে বড় বড় উলামা থাকায় অল্পদিনেই নেজামে ইসলাম পার্টি একটি শক্তিশালী বৃহৎ দলে পরিণত হয়।
নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝতে পেরে নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ; কিন্তু শেরে বাংলা ও নেজামে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের বিরোধীতায় এই দলগুলিকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে ভাসানীর চেষ্টায় গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হয়।
নির্বাচনে যাওয়ার আগে আরো একটি দল যুক্তফ্রন্টে যোগ দিতে চেয়েছে। তারা হলো খেলাফতে রব্বানী পার্টি। এই উদ্দেশে ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগে পার্টির সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা যুক্তফ্রন্টে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেই। খেলাফতে রব্বানী হলো তমুদ্দুন মজলিশের ফাদার অর্গানাইজেশন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে তমুদ্দুনকে অনেকে বাম কমিউনিস্টদের আরেকটি রূপ বলে ধরে নিয়েছে। তাই খেলাফতে রব্বানীও শেরে বাংলা ও মাওলানা আতাহার আলীর বিরোধীতায় যুক্তফ্রন্টে যুক্ত হতে পারেনি। তাই তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়, তারা মাত্র ১০টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এবং বাকি ২২৬টি আসনের জন্য রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।
এদিকে বাংলায় মুসলিম লীগের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তার প্রধানমন্ত্রীত্ব চলাকালে ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও কাদিয়ানী দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মোহাম্মদ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার আমলে দারিদ্রেরর হার বাড়ে বিধায় পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়, এটিও তার পদচ্যুতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে পদচ্যুত হয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। এই কারণেই মূলত মুসলিম লীগ দূর্বল হয়ে পড়ে। ওনার পরে মোহাম্মদ আলী বগুড়া হাল ধরলেও তিনি নাজিমুদ্দিনের মতো প্রভাবশালী নেতা ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের গ্রহণ যোগ্যতাও ভালো ছিল না। সর্বোপরি আলেমদের একটি বড় অংশ মুসলিম লীগকে ত্যাগ করলে মুসলিম লীগের অবস্থান নষ্ট হয়ে পড়ে।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট তাদের নীতি ও ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে।
নীতি : কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।
নির্বাচনী ওয়াদা :
১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ, পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।
৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত উপকূলে কুটিরশিল্প ও বৃহৎশিল্পে লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিমীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মুহাজিরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।
৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।
৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকলপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।
৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।
১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।
১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া কম বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।
১৩. দুনীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য-আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।
১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।
১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।
১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তান অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।
২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।
২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।
১৯৫৪ সালে মার্চের ৮-১২ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে একটি বড় অংশ মানুষ ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এর কারণ সম্ভবত মুসলিম লীগের নিষ্ক্রিয়তা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩৭% ভোট কাস্ট হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে মোট আসন ছিল ৩০৯ টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭ টি। এর মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন, যুক্তফ্রন্ট ২১৫টি আসন, খেলাফতে রব্বানী ১টি আসন ও বাকীগুলো স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতে নেয়। পরবর্তীতে স্বতন্ত্রদের একজন মুসলিম লীগে ও আটজন যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়। ফলে মুসলিম লীগের জয়ী আসন হয় ১০টি আর যুক্তফ্রন্টের জয়ী আসন হয় ২২৩টি।
প্রচণ্ড জনপ্রিয় মুসলিম লীগের এই পতনের কারণ যা পাওয়া যায় তা হলো,
১- দল ভেঙে যাওয়া ও বহু প্রভাবশালী নেতার আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান
২- লবণ, কোরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।
৩- দীর্ঘ ৭ বছরেও সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়া।
৪- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি
৫- খাজা নাজিমুদ্দিনের নীরব থাকা
৬- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া
৭- পূর্ববাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা।
৮- মুসলিম লীগের গণসংযোগের অভাব।
৯- দুর্নীতি দমনে সরকারি ব্যর্থতা
নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জিতে যাওয়া মূলত মুসলিম লীগের অদক্ষতার কারণেই হয়েছে। এর বাইরে আরেকটি কারণ ছিল যুক্তফ্রন্ট নেতাদের প্রচারণা ছিল চোখে পড়ার মতো। সারাদেশে সাংগঠনিক মজবুতি ও নির্বাচন মনিটর করার জন্য ভাসানী কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। একইসাথে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবেন বলে প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রার্থী হন নি। সেই সুবাদে এই দুই নেতা সারা বাংলায় জনসমাবেশ করে বেড়িয়েছেন।
নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে তাদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের সরকার যুক্তফ্রন্টের সাথে কোয়ালিশন করে। যুক্তফ্রন্ট থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন মোহাম্মদ আলী বগুড়া ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।
এদিকে যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রধান নির্বাচিত হন শেরে বাংলা ফজলুল হক। কারণ সোহরাওয়ার্দি ও ভাসানী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সেই জন্য শেরে বাংলা পূর্ববাংলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান এবং তার নেতৃত্ব ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) চার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির সৈয়দ আজিজুল হক ও আবু হোসেন সরকার এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে কৃষক শ্রমিক-পার্টির আবদুল হাকিম এবং আওয়ামী লীগের শাহেদ আলী। ১৫ মে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক। মন্ত্রী পরিষদ গঠন নিয়ে শেরে বাংলা ও আওয়ামীলীগের সাথে ব্যাপক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেরে বাংলা কিছু কিছু নেতা যেমন শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খানকে কোনোভাবেই মন্ত্রীসভায় নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।
যাই হোক, শেরে বাংলা আওয়ামীলীগের চাপে মন্ত্রিসভা গঠন করেন নিজের অপছন্দের ব্যাক্তিরাসহ। মন্ত্রীসভার সদস্যরা হলেন, এ কে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন; আবু হোসেন সরকার অর্থ; আতাউর রহমান খান বেসামরিক সরবরাহ; আবুল মনসুর আহমদ জনস্বাস্থ্য; কফিল উদ্দিন চৌধুরী বিচার ও আইন; সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন; আবদুস সালাম খান শিল্প ও পূর্ত; শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন; আবদুল লতিফ বিশ্বাস রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার; আশরাফ আলী চৌধুরী সড়ক ও গৃহ নির্মাণ; হাশিম উদ্দিন আহমদ বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন; রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী স্বাস্থ্য ও কারা; ইউসুফ আলী চৌধুরী কৃষি, বন ও পাট এবং মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন জমিদারি অধিগ্রহণ।
মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরুর আগে আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গায় ১ হাজার ৫০০ নিরপরাধ শ্রমিক নিহত হন। শুরুতেই এমন একটি বিপর্যয় প্রাদেশিক সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। শপথ নেয়ার পর শেরে বাংলা কলকাতায় সফরে যান এবং সেখানে হিন্দু মহাসভার কয়েক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সেসব বক্তব্যে তিনি হিন্দু মহাসভার পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে এক করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর ঢাকায় তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাতকারে তিনি সাংবাদিক কালাহানকে বলেছেন, বাংলাকে স্বাধীন করা তাঁর প্রথম কাজ।’ কলকাতার বক্তব্য ও সাক্ষাৎকারের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় ঢাকায়। মাত্র কয়েকদিন আগে বিপুল ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান ফজলুল হকের বিরুদ্ধে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ফজলুল হকের পদত্যাগের দাবি জোরালো হতে থাকে। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩১ মে দেশদ্রোহের অভিযোগে এ কে ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন।
শেরে বাংলা ফজলুল হককে গৃহবন্ধী করা হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ করার অপরাধে শেখ মুজিব ও আওয়ামীলীগের বহু নেতাকর্মীকে আটক করা হয়। এদিকে সোহরাওয়ার্দি ছিলেন পাকিস্তানে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। আর ভাসানী ইউরোপ সফরে ব্যস্ত ছিলেন। সদ্য নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্টের এই বেহাল দশা দেখে শেখ মুজিব আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘এই দিন থেকে বাঙালীদের দুঃখের দিন শুরু হলো। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কাজ করতে নামতে নেই, তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশ বেশি হয়।’
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। প্রায় সাত মাস বন্দী জীবন যাপন করে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। এরপর দলের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান করাচি গমন করেন। সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:
আমি তাঁর (সোহরাওয়ার্দী) সঙ্গে বেয়াদবি করে বসতে পারি। পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।…তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, “বুঝেছি, আর বলতে হবে না, বেলা তিনটায় এসো, অনেক কথা আছে।” আমি বেলা তিনটায় গিয়ে দেখি, তিনি একলা শুয়ে বিশ্রাম করছেন।…আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ আলাপ করলেন, তার সারাংশ হলো গোলাম মোহাম্মদ জানিয়ে দিয়েছেন যে মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলে তিনি মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেবেন। আমি বললাম, পূর্ব বাংলায় গিয়ে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রিত্ব দিতে পারতেন। আমার মনে হয়, আপনাকে ট্র্যাপ করেছে। ফল খুব ভালো হবে না, কিছুই করতে পারবেন না। যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন, তা শেষ করতে চলেছেন।
মাওলানা ভাসানী ইউরোপ থেকে ফিরে কলকাতায় একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগ নেই। যুক্তফ্রন্ট নিষ্ক্রিয়প্রায়। এদিকে গোলাম মুহাম্মদ কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকারকে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা মাওলানা ভাসানীর দেশে ফিরে আসার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় ভাসানী ১৯৫৫ সালের ২৬ এপ্রিল কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন।’
এদিকে মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী বগুড়ার সাথে শেরে বাংলার সমঝোতা হয়ে যায়। বগুড়ার পরামর্শে ফজলুল হক আওয়ামীলীগকে ছাড়াই পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটা সঠিক কাজ ছিল না, কারণ আওয়ামীলীগ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এতে ক্ষিপ্ত হয় সোহরাওয়ার্দি এবং ভাসানী। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না কারণ তারা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নন। তাই তারা শেখ মুজিবকে দিয়ে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তারা ভেবেছিল এতে শেরে বাংলা মূখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারি নেতা হিসেবে ফজলুল হকের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে শেখ মুজিব। কিন্তু এতে আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীত হয়। ৩২ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য পার্টি পরিবর্তন করে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন। এই ধারা অব্যাহত থাকে, ফলে ২ এপ্রিল (১৯৫৫)এর মধ্যেই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যসংখ্যা ১৪০ থেকে ৯৮-এ নেমে আসে। তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩৪ থেকে বেড়ে ৬৯ হয় এবং নেজামে ইসলামীর সদস্য সংখ্যাও বেড়ে ১২ থেকে ১৯ হয়।
তাছাড়া ১৯৫৫ সালের শুরুর দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ভাসানী মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলের নাম শুধু আওয়ামী লীগ করে। এই ‘মুসলিম' শব্দ বাদ দেবার কারণে ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে দলবদ্ধ হয় এবং তারা কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামীকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন দেয়। এইভাবে যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ। গণতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট দলের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, অন্য দিকে খিলাফতে রব্বানী পার্টি ও কিছু হিন্দু-সদস্য ফজলুল হকের জোটকে সমর্থন দেন। এইভাবে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত মুসলমান সদস্যবৃন্দ দুই ধারায় বিভক্ত হয়। ১৯৫৫ সালের ৬ জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গঠিত মন্ত্রিসভা ‘যুক্তফ্রন্ট’ নাম নিয়েই শপথ নিয়েছিল। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল, তবে এখানে আওয়ামীলীগের কেউ ছিল না।
আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে গ্রহণ করে, অপরপক্ষে ফজলুল হকের জোট মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রক্ষার্থে ১৯৫৬ সালে ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ববাংলার গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন। গভর্নর পদে যোগদান করে ফজলুল হক ২২ মে ১৯৫৬ তারিখে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভার পতন হবে এই আশঙ্কায় গভর্নর ২৪ মে (১৯৫৬) আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছে না এই কারণ দেখিয়ে জরুরি ক্ষমতা বলে এখানে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। সাত দিন পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল করা হয়।
১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া-সংবিধান সমর্থন করে আবু হোসেনের মন্ত্রীসভা। অপরদিকে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করাকে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে বিরোধিতা করে ভাসানীর নির্দেশে। কিন্তু আওয়ামীলীগের মূল নেতা সোহরাওয়ার্দি ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করেন। আওয়ামী লীগ সংবিধানে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা ও পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি করে। কিন্তু গণপরিষদে কৃষক-শ্রমিক পার্টি মুসলিম লীগকে সমর্থন করায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার সংবিধান পাস করিয়ে নিতে সমর্থ হন। আওয়ামী লীগ গণপরিষদ থেকে ওয়াকআউট করে এবং সংবিধানে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। তবে সোহরাওয়াদী ব্যক্তিগতভাবে সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।