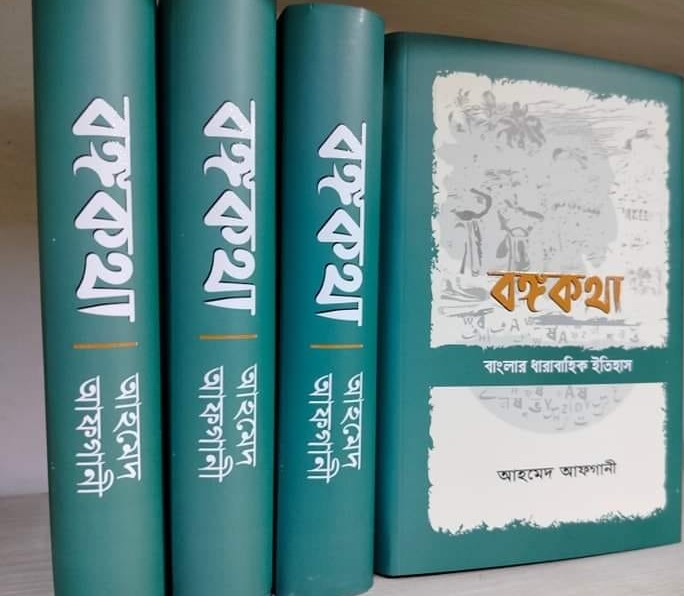ইসলাম খান চিশতির পর ১৬১৩ থেকে ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় নয়জন সুবাহদার বাংলা শাসন করেন। তাদের এই শাসনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। মোগল সম্রাট শাহজাহান তার ছেলে শাহ সুজাকে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাহদার নিযুক্ত করেন। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ঊড়িষ্যা প্রদেশের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বছরের কিছু অধিক সময় ধরে তিনি প্রদেশ দুটি শাসন করেন। এ সময়ে তাঁর শাসনের দুটি সংক্ষিপ্ত বিরতি ছিল প্রথম বিরতি হয় ১৬৪৭-৪৮ পর্যন্ত। প্রথম বিরতিতে আফগানিস্তানের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে তিনি সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন, দ্বিতীয় বিরতি ঘটে ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে তখন তিনি এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত চার মাস কাল কাবুলে অবস্থান করেন। তাঁর সুবাহদারির শেষ দিকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিংহাসন দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে দু'বার তিনি রাজধানী দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন।
শাহ সুজার নিযুক্তির সময় ঢাকা সুবাহ বাংলার রাজধানী ছিল। শাহ সুজার শাসনকালে বাংলা ও ঊড়িষ্যা প্রদেশ দুটিতে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছিল; কোন অংশেই কোন বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। প্রকৃতপক্ষে জমিদার ও দুষ্কৃতিকারীরা সুবাহদার হিসেবে রাজকুমারকে দেখে হতবিহবল হয়ে পড়ে। তদুপরি সুজার উপর কেবল দুই প্রদেশের (বাংলা ও ঊড়িষ্যা) সুবাদারির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নি, তিনি কামরূপ ও আশ্রিত রাজ্য কুচবিহার দখল করেন, যা তৃতীয় আর এক প্রদেশের সমতুল্য ছিল এবং এটিও তাঁর অধীনে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সুজা পূর্ব ভারতের শাসক ছিলেন।
শাহ সুজা ব্যাপক রাজ্য বিজয়ের জন্য খ্যাত ছিলেন না, তবে মনে হয় তিনি হিজলি ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হিজলি অঞ্চলে বাহাদুর খান নামক এক স্বভাবগত বিদ্রোহী শাসন করতেন (পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলা)। সুজার সময়ে বাহাদুর রাজস্ব পরিশোধে বিলম্ব করেন, এই বিলম্বের জন্য সুজা তড়িৎ ব্যবস্থা নেন। বাহাদুর খান পরাজিত হন এবং আগের চেয়ে আরও বেশি রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ক্ষমা লাভ করেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালায় ওই রাজ্যের সাথে সুজার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বর্তমান কুমিল্লার সীমান্ত সংলগ্ন অংশবিশেষ ছেড়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন। একটি মসজিদ তৈরির মধ্যদিয়ে সুজা এই বিজয় স্মরণীয় করে তোলেন। মসজিদটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে এবং সুজার নাম মনে করিয়ে দেয়। এটি কুমিল্লা শহরের অদূরে গোমতি নদীর তীরে অবস্থিত।
শাহ্ সুজা বড় নির্মাতা ছিলেন। ঢাকার প্রাচীন মোগল দালানগুলি তাঁর সময়েই নির্মিত হয়। দালানগুলি হলো বড় কাটরা, ঈদগাহ, হোসেনী দালান এবং চুড়িহাট্টা মসজিদ। চকবাজারের একটু দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে বড় কাটরা তৈরি করা হয়। মনোমুগ্ধকর স্থাপনাটি মূলত যুবরাজের বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়, কিন্তু থাকার জন্য তিনি রাজমহল পছন্দ করায় বড়কাটরা ভ্রাম্যমাণ বণিকদের বাসের জন্য দেওয়া হয়, অর্থাৎ এটি কাটরা বা সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঈদগাহ উঁচু ভিতের চারদিকে ঘেরা দিয়ে বানানো হয়। বছরে দুই ঈদে জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। তার শাসনামলে সৈয়দ মুরাদ ১৬৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেনী দালান নির্মাণ করেন। এখানে শিয়া সম্প্রদায় জামাতে নামাজ আদায় করতেন, আর চুড়িহাট্টা মসজিদ ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়। রাজমহলে শাহ সুজা ‘সাঙ্গ-ই-দালান’ (পাথরের প্রাসাদ) নামে এক প্রাসাদ এবং মার্বেল পাথরের এক মসজিদ তৈরি করেন। ‘আনন্দ-সরোবর’ নামে এক দিঘি এখনও শাহ সুজার স্মৃতি বহন করে। পুকুরের চারদিকে তৈরি করা হয় দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, হাম্মাম (গোছল খানা), হাউজ (জলাধার) এবং ফোয়ারা (ঝর্ণা)। এর বাইরে গৌড়ে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) তিনি তাহখানা, তিন গম্বুজ মসজিদ, সরাইখানা, দীঘি খননসহ নানান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে শাহ সুজা সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি বিদেশি বণিক ও ইউরোপীয় কোম্পানিদের সাদর আমন্ত্রণ জানান এবং অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা করে দেন। তিনি পর্তুগিজদের এক ‘নিশান’ (যুবরাজের দেওয়া অনুমতি পত্র) প্রদান করেন, যার মাধ্যমে সম্রাটের ‘ফরমানে’ দেওয়া বাণিজ্যিক সুবিধাদি স্বীকার করা হয়। তিনি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ডাচ কোম্পানিকেও অনুরূপ সুবিধাদি দেন।
১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে গুজব রটে যে সম্রাট মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর বড় পুত্র দারাশিকো সিংহাসনে তাঁর অবস্থান দৃঢ়করণের জন্য তা গোপন রেখেছেন। বাকি তিন যুবরাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী অভিমুখে যাত্রার প্রস্ত্ততি নিতে থাকেন। সুজা নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন ও রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। গঙ্গা নদীতে বহু সংখ্যক যুদ্ধের নৌকা সজ্জিত করে বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। বাহাদুরপুরের তুমুল যুদ্ধে (আধুনিক উত্তর প্রদেশ, ভারত) দারার বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে আবার প্রস্ত্ততি নেওয়ার জন্য সুজা রাজমহলে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব দুবার (ধর্মাট ও সামগড়ে) দারাকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে বন্দি ও হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুজা আবারও রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। এবার তাঁর অভিযান ছিল আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি খাজোয়াতে (ফতেহপুর জেলা, উত্তর প্রদেশ, ভারত) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও সুজা পরাজিত হন। তিনি বাংলার দিকে পশ্চাদপসরণ করেন।
আওরঙ্গজেবের সেনানায়ক মীর জুমলার অধীন রাজকীয় বাহিনী দ্বারা ভীষণভাবে তাড়িত হলেও সুজা প্রতিটি জায়গায় তাদেরকে বাধা দিতে থাকেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন। প্রতিটি পরাজয়ের পর স্বীয় বাহিনীর সেনারা তাঁকে ছেড়ে যেতে থাকে কিন্তু তিনি তাতে হতোদ্যম হন নি। তিনি বরং নতুন উদ্যমে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। কিন্তু তান্ডাতে যখন চারদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ছিলেন এবং সৈন্য পুনর্গঠিত করা আর সম্ভব নয় মনে করলেন তখন চিরকালের জন্য তিনি বাংলা (এবং ভারতবর্ষ) ত্যাগ করে আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সপরিবারে এবং দলবল নিয়ে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তান্ডা ত্যাগ করে এপ্রিলের ১২ তারিখে ঢাকা পৌঁছেন। ৬ মে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ১২ মে নোয়াখালীতে দলবল নিয়ে আরাকানের পথে জাহাজে ওঠেন।
শাহ্ সুজার পর বাংলার নতুন সুবাহদার নিযুক্ত হন মীর জুমলা। তিনি সম্রাট আলমগীরের (আওরঙ্গজেব) প্রতিনিধি ছিলেন। মীর জুমলার শাসন ছিলো মাত্র তিন বছরের। কিন্তু তিনি যুদ্ধ জয় ও বাংলায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলাকালে শাহ সুজার অনুপস্থিতির কারণে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং সেখানে অবাধ্যতা এবং একগুঁয়েমি দেখা দিয়েছিল। তিনি সুজা কর্তৃক রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর বাতিল করে ঢাকাকে তার পূর্বতন গৌরবে পুনঃঅধিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি বিচার বিভাগের প্রতি নজর দেন। তিনি অসৎ কাজী ও মীর আদলদের বরখাস্ত করে তাদের স্থলে সৎ ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করেন।
 |
| মীর জুমলার গেট |
ঢাকা ও শহরতলী এলাকায় মীরজুমলার নির্মাণ কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে দ্রুত সৈন্য চলাচল, যন্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ প্রেরণের জন্য এবং জনকল্যাণমূলক দুটি রাস্তা ও দুটি সেতু। কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে তিনি কয়েকটি দুর্গও নির্মাণ করেন। একটি দুর্গ ছিল টঙ্গী জামালপুরে, যা ঢাকাকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্তকারী (বর্তমানে ময়মনসিংহ রোড নামে পরিচিত) সড়কটির নিরাপত্তা বিধান করত। অন্য সড়কটি পূর্বদিকে চলে গিয়ে রাজধানীকে ফতুল্লার (পুরাতন ধাপা) সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেখানে দুটি দুর্গ রয়েছে। আরও বিস্তৃত হওয়া এই সড়কটি দিয়ে খিজিরপুর পর্যন্ত যাওয়া যেত এবং সেখানেও দুটি দুর্গ অবস্থিত ছিল। ফতুল্লার অদূরে পাগলা সেতুটি এই রাস্তায় অবস্থিত। মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত সড়ক ও দুর্গগুলির কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান।
বাংলায় মীরজুমলার শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তিনি সীমান্তবর্তী কামরূপ এবং আসাম রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন। কুচবিহার ছিল সামন্ত রাজ্য, কিন্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধের সুযোগে রাজা প্রাণ নারায়ণ আনুগত্য অস্বীকার করেন। আসামের রাজা জয়ধ্বজ সিংহ কামরূপ দখল করে নেন। এটা আগে বাংলা সুবাহর অঙ্গীভূত ছিল। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে মীর জুমলা শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর মূল অংশ কামরূপের দিকে প্রেরণ করে তিনি নিজে কুচবিহারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি নিকটবর্তী হলে প্রাণ নারায়ণ দেশ ত্যাগ করে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যান। কুচবিহার দখল করতে দেড় মাসের মতো সময় লেগেছিল এবং সেখানকার প্রশাসনিক বন্দোবস্ত করে মীরজুমলা কামরূপের দিকে প্রেরিত অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগদান করেন। আসামের রাজা কামরূপ ত্যাগ করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দান করেন। তবে মীরজুমলা আসাম জয়েরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে আসাম ছিল একটি বড় ভূখন্ড এবং এর ভৌগোলিক প্রকৃতি ছিল বাংলা থেকে অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু কিছুই মীরজুমলাকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি।
 |
| উসমানী উদ্যানে স্থাপিত মীর জুমলার কামান "বিবি মরিয়ম" |
গৌহাটি থেকে যাত্রা শুরু করার পর ছয় সপ্তাহেরও কম সময়ে মীরজুমলা আসামের রাজধানী গড়গাঁও পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। রাজা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই ভূখন্ডটি ছিল ঘোড়া ও সৈন্যদের পক্ষে দুর্গম উঁচু পাহাড়। বর্ষাকালে মুগল সৈন্যবাহিনী কিছু উঁচু ভূমিতে আটকে পড়ে, রাস্তাঘাট ডুবে যায় এবং ছোট ছোট নদী, এমনকি নালাগুলিও (নর্দমা) স্ফীত হয়ে বড় নদীর আকার ধারণ করে। অসমিয়াগণ চারদিক থেকে তাদের অভ্যাসগত রাত্রিকালীন আক্রমণ চালিয়ে মুগলদের নাজেহাল করে; রাস্তাগুলি প্লাবিত হওয়ার ফলে কোন কিছু পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়ে যার ফলে ঘাঁটি থেকে তাদের জন্য খাদ্য দ্রব্যাদি আসাও বন্ধ হয়ে যায়। শিবিরগুলিতে মানুষ ও পশুর জন্য প্রচন্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ঘোড়াগুলি হত্যা করতে শুরু করে এবং বহু কষ্টে মুগলগণ সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়। খাদ্যাভাব ছাড়াও দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর বায়ু এবং জলের কারণে মোগল শিবিরগুলিতে মহামারি দেখা দেয়। এর ফলে মীরজুমলার সৈন্যবাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মীরজুমলা নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন।
দেশের অর্থনীতিতে ব্যবসা ও ব্যবসায়ীদের অবদান সম্পর্কে মীর জুমলা অবগত ছিলেন। বাংলার সুবাহদার হিসেবে তিনি ব্যবসায়ীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর আমলে পর্তুগিজদের বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু, তাদের স্থান নেওয়ার জন্য ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানিগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা তাঁর ক্ষমতায় ভীত ছিল এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করত। রাজকীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে তাদেরকে প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধাদি ভোগ করার জন্য তিনি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিসহ বিদেশী বণিকদের সাহায্য করেছিলেন।
নিজের চেষ্টায় সামান্য অবস্থা থেকে অতি উচ্চপদে উন্নীত মানুষ মীরজুমলা ছিলেন সতেরো শতকে ভারতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উদ্যোগী এবং নম্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। একজন সাধারণ কেরানি হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি মুগল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সুবাহদার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। একজন ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু মোগল সুবাহদার হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।
মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাহদার নিযুক্ত করেন সম্রাট আলমগীর। শায়েস্তা খান ৬৩ বছর বয়সে প্রথম বাংলায় আসেন। তাঁর ছয়জন দক্ষ পুত্র শাসনকাজে তাঁকে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই এক বা একাধিক সরকারের ফৌজদারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। যার ফলে একই পরিবার বাংলার সব বিভাগ কার্যকরভাবে শাসন করেছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ, কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন এবং অন্যায় কর বিলোপ করে জনগণকে স্বস্তিদানের জন্য শায়েস্তা খানের প্রশংসা করেছেন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাদের শাসনকালে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং শায়েস্তা খান প্রশাসনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর শক্তি নিয়োজিত করেন। সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক সততার ফলে অসৎ কর্মকর্তা ও অবাধ্য জমিদাররা ভীত হয়ে পড়েছিল, যার ফলে প্রশাসনের সকল শাখায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।
 |
| লালবাগ কেল্লা |
প্রধানত চট্টগ্রাম জয়ের জন্যই বাংলায় শায়েস্তা খানের বিশাল খ্যাতি। মোগলদের বাংলা বিজয়ের আগে চট্টগ্রাম আরাকানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাহদার ইসলাম খান চিশতি বাংলা ও আরাকানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী ফেনী নদী পর্যন্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের কয়েকজন সুবাহদার চট্টগ্রাম দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আরাকানি সৈন্যরা নৌ-চালনা ও নৌ-যুদ্ধে দক্ষ ছিল। যার ফলে আরাকানের রাজাগণ কখনোই মোগল সুবাহদারদের শান্তিতে থাকতে দেন নি। মাঝে মাঝেই তারা বাংলায় নৌ-অভিযান পাঠাতেন এবং তাদের গতিপথের অন্তর্ভুক্ত এলাকার যে কোন অংশে লুঠপাট চালাতেন। এমনকি কখনও কখনও তারা রাজধানী শহর ঢাকায়ও আক্রমণ করতেন। ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য হারিয়ে ফেলার পর পর্তুগিজরাও সতেরো শতকের গোড়া থেকে জলদস্যুতা শুরু করেছিল। পর্তুগিজ জলদস্যুরা আরাকানে আশ্রয় লাভ করত। আরাকানের রাজা তার শত্রুর অধীন বাংলার সীমান্ত অঞ্চল লুঠ করার জন্য মগ জলদস্যুদের সঙ্গে পর্তুগিজদেরও নিযুক্ত করতেন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত জলদস্যুদের যাত্রাপথে নদীগুলির দুই তীর অর্থাৎ উপকূলীয় জেলাগুলি প্রায় জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছিল। জলদস্যুরা ধনসম্পদের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান, পুরুষ, নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে যেত এবং ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসিদের মতো বিদেশী বণিকদের কাছে এবং দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলিতে বন্দিদের দাস হিসেবে বিক্রি করত।
কাজেই বাংলায় পৌঁছে শায়েস্তা খান প্রথমেই আরাকানীদের বিপজ্জনক মনোভাবের প্রতি মনোযোগী হন। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সুবাহদার ত্রিমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করেন:
প্রথমত, তিনি নওয়ারা বা রণতরীগুলি পুনর্গঠিত করেন,
দ্বিতীয়ত, পর্তুগিজদের নিজের দলে টেনে আনার চেষ্টা করেন, এবং
তৃতীয়ত, তারা যেন তাঁকে সাহায্য করে অথবা অন্তঃতপক্ষে নিরপেক্ষ থাকে এ উদ্দেশ্যে তিনি ওলন্দাজ কোম্পানিকে তাঁর দলে টানার চেষ্টা করেন।
শায়েস্তা খান মুগল সরকারের পূর্ববর্তী নৌ-বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। তাছাড়া পুরানো নৌকাগুলিকে মেরামত করা হয় এবং ঢাকা ও যশোরের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানায় এবং অন্যান্য নদীবন্দরে নতুন নৌকা তৈরি করা হয়।
সকল প্রস্ত্ততি সম্পন্ন করে শায়েস্তা খান প্রথমে সন্দ্বীপ দ্বীপটি জয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে অভিযানের ঘাঁটি ছিল ভুলুয়া (নোয়াখালী), তবে এটা ছিল স্থলবাহিনীর জন্য ঘাঁটি। পক্ষান্তরে আরাকান ছিল মূলত একটি নৌ-শক্তি। স্থল ও জল উভয় দিক থেকেই চট্টগ্রাম আক্রমণ করা ছিল আবশ্যক। সুতরাং নৌ-বাহিনীর জন্য একটি ঘাঁটির প্রয়োজন ছিল এবং সন্দ্বীপ ছিল একটি আদর্শ নৌ-ঘাঁটি। শায়েস্তা খান তাঁর নৌ-সেনাপতিকে সন্দ্বীপ আক্রমণের আদেশ দেন এবং তিনি ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। সন্দ্বীপের শাসক ছিলেন মোগলদের এক পলাতক প্রাক্তন নাবিক, ৮০ বছর বয়স্ক দিলওয়ার খান। তিনি শৌর্য ও দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। সন্দ্বীপ দখল করে মোগলদের শাসনাধীন করা হয়।
 |
| সাত গম্বুজ মসজিদ |
ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিরাও মোগলদের পক্ষে চলে আসে। মোগলদের জন্য সৌভাগ্যক্রমে তখন চট্টগ্রামের মগ রাজা ও সেখানকার পর্তুগিজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আরাকানি রাজার তীব্র রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্তুগিজরা তাদের পরিবার, জাহাজ এবং কামান নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে ভুলুয়ার (নোয়াখালী) মোগল সেনাপতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। শায়েস্তা খান পর্তুগিজ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জানান। তিনি তাকে নগদ ২০০০ টাকা পুরস্কার ও ৫০০ টাকা মাসিক বেতন প্রদান করেন। তার অনুগামীদেরও উপযুক্ত বেতন-ভাতাসহ মুগল সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়। বাটাভিয়ার ওলন্দাজ গভর্নর জেনারেল তার কোম্পানির সাহায্যের ব্যাপারেও শায়েস্তা খানকে আশ্বস্ত করেছিলেন। তারা আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ তাদের বাণিজ্য কুঠি বন্ধ করে দেয়, তাদের কর্মচারীদের প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের জাহাজগুলির গতিপথ আরাকান থেকে অন্যান্য স্থানে পাল্টে দেয়। চট্টগ্রাম অভিযানে কাজে লাগানোর জন্য ওলন্দাজ কোম্পানি শায়েস্তা খানকে দুটি জাহাজ পাঠান। তবে সেগুলি এসে পৌঁছার আগেই শায়েস্তা খান চট্টগ্রামে আরাকানিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।
শায়েস্তা খান ১৬৬৫ খিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তাঁর দীর্ঘ দিন ধরে পরিকল্পিত চট্টগ্রাম অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানকে সার্বিক নেতৃত্ব দেওয়া হয় এবং নৌ-সেনাপতি ইবনে হোসেনকে নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। সুবাহদার নিজে রসদ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী একই সময়ে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে স্থল ও সমুদ্রপথে যাত্রা করে। স্থল বাহিনীকে জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করে অগ্রসর হতে হয়েছিল। সমুদ্রে এবং পরে কর্ণফুলী নদীতে একটি বড় যুদ্ধে পর্তুগিজদের সাহায্য নিয়ে মুগলরা বিজয়ী হয়। আরাকানী নৌ-বাহিনী পরাজিত হলে তাদের নাবিকরা পালিয়ে যায় এবং তাদের কেউ কেউ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম দুর্গ অবরোধ করা হয় এবং ১৬৬৬ খিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তা মোগল অধিকারে আসে। পরের দিন বুজুর্গ উমেদ খান দুর্গে প্রবেশ করেন এবং চট্টগ্রামকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একজন ফৌজদারের অধীনে মোগল প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সম্রাটের অনুমতি সাপেক্ষে এর নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ রাখা হয়। প্রধানত মগ-পর্তুগিজ জলদস্যুদের লুটতরাজ, অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মানুষ রক্ষা পাওয়ায় চট্টগ্রাম জয় সারাদেশে অবর্ণনীয় আনন্দ বয়ে আনে। হাজার হাজার অপহৃত ও ক্রীতদাসে পরিণত বাঙালি কৃষকদের মুক্তিলাভ ছিল এই বিজয়ের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল।
শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির ব্যবসাকে উৎসাহিত করেন এবং তাদের স্বার্থের নিরাপত্তার জন্য রাস্তা ও নদীগুলিকে ডাকাতমুক্ত করেন। রাজকীয় ফরমানগুলির শর্তানুসারে তিনি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে বিশেষ অধিকার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি তাদের বিশেষ অধিকারগুলির অপব্যবহার করত এবং তাদের কুঠিয়াল ও নাবিকরা রাজকীয় ফরমান দ্বারা নিষিদ্ধকৃত ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হতো। কাজেই মাঝে মাঝে বিশেষত শুল্ক দাবি ও প্রদান নিয়ে বন্দর ও শুল্ক বিভাগের মোগল কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটত। সম্রাট বাণিজ্যের প্রসারকে উৎসাহিত করতেন, কারণ বাণিজ্য, বিশেষত রপ্তানি বাণিজ্য আয় বৃদ্ধি ঘটায়।
শায়েস্তা খান একজন নির্মাতাও ছিলেন। তিনি রাজধানী শহর ঢাকা ও তার বাইরে বেশ কয়েকটি মসজিদ, সমাধি এবং অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ঢাকাকে স্থানীয় বাণিজ্য, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যান। তাঁর কল্যাণে ঢাকা একটি ছোট দাপ্তরিক কেন্দ্র থেকে বৃহৎ ও উন্নত শহরে পরিণত হয়। শয়েস্তা খাঁ মসজিদটি তার তৈরি একটি সুবৃহৎ কীর্তি। বাংলা ও মুঘল স্থাপত্য কীর্তির মিশ্রণে তৈরি এই ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও তার আমলে লালবাগ কেল্লা, হোসনী দালান, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা নির্মিত হয়।
তাঁর দক্ষ সেনাপতিত্ব, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণের অগ্রগতি সাধনের জন্য সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকবৃন্দ শায়েস্তা খানের প্রশংসা করেছেন। তাঁর উদারতা, বদান্যতা এবং ধর্মপ্রাণতার উপরও তাঁরা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি একজন কবি ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নির্মাণ কার্যাবলি পরবর্তীকালে শায়েস্তা খানী রীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। মোগল আমলে সুবাহ বাংলার দায়িত্ব পাওয়া সুবাহদারদের মধ্যে অনন্য কীর্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন শায়েস্তা খান। তার জীবদ্দশায় তিনি দুই পর্বে বাংলার সুবাদারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একই সাথে সবচেয়ে বেশি সময় বাংলার সুবাদারের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথম দীলির খান ও দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার রূপে বাংলাদেশ শাসন করেন।
১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খান সুবাদারের দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় আসেন। ১৬৭৬ সালে উড়িষ্যা তার সুবেদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। টানা ১৪ বছর পর ১৬৭৮ সালে জাহাঙ্গীরের আদেশে এক বছরের জন্য তিনি দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন। ১৬৭৯ সালে সেপ্টেম্বরে তিনি আবার দ্বিতীয়বারের কত বাংলায় ফিরে আসেন। শায়েস্তা খান প্রায় ২২ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। শায়েস্তা খান একদিকে ছিলেন সুশাসক, অন্যদিকে একজন বিজয়ী যোদ্ধা ও নিপুণ নির্মাতা। ১৬৮৮ খৃস্টাব্দের জুন মাসে এইই শাসব দিল্লির উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন। এর মধ্য দিয়েই শেষ হয় শায়েস্তা খানের সোনালি যুগ।