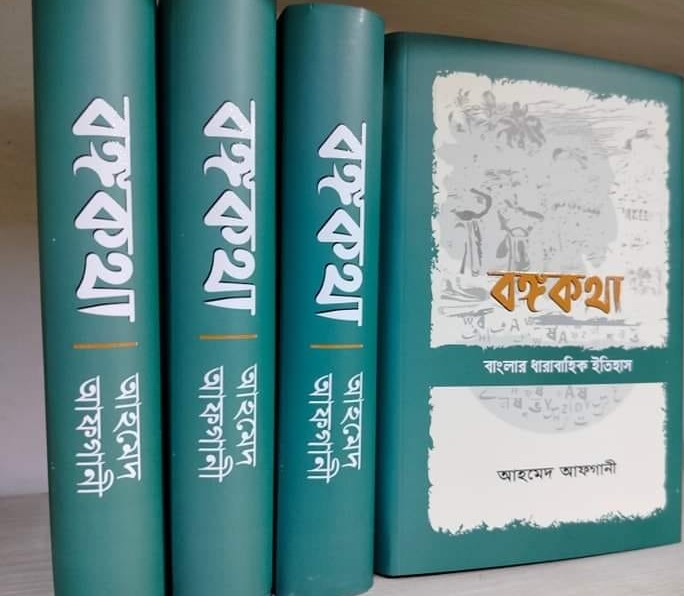বন্ধুবর মঈন সাহেবের বিয়ে। খুলনায় যেতেই হবে। তার একদিন পর আবার আরেক কলিগের বিয়ে সাতক্ষীরায়। সেখানেও যেতে হবে। এদিকে পকেট প্রায় ফাঁকা। কী যে করি! সুন্দরবনে যাবো অনেক দিন ধরেই ভাবছি। তবে নানান প্রতিবন্ধকতায় সুন্দরবনে যাওয়া হয়নি। যাই হোক পকেটের অংকের সাথে জরুরী প্রয়োজনের হিসেব কোনদিনেই মিলে না।
অবশেষে প্ল্যান করলাম খুলনা-সাতক্ষীরা থেকে ঘুরে আসে। সাথে বাগেরহাট ও সুন্দরবনও একনজর দেখে আসি।
একজন দুজন করে সাতজন জুটে গেলো। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর ফোরকাস্ট করলো আগামী কয়েকদিন শীত বেড়ে যাবে, কুয়াশা হবে প্রচুর, শৈত্যপ্রবাহ সাথে বৃষ্টিও থাকবে।
রাতে রওনা হলাম। পরদিন দুপুরে বিয়ে। যেহেতু আবহাওয়া সুবিধের না, ভেবেছি আমাদের পৌঁছাতে সকাল গড়িয়ে যাবে। বাসে উঠে গল্প-গুজব শেষ করে যেই চোখটা একটু লেগে আসলো তখনই মাওয়া ঘাটে আমাদের বাস থকে নামিয়ে ফেরিতে উঠানো হলো। ফেরিতে বসা পরের কথা দাঁড়ানোরও পর্যাপ্ত জায়গা নেই। অবশেষে পদ্মা নদীর ঐ পাড়ে পৌঁছলাম।
ভোগান্তি ছাড়াই ঐ পাড়ে দাঁড়ানো কানেক্টিং বাস পেয়ে গেলাম। বাসে উঠেই ঘুমিয়ে পড়লাম। এই সময় এক সহযাত্রীর হাঁক ডাকে ঘুম টুটে গেলো। সে আমাদের সবাইকে চিৎকার করে জানালো গাড়ি খুলনা শহর পার হয়ে চলে যাচ্ছে। তখনো সুবহে সাদিকও হয়নি। শিরোমনি বাজারে নামলাম। সেখান থেকে আবার সোনাডাঙায় ফেরত এলাম। ঘুমে থাকার কারণে কিছু টাকা খরচ হলো। কিন্তু খরচেই চাইতেই যেটা বেশি গায়ে লেগেছে তা হলো ঠান্ডা। সোনাডাঙা বাস স্টেশনে ফেরত আসতে গিয়ে জমে গেছি।
নামাজ ও নাস্তা শেষ করে রওনা হলাম বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদের উদ্দেশ্যে। প্রথমে গেলাম গাজী খান জাহান আলীর মাজারে।
বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসকল ওলী-আউলিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় একটি নাম হযরত খান জাহান আলী (র)। একাধারে তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা, সাধক, ধর্ম প্রচারক ও সুশাসক। জীবনের একটা বিশাল সময় তিনি ব্যয় করেন ইসলামের সেবায়। দক্ষিণবঙ্গে খান জাহান আলী খলিফাতাবাদ নামে ইসলামী শাসন চালু করেন। খান জাহান আলীর প্রকৃত জন্ম তারিখ জানা যায় না। তিনি প্রায় ৪০ বছর দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করেন।
হজরত খান জাহান আলী (রহ.) ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আকবর খাঁ এবং মাতার নাম আম্বিয়া বিবি। খান জাহান আলীর প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতার কাছে শুরু হলেও তিনি তার মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন দিল্লির বিখ্যাত অলি ও কামেল পীর শাহ নেয়ামত উল্লাহর কাছে। তিনি কোরআন, হাদিস, সুন্নাহ ও ফিকহ শাস্ত্রের ওপর গভীর জ্ঞানার্জন করেন।
খান জাহান আলী ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে তুঘলক সেনাবাহিনীতে সেনাপতির পদে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন। ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি জৈনপুর প্রদেশের গভর্ণর পদে যোগ দেন। পরবর্তী জীবনে নানা ধাপ পেরিয়ে জৈনপুর থেকে প্রচুর অর্থসম্পদ এবং প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। তার এই বাহিনীতে কয়েকজন সূফি ও প্রকৌশলী ছিল। তিনি তদানীন্তন বাংলার রাজধানীর দিকে না যেয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের দিকে আসেন এবং এখানে ইসলামী শাসন কায়েম করেন।
তিনি এই বৃহৎ অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেন। নোনা পানির এই অঞ্চলে মিঠা পানির ব্যবস্থা করেন অসংখ্য বিশাল বিশাল দীঘি খনন করে, যার অনেকই খাঞ্জালির দীঘি নামে পরিচিত। অনেক রাস্তা-ঘাট, বাজার, সরাইখানা (হোটেল) নির্মাণ করেন। তার নির্মিত রাস্তা খাঞ্জালির জাঙ্গাল নামে অভিহিত। তিনি এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন।
খান জাহান আলী (রহ.) এই অঞ্চলে পাথরের তৈরি মসজিদ নির্মাণ করেন। দূর-দূরান্ত থেকে পাথর নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তি এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে এখনও শোনা যায়।
খান জাহান আলীর আগমনকালে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গা ছিল বনাঞ্চল। বন-জঙ্গল সাফ করে তিনি ও তার অনুসারীরা দক্ষিণবঙ্গকে বসবাসের উপযোগী করে তোলেন। পুরো দক্ষিণাঞ্চল একরকম তার রাজ্য ছিল। কোনো বাধা ছাড়াই এই এলাকা তিনি শাসন করতে থাকেন। জনগণও তার নেতৃত্ব মেনে নেয়। তবে আঞ্চলিক শাসক হলেও প্রকট শাসকসুলভ জীবনযাপন কখনোই করেননি খান জাহান আলী। স্বাধীন বাদশাহদের মতো তিনি চলতেন না। এমনকি নিজের নামে কোনো মুদ্রার প্রচলনও তিনি করেননি। এছাড়া গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় তার সনদ নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেছেন তিনি। খান জাহান আলীর মৃত্যুর পরে তার প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক টাকশাল। পরবর্তী ৪০/৫০ বছর এই টাকশাল থেকেই বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা তৈরি হতো। বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ ছিল তার দরবারগৃহ। ষাট গম্বুজ মসজিদ হতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ছিল খান জাহান আলীর বসতবাড়ি। এখন সেটির কোনো অস্তিত্বই নেই, সেটি আসলেই দুর্বল স্থাপনা ছিলো অথচ তার পাবলিক স্থাপনাগুলোর ভিত ছিলো শক্তিশালী। যেগুলো এখনো বর্তমান।
খান জাহান আলী তার দীর্ঘ শাসনামলে এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ২০/২৫টি গ্রাম নিয়ে তার রাজধানী খলিফাতাবাদ গড়ে উঠেছিল। এখানে তিনি থানা, কাচারি, বিভিন্ন সরকারী দফতর, বিচারালয়, সেনানিবাস ইত্যাদি নির্মাণ করেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে দক্ষিণবঙ্গকে তিনি ভাগ করেন কয়েকটি ভাগে, ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন সুশাসন। তার এই ছোটখাট রাজ্যে তিনি কায়েম করেন ইসলামী হুকুমত। খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট এলাকায় ইসলাম প্রচারের সময় স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুদের বাধার সম্মুখীন হন খান জাহান আলী। তাদের বিরোধিতার কারণে ঐ এলাকার রণবিজয়পুর, ফতেহপুর, পিলঙ্গজ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুদের সাথে যুদ্ধ হয় মুসলিমদের। খান জাহান আলী তাদের পর্যুদস্ত করে নিজের শাসনক্ষমতা কায়েম করতে সমর্থ হন।
প্রায় ৪০ বছর স্বাচ্ছন্দ্যে দক্ষিণবঙ্গে রাজত্ব করেন খান জাহান আলী। এই পুরো এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন এই মহান সাধক। তাঁর সুশাসন ও বিনয়ী স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে এই এলাকার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। জীবনের শেষ দিনগুলো দরগায় বসে আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন তিনি। অনেক মূল্যবান বাণী তিনি দিয়ে যান নিজের প্রজ্ঞা ও সাধনালব্ধ জ্ঞান থেকে। এই মহান শাসক ও ধর্ম প্রচারক ৮৬৩ হিজরীর ২৬ জিলহজ্জ, ইংরেজি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।
খান জাহান আলীর মাজার সংশ্লিষ্ট বিশাল দিঘী যা ঠাকুরদিঘী নামে পরিচিত সেখানে খান জাহান একজোড়া কুমির ছেড়েছিলেন। কথিত আছে এই কুমির জোড়া তার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই কুমিরের বংশধররা সাতশ বছর ধরে কালাপাহাড় এবং ধলাপাহাড় নামে ছিল। তাদের সর্বশেষ বংশধর ২০১৫ সালে মারা গিয়েছে। এই কুমিরগুলোর ব্যতিক্রম হলো এরা কখনোই হিংস্রতা দেখায়নি। একেবারেই শান্ত ছিলো। মানুষ তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতো। এখনো সেই দিঘীতে কুমির আছে। তাদের পরে এনে ছাড়া হয়েছে এখানে। এরা শুরুতে কিছুটা হিংস্র থাকলেও এখন শান্ত আচরণ করে। তবে তারা আগের কুমিরদের মতো মানুষবান্ধব নয়।
গাজী খান জাহান আলী রহ. -এর মাজার থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরেই আছে তাঁর অফিস ও ক্যান্টনমেন্ট। এখান থেকেই তিনি খলিফতাবাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আমরা মাজার পরিদর্শন করে ওনার অফিস পরিদর্শনের জন্য বের হলাম। যা ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত। দশটাকা করে ভাড়া দিয়ে ষাট গম্বুজে যাওয়ার জন্য ব্যাটারি চালিত টমটম আছে। যদিও ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয় তবে এর গম্বুজ সংখ্যা ৮১ টি। মসজিদের ছাদে ৭৭ টি গম্বুজ। চারটি মিনারের উপর চারটি। সবমিলিয়ে ৮১ টি।
আভিধানিকভাবে ‘ষাটগম্বুজ’ অর্থ হলো ষাটটি গম্বুজ সম্বলিত। তবে সাধারণভাবে মসজিদটিতে একাশিটি গম্বুজ পরিলক্ষিত হয়। নামকরণের ব্যাপারে দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় নেভের উপর স্থাপিত সাতটি চৌচালা ভল্ট মসজিদটিকে ‘সাতগম্বুজ’ মসজিদ হিসেবে পরিচিত করে, কিন্তু সময় পরিক্রমায় এই ‘সাতগম্বুজ’ই ‘ষাটগম্বুজ’ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে, মসজিদের বিশাল গম্বুজ-ছাদের ভারবহনকারী মসজিদ অভ্যন্তরের ষাটটি স্তম্ভ সম্ভবত একে ‘ষাট খামবাজ’ (খামবাজ অর্থ স্তম্ভ) হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলে। এটি অসম্ভব নয় যে, এই ‘খামবাজ’ শব্দটিই পরবর্তীকালে বিকৃতরূপে ‘গম্বুজ’-এ পরিণত হয়ে মসজিদটিকে ষাটগম্বুজ হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি সম্ভবত বেশি গ্রহণযোগ্য। নামকরণের এই ব্যাখ্যা বাংলাপিডিয়ার।
খানজাহান (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ষাট গম্বুজ মসজিদ। পিরোজপুর-রূপসা মহাসড়কের পাশে খানজাহান আলী (রহ.) মাজার শরীফ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে সুন্দরঘোনা গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে পাকা সড়ক, পশ্চিম পাশে ঐতিহাসিক ঘোড়াদীঘি। এই দিঘীটির আয়তন প্রায় ৪০ একর। কথিত আছে এই দিঘী খনন করার পর বহুদিন এখানে পানি উঠে নি। এরপর খান জাহান আলী ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে দিঘীতে নামেন এবং পানিপূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করেন। এরপর পানি উঠতে থাকে। একারণে এই দিঘীর নাম ঘোড়াদিঘী।
ষাট গম্বুজের স্থাপত্য কৌশল আর লাল পোড়া মাটির উপর সুনিপুণ লতাপাতার অলঙ্করণে নানারূপে কারুকার্যখচিত মসজিদের ভেতর-বাইরে অভাবনীয় সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছে। বাংলাদেশে এতবড় ঐতিহাসিক মসজিদ আর নেই। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট। আর এর উচ্চতা ২২ ফুট। এর দেয়াল প্রায় ৯ ফুট পুরু। পূর্ব-পশ্চিমে ৭টা করে ১১টি সারিতে মোট ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। এর মধ্যে মাঝের এক সারিতে ৭ গম্বুজের উপরিভাগ চৌকোণা, বাকি ৭০টির উপরিভাগ গোলাকার। মসজিদের ভেতরে পূর্ব-পশ্চিমে ১০টি সারিতে ৬টা করে মোট ৬০টি স্তম্ভ রয়েছে। স্থানীয় লবণাক্ত জলবায়ুর প্রভাবে যাতে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে কারণে মসজিদের স্তম্ভের নিচে ৪ ফুট পর্যন্ত চারপাশে পাথরের আন্তরণ দেয়া হয়েছে। এসব পাথর বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছিল। মসজিদের ভেতর এমন জ্যামিতিক পদ্ধতিতে স্তম্ভগুলো বিন্যাস করা হয়েছে যে ইমাম সাহেবের দৃষ্টি মসজিদের যে কোনো প্রান্ত পর্যন্ত কোনো বাধা ছাড়াই পৌঁছতে পারে।
মসজিদে দরজা আছে মোট ২৫টি। এর একটি দরজা রয়েছে পশ্চিম দিকে, যা সম্ভবত জানাজার নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। ছাদ থেকে প্রায় ১৩ ফুট উঁচু মসজিদের চার কোণে চারটি মিনার আছে। সামনের মিনার দুইটির ভেতর দিয়ে ওপরে যাওয়ার জন্য ঘোরানো সিঁড়িপথ রয়েছে। এ দুইটি মিনারের ভেতরে খিলানের সাহায্যে নির্মিত একটি করে ছোট কক্ষ রয়েছে। এ কক্ষ দুইটির নাম ‘আন্ধার মানিক’ ও ‘শলক মালিক’। মিনার দুইটি আজান দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো বলে মনে হয় এবং একইসাথে এসব মিনারে চড়ে খানজাহানের সৈন্যরা পাহারা দিতেন, বহিঃশত্রুর চলাচলের ওপর নজর রাখতেন।
খানজাহান (রহ.) জৌনপুরের দক্ষ নির্মাণ শিল্পী এনে এই সুবিশাল সুরম্য মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। তবে কত সময় এবং কত লোক এর নির্মাণ কাজ করেছেন তা জানা যায়নি। এ মসজিদে প্রায় আড়াই হাজার লোক এক সঙ্গে নামায পড়তে পারে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে অযত্নে অবহেলায় মসজিদটি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। ১৯০৪ সালে ইংরেজ শাসনামলে পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এটি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। এরপর মসজিদটিকে কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের চারপাশে সীমানা প্রাচীর রয়েছে। পূর্ব দিকে ছিল প্রবেশ তোরণ। তোরণের দু'পাশের দু'টি কক্ষ ছিল কিন্তু এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই।
এটি শুধু মসজিদ ছিল না, খানজাহান (রহ.) এর দরবার ও সেনা ছাউনি হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এখান থেকেই তৎকালীন দক্ষিণাঞ্চলীয় স্বাধীন-সার্বভৌম ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র হাবেলী পরগণা বা খলিফাতাবাদ রাষ্ট্র পরিচালনা করা হতো। বর্তমান ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গণের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো জাদুঘর। ১৯৯৩ সালে এখানে জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। জাদুঘরে ২৮টি গ্যালারি রয়েছে। এখানে খানজাহান (রহ.)- এর আমলের শতাধিক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।
আমাদের দুপুরে মঈন সাহেবের বিয়ের দাওয়াত ছিলো। তাই এখানে বেশি সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পাইনি। একটার মধ্যেই খুলনায় ফেরার তাগিদ থেকে অনুপম এই নিদর্শন থেকে বিদায় নিই। ষাট গম্বুজের ঠিক উল্টোপাশেই রয়েছে সিঙ্গাইর মসজিদ। ধারণা করা হয় এটি মুঘল আমলে তৈরি করা হয়। ষাট গম্বুজের এতো কাছে আরেকটি ছোট মসজিদের কেন প্রয়োজন হয়েছিলো এই উত্তর আমি কারো কাছ থেকে পাইনি।
ষাটগম্বুজ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মধ্যযুগীয় এই মসজিদটি অবস্থিত। এটি একগম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদ সম্পূর্ণরূপে ইটের তৈরি। বাইরের পরিমাপ ১২.১৯ মি। এর দেওয়ালগুলি প্রায় ২.১৩ মি পুরু। মসজিদ ইমারতটির পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ আছে, আর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আছে একটি করে। পূর্বদিকের মাঝের প্রবেশপথটি পার্শ্বদেশে অবস্থিত প্রবেশপথের চেয়ে বড়। কিবলা দেওয়ালের ভেতরে আছে খাজকৃত খিলান মিহরাব যার বাইরের দিকে রয়েছে একটি আয়তাকার।
সিঙ্গাইর মসজিদ দেখে এসে বাসে করে আবার খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ইতোমধ্যে আকাশের অবস্থা পাল্টে গেলো। রোদযুক্ত আকাশ কুয়াশাছন্ন হয়ে পড়লো। যতই খুলনার দিকে আগাচ্ছি ততই শীত জেঁকে বসা শুরু করেছে। সোনাডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডের পাশেই আমরা হোটেল খুঁজতে থাকলাম। খুলনায় হোটেল ভাড়া চট্টগ্রাম বা কক্সবাজারের তুলনায় অনেক সস্তা। আমরা একটি বড় কক্ষ যেখানে তিনটি ডাবল বেড সেট করা আছে এমন একটি কক্ষ মাত্র ১৫০০ টাকায় ভাড়া করলাম। অর্থাৎ সাত জন থাকলাম ১৫০০ টাকায়। হোটেলের সার্ভিসও খারাপ ছিলো না।
হোটেলে ফ্রেশ হয়ে ও ব্যাগ রেখে দুটোর সময় গেলাম কমিউনিটি সেন্টারে। সেখানে আরো অনেক পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হলো। বরের সাথে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে পেট পুরে খেলাম। খাওয়া শেষে বের হলাম চা খাবো বলে। খুলনায় একটা বিষয় আমাকে অবাক করেছে। এখানে হোটেলগুলোতে চা পাওয়া যায় না। একটি হোটেলে চা চেয়েছি। ম্যানেজার বললেন এটা তো হোটেল, চা দোকান না। চা পাওয়া যায় টং দোকানগুলোতে।
টং দোকানে চা খাওয়ার পর আমার সহযাত্রীরা শহর ঘুরেছেন। আর আমি আইলসা মানুষ। হোটেলে এসে ঘুম দিয়েছি। এই শীতের মধ্যে শহরে ঘোরাঘুরি আমার পছন্দ হয়নি।