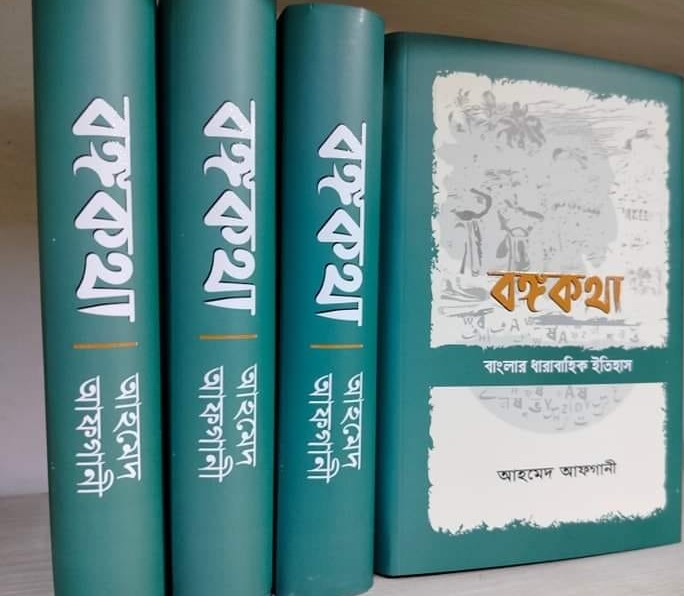মুনাফিকদের অব্যাহত অপবাদে এক সম্মানিতা নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরিক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর ধৈর্য দ্বারা তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার চরিত্রের নিষ্কলুষতা প্রমাণে মহান রব সূরা নূরের ১১ থেকে ২০ নং আয়াত নাজিল করেছেন।
আসুন আমরা সেই ঘটনা ভিকটিমের মুখেই শুনি।
সফরে যাওয়ার সময় তিনি (রাসূল সা.) তাঁর স্ত্রীদের নামে লটারী ফেলতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। ঘটনাক্রমে বনু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। আমি তাঁর সাথে গমন করি। আমি আমার পালকিতে বসে থাকতাম। যখন কাফেলা কোনো জায়গায় অবতরণ করতো তখন আমার পালকি নামিয়ে নেওয়া হতো। আমি পালকিতেই থাকতাম। আবার যখন কাফেলা চলতে শুরু করতো তখন আমার পালকি উটের ওপর উঠিয়ে দেয়া হতো।
যাই হোক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর আমরা মদিনার পথে ফিরতে শুরু করি। আমরা মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে পৌঁছলে রাত্রে যাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ভোরে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি এবং সেনাবাহিনীর তাবু থেকে বহু দূরে চলে যাই। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে আমি আবার ফিরে আসি। সেনাবাহিনীর তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে আমি গলায় হাত দিয়ে দেখি যে, গলায় হার নেই। আমি তখন হার খুঁজবার জন্যে আবার ফিরে যাই এবং হার খুঁজতে থাকি।
এদিকে সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে দিলো। যে লোকগুলো আমার পালকি উঠিয়ে দিতো তারা মনে করলো যে, আমি পালকির মধ্যেই রয়েছি, তাই তারা আমার পালকিটি উটের পিঠে উঠিয়ে দিলো এবং চলতে শুরু করলো। এখানে উল্লেখ্য যে, আমি খুবই শীর্ণকায় ও হালকা ছিলাম। তাই আমাকে বহনকারীরা পালকির মধ্যে আমার থাকা বা না থাকার বিষয়টি টেরই পেলো না। তাছাড়া আমি ছিলাম ঐ সময় খুবই অল্প বয়সের মেয়ে।
যাই হোক দীর্ঘক্ষণ পর আমি আমার হারানো হারটি খুঁজে পেলাম। সেনাবাহিনীর বিশ্রামস্থলে এসে আমি কোন মানুষের নাম নিশানাও পেলাম না। আমার চিহ্ন অনুযায়ী আমি ঐ জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে আমার উটটি বসা ছিল। সেখানে আমি এ অপেক্ষায় বসে পড়লাম যে, তিনি (রাসূল সা.) ও সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার না থাকার খবর পাবেন তখন অবশ্যই এখানে লোক পাঠাবেন। বসে থাকতে থাকতে আমার ঘুম এসে যায়।
হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. যিনি মূল কাফেলা থেকে পিছনে ছিলেন এবং তার দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া কিছু থাকলে নিয়ে আসা। তিনি যখন একজন আসলেন তখন আমাকে দেখতে পেলেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন বলে দেখামাত্রই চিনে ফেলেন এবং উচ্চ স্বরে বললেন, ইন্নালিল্লাহ। তার এ শব্দ শোনা মাত্রই আমার চক্ষু খুলে যায় এবং আমি চাদর দিয়ে আমার মুখটা ঢেকে ফেলে নিজেকে সামলিয়ে নিই।
তৎক্ষণাৎ তিনি তার উটটি বসিয়ে দেন এবং আমাকে উটে উঠতে বলেন। আমি উঠে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাই। তিনি উটকে উঠিয়ে চালাতে শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তার সাথে কোন কথা বলিনি। প্রায় দুপুর বেলায় আমরা আমাদের যাত্রীদলের সাথে মিলিত হই। এটুকু ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অভিশপ্তরা তিলকে তাল করে প্রচার শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা রচনাকারী ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।
মদীনায় এসেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এক মাস পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকি। এই সময়ে বাড়িতেই অবস্থান করি। এই সময়ের মধ্যে আমি নিজেও কিছু শুনিনি এবং কেউ আমাকে কোনো কথা বলেওনি। আলোচনা সমালোচনা যা কিছু হচ্ছিল তা লোকদের মধ্যেই হচ্ছিল। আমি ছিলাম এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর। তবে মাঝে মাঝে এরূপ ধারণা আমার মনে জেগে উঠতো যে, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ সা.-এর যে প্রেম ও ভালবাসা ছিল তা কমে যাওয়ার কারণ কি! অন্যান্য সময় আমি রোগাক্রান্তা হলে তিনি আমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাতেন, এই রোগের অবস্থায় আমি তা পেতাম না। এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখ হতাম, কিন্তু এর কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। তিনি আমার কাছে আসতেন, সালাম দিতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া তিনি আর কিছু বলতেন না। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেতাম। কিন্তু অপবাদদাতাদের অপবাদ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না।
ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং আরবদের প্রাচীন অভ্যাসমত আমরা আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার জন্যে দূরের মাঠে গমন করতাম। স্ত্রী-লোকেরা সাধারণত রাত্রেই যেতো। বাড়িতে পায়খানা তৈরি করতে মানুষ সাধারণভাবে ঘৃণাবোধ করতো। অভ্যাসমত আমি উম্মে মিসতাহ'র সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার জন্যে গমন করি। ঐ সময় আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই উম্মে মিসতাহ আমার আব্বার খালা ছিলেন।
আমরা যখন বাড়ি ফিরতেছিলাম তখন হযরত উম্মে মিসতাহর পা তার চাদরের আঁচলে জড়িয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। এটা আমার কাছে খুবই খারাপবোধ হয়। আমি তাকে বলি, তুমি খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করেছ, সুতরাং তাওবা কর। তুমি এমন লোককে গালি দিলে যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন উম্মে মিসতাহ বলে, “হে সরলমনা মেয়ে! আপনি কি কিছুই খবর রাখেন না?”
আমি বলি, ব্যাপার কী? সে উত্তরে বলে, “যারা আপনার উপর অপবাদ আরোপ করেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। তার একথায় আমি খুবই বিস্ময়বোধ করি এবং তাকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি খুলে বলতে অনুরোধ করি। সে তখন অপবাদদাতাদের সমস্ত কার্যকলাপ আমার কাছে খুলে বলে। এতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার উপর দুঃখ ও চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। এই চিন্তার ফলে আমি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ি।
আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বাবার বাড়ি গিয়ে খবরটা ভালোভাবে জানবো। সত্যিই কি আমার বিরুদ্ধে এসব গুজব রটে গেছে! কি কি খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমি সঠিকভাবে জানতে চাই। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সা. আমার নিকট আগমন করেন এবং সালাম দিয়ে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে আপনি আমার পিতার বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন! তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতার বাড়ি চলে গেলাম। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান! লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে কি কথা ছড়িয়ে পড়েছে? উত্তরে তিনি বলেনঃ “হে আমার কলিজার টুকরো! এটা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। এতে তোমার মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। যে স্বামীর কাছে তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন স্ত্রী খুবই প্রিয় হয় সেখানে এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।”
তখন আমি শোকে ও দুঃখে এতো মুষড়ে পড়ি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন থেকে যে আমার কান্না শুরু হয়, তা ক্ষণেকের জন্যেও বন্ধ হয়নি। আমি মাথা নীচু করে শুধু কাঁদতেই থাকি। কারণ আমি বুঝতে পারি আমার প্রতি রাসূল সা.-এর আচরণ পরিবর্তন করার কারণ অভিশপ্তদের অপবাদ। পানাহার, শোয়া, বসা, কথা বলা সবকিছুই বাদ দিয়ে আমার একমাত্র কাজ হয় চিন্তা করা, আর না হয় কাঁদা। সারারাত এভাবেই কেটে যায়। এক মুহূর্তের জন্যেও আমার অশ্রু বন্ধ হয়নি। দিনেও ঐ একই অবস্থা।
রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে ওহি আসতে বিলম্ব হয়। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। তাই তিনি পরামর্শ করার জন্য হযরত আলী রা. ও হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে ডেকে পাঠান। তিনি আমার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিবেন তার ব্যাপারে এ দু’জনের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত উসামা রা. স্পষ্টভাবে বলে দেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল সা.! আপনার এ স্ত্রীর কোনো মন্দগুণ আমার জানা নেই। আমাদের হৃদয় তাঁর মহব্বত, মর্যাদা ও তার সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে সদাবিদ্যমান রয়েছে।
তবে হযরত আলী রা. বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সা.! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার ওপর কোন সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে। আপনি তাঁকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। (হযরত আলী রা.-এর এই মন্তব্য এজন্য নয় যে, তিনি আয়িশা রা.-কে সন্দেহ করেছেন। বরং এজন্য যে, তাঁকে নিয়ে ব্যাপক কথা হচ্ছে। এজন্য রাসূল সা. বিচলিত হয়ে আছেন। এমতাবস্থায় তাঁকে তালাক দিয়ে রাসূল সা. যাতে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেন। কিছু উগ্রপন্থী শিয়ারা আলী রা.-এর এই মন্তব্যকে পুঁজি করে আয়িশা রা.-কে এখনো অপবাদ দেন। এটা সুস্পষ্ট কুফুরি। কারণ আয়িশা রা. চরিত্রের নিষ্কলুষতা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত)
আলী রা. রাসূল সা.-কে আরো বলেন, আপনার বাড়ীর চাকরানীকে জিজ্ঞেস করলে তার (আয়িশা) সম্পর্কে আপনি সঠিক তথ্য জানতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাৎ বাড়ির চাকরানী হযরত বুরাইরা রা.-কে ডেকে পাঠান। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, “তোমার সামনে আয়েশা রা.-এর এমন কোনো কাজ কি প্রকাশ পেয়েছে যা তোমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলেছে? উত্তরে হযরত বুরাইরা রা. বলেন, “আল্লাহর শপথ! তার এ ধরনের কোনো কাজ আমি কখনো দেখিনি। হ্যাঁ, তবে এটুকু শুধু দেখেছি যে, তাঁর বয়স অল্প হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে আটা মাখাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে বকরি এসে ঐ আটা খেয়ে নেয়। এছাড়া তাঁর অন্য কোনো ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়েনি।
এ ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না বলে ঐ দিনই রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে ওঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, “কে এমন আছে। যে আমাকে ঐ ব্যক্তির অনিষ্ট ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে ঐ কষ্ট আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে শুরু করেছে? আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে আমার এ পত্নীর মধ্যে ভাল গুণ ছাড়া মন্দ গুণ কিছুই নেই। তার সাথে যে ব্যক্তিকে তারা এ কাজে জড়িয়ে ফেলেছে তার মধ্যেও সততা ছাড়া আমি কিছুই দেখিনি। সে আমার সাথেই আমার বাড়ীতে প্রবেশ করতো।”
রাসূলুল্লাহ সা.-এর একথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ রা. দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমি প্রস্তুত রয়েছি। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তবে এখনই আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি। আর যদি সে আমাদের খাযরাজী ভাইদের মধ্যকার লোক হয় তবে আপনি নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ পালনে মোটেই ত্রুটি করবো না।”
তার একথা শুনে হযরত সা’দ ইবনে উবাদা রা. দাড়িয়ে যান। তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি খুবই সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু হযরত সা'দ বিন মুয়াজের রা.-এর ঐ সময়ের ঐ উক্তির কারণে তার গোত্রীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। তাই তিনি হযরত সা’দ ইবনে মুয়াজ রা.-কে সম্বোধন করে বলেনঃ “তুমি মিথ্যা বললে। না তুমি তাকে (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই) হত্যা করবে, না তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। সে যদি তোমার গোত্রের লোক হতো তবে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না।”
তাঁর একথা শুনে হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের রা. দাড়িয়ে যান। তিনি ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা.-এর ভাতুস্পুত্র। তিনি বলতে শুরু করেনঃ “হে সা’দ ইবনে উবাদা। আপনি মিথ্যা বললেন। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। আপনি মুনাফিক বলেই মুনাফিকদের পক্ষপাতিত্ব করছেন। এভাবে পাল্টাপাল্টি কথাবার্তায় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বরের ওপর থেকেই তাদের থামিয়ে দেন। অবশেষে উভয় দল নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।
আর এদিকে আমার অবস্থা এই ছিল যে, সারাদিন আমার কান্নাতেই কেটে যায়। আমার পিতা-মাতা ধারণা করলেন যে, এ কান্না আমার কলেজা ফেড়েই ফেলবে। বিষণ্ণ মনে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসেছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় আনসারের একজন স্ত্রীলোক আমাদের নিকট আগমন করে এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করে। আমরা সবাই এভাবেই বসেছিলাম এমতাবস্থায় অকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সেখানে আগমন ঘটে। তিনি সালাম দিয়ে আমার পাশে বসে পড়েন।
আল্লাহর কসম! যখন থেকে এই অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে নিয়ে ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার পাশে বসেননি। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অবস্থা ঐরূপই ছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁর ওপর কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই কোনো সিদ্ধান্তেই তিনি পৌঁছতে পারেননি। বসেই তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ “হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি সত্যিই সতী-সাধ্বী থেকে থাকো তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি প্রকৃতই তুমি কোনো পাপে জড়িয়ে পড়ে থাকো তবে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাওবা করো। কারণ বান্দা যখন কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হবার পর তা স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে থাকেন।”
রাসূলুল্লাহ সা. এটুকু বলার পর নীরব হয়ে যান। তাঁর একথা শুনেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। অশ্রু শুকিয়ে যায়। এমন কি এক ফোঁটা অশ্রুও চোখে ছিল না। প্রথমে আমি আমার পিতাকে বললাম যে, তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-কে জবাব দেন। কিন্তু তিনি বলেন, “আমি তাঁকে কী জবাব দেবো তা বুঝতে পারছি না।” তখন আমি আমার মাতাকে লক্ষ্য করে বলি, আপনি আমার পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তর দিন। কিন্তু তিনিও বলেন, “আমি তাঁকে কী উত্তর দেবো, তা খুঁজে পাচ্ছি না।
তখন আমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলাম। আমার বয়সতো তেমন বেশী ছিল না এবং কুরআনও আমার বেশি মুখস্ত ছিল না। আমি বললাম, আপনারা সবাই একটা কথা শুনেছেন এবং মনে স্থান দিয়েছেন। আর হয়তো ওটা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন আমি যদি বলি যে, আমি এই বেহায়াপনা কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি আসলেও এ পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত, কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো করে জানেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আল্লাহ বললেই আপনারা আমার কথা মেনে নিবেন।
এখন আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ত তো সম্পূর্ণরূপে আবু ইউসুফের (হযরত ইউসুফের আ. পিতা হযরত ইয়াকুবের আ.) মতো। তিনি বলেছেন, ‘সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল।" (১২:১৮)। এটুকু বলেই আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করি এবং আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি।
আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু আমি পবিত্র ও দোষমুক্ত, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ত থাকার কথা রাসূল সা.-কে অবহিত করবেন। কিন্তু আমি এটা কল্পনাও করিনি যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। তবে আমার ধারণা এরূপ হতো যে, আল্লাহ নবী সা.-কে হয়তো স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে দিবেন।
আল্লাহর শপথ! তখনও রাসূলুল্লাহ সা. নিজের জায়গা থেকে সরেননি এবং বাড়ির কোন লোকও বাড়ি হতে বের হননি এমতাবস্থায় তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়ে যায়। তাঁর মুখমণ্ডলে ঐসব নিদর্শন প্রকাশ পায় যা ওহীর সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ওহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হলে আমরা দেখতে পাই যে, তার চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রথম তিনি আমার দিকে চেয়ে বলেন,
“হে আয়েশা! তুমি খুশি হও। কারণ মহান আল্লাহ তোমার দোষমুক্ত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।” তৎক্ষণাৎ আমার মা আমাকে বলেন, “হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহর রাসূল সা.-এর সামনে দাঁড়িয়ে যাও।” আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবো না। তিনিই আমার দোষমুক্তি ও পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।
আমার এই ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব রা.-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে হযরত যয়নব রা. আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু তার আল্লাহর ভীতির কারণে তিনি আমার প্রতি কলংক আরোপ করা হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুকে রক্ষিত রাখছি, আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।”
অথচ তার বোন হিমনাহ বিনতে জাহাশ আমার সম্পর্কে বহুকিছু বলেছিল এবং আমার বিরুদ্ধে তার বোনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। তারপরও হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা. আমার সম্পর্কে একটিও মন্দ কথা উচ্চারণ করেননি। তবে তার ভগ্নী আমার অপবাদ রচনায় বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।”
এভাবেই আমাদের মা আয়িশা রা. তার ওপর আরোপিত অপবাদের ঘটনার বর্ণনা দেন। মহান রাব্বুল আলামীন এই ব্যাপারে সূরা নূরের ১১ নং আয়াতে বলেন,
//যারা এ মিথ্যা অপবাদ তৈরী করে এনেছে তারা তোমাদেরই ভিতরের একটি অংশ। এ ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য ভালই। যে এর মধ্যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে আর যে ব্যক্তি এর দায়-দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে তার জন্য তো রয়েছে মহাশাস্তি।//
হাদীসে মাত্র কয়েকজন লোকের নাম পাওয়া যায়। তারা এ গুজবটি ছড়াচ্ছিল। তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রিফা’আহ, মিস্তাহ ইবনে উসামাহ, হাস্সান ইবনে সাবেত ও হামনা বিনতে জাহশ। এর মধ্যে প্রথম দু’জন ছিল মুনাফিক এবং বাকি তিনজন মু’মিন। মু’মিন তিন জন বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে এ চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরা ছাড়া আর যারা কমবেশী এ গোনাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের নাম হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না।
এই ধরনের অপবাদ ছড়ানো এবং কেউ ছড়ালে মুমিন কী করা উচিত তা নিয়ে সূরা নূরের ১২ থেকে ২১ আয়াতে বলেন,
//যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলো না এবং বলল কেন না, ‘এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ’? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।আর যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, তার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই কঠিন আযাব স্পর্শ করত।
যখন এটা তোমরা তোমাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে, যাতে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না; আর তোমরা এটাকে খুবই তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর।আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন তোমরা কেন বললে না যে, ‘এ নিয়ে কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি অতি পবিত্র মহান, এটা এক গুরুতর অপবাদ’।
আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করবে না। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) আর নিশ্চয় আল্লাহ বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু।
হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।//
এই পুরো ঘটনায় যে লোকটি লজ্জায় অপমানে কুঁকড়ে গিয়েছেন তিনি হলেন আমাদের মা হযরত আয়িশা রা.-এর পিতা আবু বকর রা.। সাহাবারা এমনকি তাঁর আত্মীয়রাও যখন এসব নিয়ে কথা বলছে তখন তিনি নীরবে চোখের পানি ফেলতেন। এরমধ্যে মিস্তাহ ইবনে উসামাহ ছিল অপবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম। অথচ এই মিসতাহ আবু বকর রা.-এর আত্মীয় এবং তাঁর অনুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করেন। আল্লাহর ঘোষণার মাধ্যমে মিসতাহ মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হওয়ায় আবু বকর রা. তাকে যে সাহায্য করে আসছিলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আসছিলেন তা বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন।
এই ঘোষণার কারনে আল্লাহ তায়ালা পরে আরেকটি আয়াত অর্থাৎ সূরা নূরের ২২ নং আয়াত নাজিল করেন। সেখানে তিনি বলেন, //আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।//
তাঁর কসমের প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে শুনেই হযরত আবু বকর রা. সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, ‘আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা চাই, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দিবেন।’ কাজেই তিনি আবার মিসতাহকে সাহায্য করতে থাকেন এবং এবার আগের চেয়ে বেশি করে করতে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, হযরত আবু বকর রা. ছাড়াও আরো কয়েকজন সাহাবীও এ কসম করেছিলেন যে, যারা মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে তাঁরা আর কোনো সাহায্য-সহায়তা দেবেন না। এ আয়াতটি নাযিল হবার পর তারা সবাই নিজেদের কসম ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ মুনাফিক দ্বারা সৃষ্ট এ ফিতনার ফলে মুসলিম সমাজে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তা এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়।