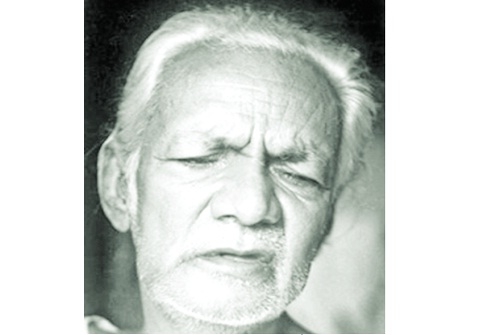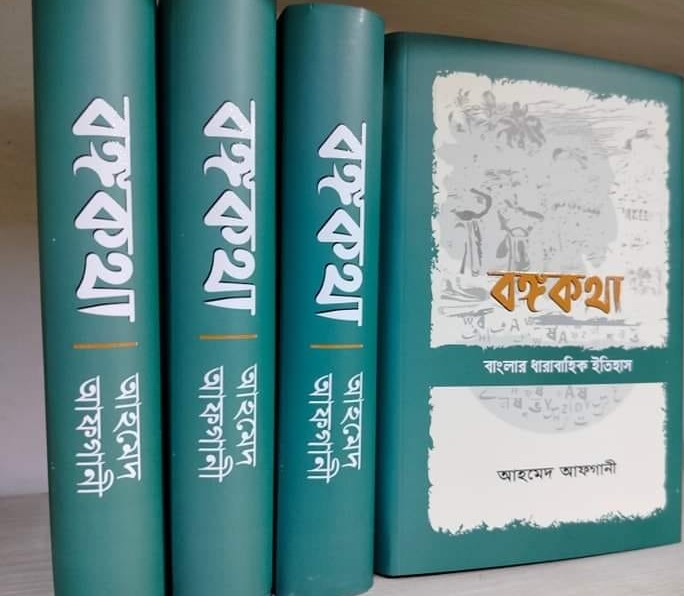২৬ ফেব, ২০২১
২৫ ফেব, ২০২১
জেএমবি, কর্নেল গুলজার ও পিলখানা হত্যাকাণ্ড
২০০২ সালের পর থেকে দেশে জঙ্গী কার্যক্রমের কিছু নজির পাওয়া যাচ্ছিল। এর মধ্যে কওমী মাদ্রাসাগুলোতে হরকাতুল জিহাদ একটিভ ছিল। হরকাতুল জিহাদের একটি ছেলে তাদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে নোয়াখালী জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েছিল আমাদের ক্লাসে। তাদের টার্গেট ছিল এই ছেলেকে ডাক্তার বানানো। পরে শুনেছি সে জার্মানী চলে গেছে। ডাক্তার সে হতে পারেনি।
একইসাথে আহলে হাদিস/সালাফি ঘরানার মধ্যে গড়ে ওঠে জেএমবি। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টে জেএমবি সারা দেশে বোমা হামলার মাধ্যমে তাদের অবস্থান জানান দেয়। তারা বোমা মেরে সরকার পতন করে দিবে। বিচারপতিদের টার্গেট করে খুন করতে শুরু করে। একইসাথে সাধারণ মানুষও খুন হতে থাকে।
তখন র্যাবের গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন কর্নেল গুলজার। স্বভাবতই চৌকস বাহিনী হিসেবে র্যাবের ওপরই দায়িত্ব আসে জঙ্গী দমনের। সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যারা জঙ্গী নামের এই সন্ত্রাসীদের অঙ্কুরেই বিনাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। না, কোনো ক্রসফায়ার নয়, প্রতিটি সন্ত্রাসীকে ধরে ধরে আইনের কাছে সোপর্দ করেছে র্যাব।
প্রতিটি জঙ্গী ধরতে কী পরিমাণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে র্যাব তা সন্ত্রাসী প্রধান আব্দুর রহমানের এরেস্টের বর্ণনায় দেখতে পাবেন। দেশের শীর্ষ জঙ্গিনেতা শায়খ আবদুর রহমান ধরা পড়েছিলেন ২০০৬ সালের ২ মার্চ। পরের বছরের (২০০৭) ৩০ মার্চ ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সিলেটের একটি বাড়ি থেকে ৩৩ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান চালিয়ে র্যাব সদস্যরা গ্রেফতার করেছিলেন আবদুর রহমানকে। সেই চূড়ান্ত অভিযানের আগেও চলে দীর্ঘ গোয়েন্দা তৎপরতা।
২০০৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর জেএমবির সামরিক প্রধান আতাউর রহমান সানি ধরা পড়ার পর র্যাবের পরবর্তী টার্গেট হন শায়খ আবদুর রহমান। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর কোনো হদিস মেলে না। সানিকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর র্যাব জানতে পারে, ঢাকার বনশ্রীর বাড়ি থেকে পালিয়ে শায়খ রহমান আশ্রয় নেন তাঁর পল্লবীর বাসায়। র্যাব সেখানে হানা দেওয়ার একটু আগেই তিনি চম্পট দেন। তবে সানির কাছ থেকে পাওয়া যায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু—জেএমবির মজলিশে শুরা সদস্য হাফেজ মাহমুদ জানে আবদুর রহমান সম্পর্কে অনেক তথ্য। ব্যস, শুরু হয়ে যায় হাফেজ মাহমুদকে গ্রেফতার অভিযান।
র্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা বলেন, অনেক কষ্টে তাঁরা জানতে পারেন, হাফেজ মাহমুদ নারকেল ব্যবসায়ী সেজে যশোরে অবস্থান করছে। কর্মকর্তারা তার ফোন নম্বর জোগাড় করেন। কিন্তু ফোনে কথা বলতে চায় না হাফেজ। র্যাবের সোর্স অন্য পরিচয়ে নানা টোপ ফেলতে থাকে। দীর্ঘ দুই মাস চলে ইঁদুর-বেড়াল খেলা। একপর্যায়ে র্যাবের সোর্স বিদেশি এনজিওর লোক পরিচয় দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখায়। বলা হয়, তাদের এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে একটি এনজিও অর্থ সাহায্য দিতে চায়। এবার বরফ গলে। হাফেজ মাহমুদ রাজি হয়ে যায়।
হাফেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর থেকেই তার মোবাইল ফোনে তীক্ষ্ণ� নজর রাখা হয়। দেখা যায়, র্যাবের সোর্সের সঙ্গে কথা বলার পরপরই হাফেজ অন্য একটি নম্বরে ফোন করে। কিন্তু তাদের কথা হয় সাংকেতিক ভাষায়। কিছুই বোঝা যায় না। একেক সময় ওই ব্যক্তির অবস্থান থাকে একেক জায়গায়। তবে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়—ওই ব্যক্তিই শায়খ রহমান। কিন্তু তার আগে ধরা দরকার হাফেজ মাহমুদকে।
র্যাব সোর্সের টোপ গিলে হাফেজ রাজি হয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাঠাগারে আলোচনায় বসা হবে। র্যাবের গোয়েন্দাপ্রধান লে. কর্নেল গুলজার ফাঁদ পাতেন ওই পাঠাগার ও তার আশপাশে। ওই দিন ভোরবেলা হাফেজ মাহমুদ যশোর থেকে নৈশকোচে ঢাকায় এসে নামে, সে খবরও পেয়ে যায় র্যাব। শুরু হয় গোয়েন্দাগিরির খেলা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারের সিঁড়ি ও প্রবেশমুখে র্যাব সদস্যরা হকার সেজে, টুপিবিক্রেতা সেজে বসে পড়েন।
বেলা সাড়ে ১১টার সময় দাড়িহীন, রঙিন চশমা আঁঁটা, সবুজ শার্ট পরা হাফেজ মাহমুদ আসে পাঠাগারের কাছে। সোর্সের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় পাঠাগারের ভেতরে। সেখানে ঘিরে ফেলেন কর্নেল গুলজার ও মেজর আতিক। কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাকে নিয়ে আসা হয় নিচে রাখা গাড়ির কাছে। একফাঁকে পালানোরও চেষ্টা করে হাফেজ। কিন্তু ব্যর্থ হয়।
তখনই শুরু হয় প্রবল জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু হাফেজ অটল। শায়খ রহমানের অবস্থান সে কিছুতেই জানাবে না। একপর্যায়ে শায়খের ফোন নম্বর জানাতে রাজি হয় সে। তার হাত থেকে মোবাইল সেট কেড়ে নিয়ে র্যাব কর্মকর্তারা দেখেন, একটি নম্বরে বারবার কথা বলা হয়েছে। র্যাবের আইটি শাখার মেজর জোহা খোঁজ করে দেখেন, এই নম্বরটি সিলেটের এমসি কলেজ টাওয়ার থেকে আসছে এবং টাওয়ারের আট বর্গকিলোমিটারের মধ্যেই ফোনটির অবস্থান। র্যাব মহাপরিচালক আবদুল আজিজ সরকারকে বিষয়টি জানানোর পর তিনি সিলেটে র্যাব-৯-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মোমিনকে নির্দেশ দেন, টাওয়ার থেকে আট বর্গকিলোমিটার দ্রুত ঘেরাও করে ফেলতে। কর্নেল মোমিন, মেজর শিব্বির ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হায়দার তখনই পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেন।
ঢাকা থেকেও রওনা হয় র্যাবের গোয়েন্দাপ্রধান লে. কর্নেল গুলজার উদ্দিনের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের একটি দল। ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে তাঁরা ঢাকা থেকে বের হয়ে সিলেট পৌঁছান রাত আটটায়। ওই দলে আরও ছিলেন মেজর আতিক, মেজর মানিক, মেজর জাভেদ, মেজর ওয়াসি, ক্যাপ্টেন তানভির ও ক্যাপ্টেন তোফাজ্জল। তাঁরা পৌঁছানোর আগেই সিলেট র্যাবের প্রায় আড়াই শ সদস্য নগরের টিলাগড় ও শিবগঞ্জের ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার প্রতিটি সড়ক ও গলিতে অবস্থান নেন।
এদের সঙ্গে ঢাকার বাহিনী যোগ দিয়ে রাত ১০টা থেকে শুরু করে চিরুনি অভিযান। আস্তে আস্তে পরিধি কমিয়ে এনে টিলাগড়, শাপলাবাগ, কল্যাণপুর, কালাশিল ও বাজপাড়া এলাকার প্রতি বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি। তল্লাশি চলাকালে র্যাবের হাতে থাকে শায়খ রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের ছবিসংবলিত লিফলেট। রাত ১২টার দিকে সিলেট নগর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে টুলটিকর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব শাপলাবাগ আবাসিক এলাকায় আবদুস সালাম সড়কের ২২ নম্বর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রথম বাধা পায় র্যাব। এক ব্যক্তি ছুরি হাতে তেড়ে এসে বলে, এগোলে খারাপ হবে। এরপর যা বোঝার বুঝে ফেলে র্যাব। গোটা অভিযান তখন কেন্দ্রীভূত হয় এই বাড়ি ঘিরে। এই বাড়ির নাম ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’।
র্যাব সদস্যরা দ্রুত ঘিরে ফেলেন সূর্য্যদীঘল বাড়ী। আশপাশের বাড়িতেও অবস্থান নেন অনেকে। নিয়ে আসা হয় ভারী অস্ত্র ও লাইফ সাপোর্ট জ্যাকেট। রাত পৌনে একটার দিকে মাইকে সূর্য্যদীঘল বাড়ীর লোকজনকে বেরিয়ে আসতে বললেও কেউ সাড়া দেয় না। আশপাশের বাড়ির লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়। রাত দেড়টার দিকে সূর্য্যদীঘল বাড়ির মালিক লন্ডনপ্রবাসী আবদুল হকের ছোট ভাই মইনুল হককে বাইরে থেকে ডেকে আনা হয়। তিনি মুখে মাইক লাগিয়ে ওই বাড়ির ভাড়াটে হূদয়ের নাম ধরে ডেকে দরজা খুলতে বলেন। তাতেও কাজ না হলে স্থানীয় ইউপি সদস্য নূরুন নবীকে দিয়ে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।
রাত দুইটার দিকে একবার বাড়ির পেছনে দরজা খোলার শব্দ হয়। র্যাব সদস্যরা সচকিত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধও হয়ে যায়। রাত দুইটা ১০ মিনিটে হঠাৎ করে বাড়ির ভেতর থেকে একজন বয়স্ক মানুষ ভারী গলায় দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করেন। কর্নেল গুলজার তখন আবদুর রহমানের নাম ধরে ডাক দিলে ভেতর থেকে ভারী গলার আওয়াজ আসে, ‘ওই কাফের! তোর মুখে আমার নাম মানায় না, আমাকে মুজাহিদ বল।’
এভাবে শেষ হয় প্রথম রাত। বুধবার সকাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় দফার চেষ্টা। ততক্ষণে ঢাকা থেকে গণমাধ্যমকর্মীরা সিলেটে হাজির হয়েছেন। টেলিভিশনে শুরু হয়েছে ‘লাইভ’ সম্প্রচার। টিভি সেটের সামনে বসে থাকে সারা দেশ। প্রথমে কিছুক্ষণ কাঁদানে গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে অবস্থা বোঝার চেষ্টা চলে। তাতে কাজ হয়নি। এরপর ডাকা হয় সিলেটের দমকলকে। তারা এসে পানি ছিটাতে থাকে বাড়ির ভেতরে। পুরো বাড়ি ভেসে যায় ফায়ার ব্রিগেডের পানিতে। কিন্তু আব্দুর রহমান অনড়। কাহিনি আরও লম্বা হতে থাকে। দিন গড়িয়ে রাত আসে।
কাহিনির ভেতরেও থাকে অনেক চমকপ্রদ ঘটনা। র্যাব ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা সারা রাত ধরে চেষ্টা চালিয়ে, একাধিকবার দীর্ঘ কথোপকথন চালিয়েও শায়খ রহমানকে আত্মসমর্পণে রাজি করাতে পারেন না। ততক্ষণে ভোরের আলো ফোটে গেছে। বুধবার সকাল নয়টা সাত মিনিটে বাড়ির ভেতরে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
পর পর চার-পাঁচটা বিস্ফোরণ ঘটে। দ্রুত নিয়ে আসা হয় দালান ভাঙার যন্ত্রপাতি। সাড়ে নয়টার দিকে ভাঙা হয় দক্ষিণের একটি জানালা। বৈদ্যুতিক কাটার এনে ছাদ ফুটো করা হয়। প্রথমে আয়না লাগিয়ে, পরে রশি দিয়ে ক্যামেরা নামিয়ে দেখা হয়, ভেতরে কী আছে। দেখা যায়, একটা বিছানা থেকে তার বেরিয়ে আছে। শুরু হয় হইচই—নিশ্চয় সারা বাড়িতে বোমা পাতা আছে। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা নিয়ে আসেন বড় বড় বড়শি। ফুটো দিয়ে নামিয়ে বিছানা টেনে তুলে দেখেন, সব ভুয়া—সাজানো আতঙ্ক।
দুপুরের দিকে র্যাবের কাঁদানে গ্যাসে টিকতে না পেরে বেরিয়ে আসেন শায়খের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। সিলেটের জেলা প্রশাসক এম ফয়সল আলম শায়খের স্ত্রী রুপাকে বলেন, ‘আপনি আপনার স্বামীকে বেরিয়ে আসতে বলুন।’ রুপা বলেন, ‘আমার কথা শুনবেন না। উনি কারও কথা শোনেন না।’ জেলা প্রশাসক পীড়াপীড়ি করলে শায়খের স্ত্রী মুখে মাইক লাগিয়ে বলেন, ‘উনারা বের হতে বলছেন, আপনি বের হয়ে আসেন।’ স্ত্রীর কথায়ও কান দেন না শায়খ।
বৃহস্পতিবার সকালে সিলেট জেলা প্রশাসক চূড়ান্ত হুমকির সুরে কঠোর সিদ্ধান্তের কথা জানালে অবশেষে জানালায় এসে উঁকি দেন শায়খ রহমান। এর মধ্যে শুরু থেকেই বিদ্যুৎ, টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। টিয়ার সেল নিক্ষেপ হতে থাকে কিছুক্ষণ পর পর। অবশেষে আব্দুর রহমান বেরিয়ে আসতে রাজি হন।
আমি যখন জেলে ছিলাম তখন সেখানে থাকা জেএমবি সদস্যদের থেকে জেনেছি কীভাবে তাদের অস্ত্র, বোমা নিয়ে আসা ও প্রশিক্ষণে তারা ভারতের মাটি ব্যবহার করেছে। তারা বলতো সেখানে বিএসএফ তাদের সহায়তা করতো। ভারত আমাদের দেশে জঙ্গী ঢুকিয়ে এদেশের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নিতে চেয়েছে, যেভাবে আমেরিকা আল-কায়েদাকে ব্যবহার করে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।
কিন্তু তাদের সেই কোটি কোটি ডলারের প্রজেক্টে ছাই ছিটিয়ে দিয়েছে র্যাবের নেতৃত্বে থাকা এদেশের সেনা অফিসাররা। ভারত তখন ভিন্ন পরিকল্পনা করে ২০০৭ সালের জানুয়ারির ১১ তারিখ সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদকে দিয়ে ক্ষমতা দখল করায়। এরপর ২০০৮ সালে পাতানো নির্বাচন দিয়ে হাসিনাকে ক্ষমতায় বসায়। এই বিষয়ে ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রণব তার আত্মজীবনীতে ইঙ্গিত করে।
ক্ষমতায় এসে হাসিনা সরকারের সাথে ষড়যন্ত্র করে তারা বিডিআর বিদ্রোহের নামে পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আর এই হত্যাকাণ্ডে যার লাশ সবচেয়ে বেশি বিকৃত করা হয় তিনি হলেন কর্নেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ। কারণ এই গুলজারের গোয়েন্দা পরিকল্পনাতেই সমন্ত জঙ্গী নেতা জীবিত এরেস্ট হয়। শায়খ আব্দুর রহমানের স্ত্রী রূপা হলেন আওয়ামী লীগ নেতা মীর্যা আযমের বোন।
এছাড়াও আমরা স্মরণ করতে পারি, ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে কুড়িগ্রামের রৌমারীতে বিডিআর-বিএসএফ যুদ্ধে ১৫০ জন বিএসএফ নিহত হয়। এর আগে পাদুয়ায় নিহত হয় ১৫ বিএসএফ। বিডিআর সেই সময়ের ডিজি মেজর জেনারেল এ এল এম ফজলুর রহমানের নির্দেশে ঐ যুদ্ধে অংশ নেয় বিডিআর জওয়ানরা।
ওই ঘটনার পর ভারতের সেই সময়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশবন্ত সিং উত্তপ্ত লোকসভায় জানান, ‘এ ঘটনার বদলা নেয়া হবে।’ এই বদলা কি সেই বদলা কিনা তাও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ওই ঘটনা দমনে কেন সেনাবাহিনী ডাকা হলো না এ নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। অনেক সাবেক সমর বিশেষজ্ঞ তখন বলেছিলেন, সেনাবাহিনী সেখানে মুভ করা হলে প্রাণহানির মত ঘটনা আরো কমানো যেত। কিন্তু সেনাবাহিনী মোতায়েন না করায় সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন সেই সময়ের আলোচিত সেনা প্রধান মইন উ আহমেদ। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, তখন তিনি নাকি নিজের ইচ্ছায় চাইলেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাহলে ইচ্ছাটা কার ছিল? এটাও একটা বড় প্রশ্ন হিসেবেই থেকে গেল।
পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ভারত ও আওয়ামীলীগ জেএমবি নিধনের প্রতিশোধ নেয়। মির্জা আজম এখানেই থেমে থাকে না। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে সেই হাফিজ মাহমুদকেও কারাগার থেকে বের করে ক্রসফায়ারের মাধ্যমে খুন করে। যে হাফিজ মাহমুদের মাধ্যমে গ্রেফতার হয়েছিল শায়খ আব্দুর রহমান।
২৩ ফেব, ২০২১
ফতওয়ার কিতাবের শেষ পাতা
২০ ফেব, ২০২১
ইসলামী কমিউনিজম ও তমদ্দুনে মজলিশ
 |
| তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেম |
১৫ ফেব, ২০২১
বিশ্বাসীদের কবি 'কবি আল মাহমুদ'
১৪ ফেব, ২০২১
শহীদ মাওলানা আবদুস সুবহান : একজন গণমানুষের নেতা
১২ ফেব, ২০২১
শহীদ হাসান আল বান্না : ইসলামী রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ ইমাম
১০ ফেব, ২০২১
দেওবন্দীদের সাথে মাওলানা মওদূদীর বিরোধ যেভাবে শুরু হয়
 |
| ছবি : মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী |
মেজর জিয়াউর রহমান ও গণহত্যা প্রসঙ্গ
১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ ও সত্যাসত্য প্রসঙ্গ