ইতিহাস
বাংলায় মুশরিকদের যাত্রা শুরু হয়েছে
আর্যদের হাতে। আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ থেকে যখন বিপুল নিন্মবর্ণের মুশরিক মুখ
ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তখন হিন্দুত্ববাদের উত্থান হয়। এখানে জাত-পাতকে কিছুটা মিনিমাইজ করে
মুশরিক জাতীয়তাবাদী ধারণা দেওয়া হয়েছে।
হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস ১৯২৩ সালে শুরু হয়, যখন ভিনায়ক দামোদর সাভারকর এটি প্রচলন
করেন। সাভারকর হিন্দুত্ববাদকে একটি জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে বর্ণনা করে,
যা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এবং সিখদের অন্তর্ভুক্ত করে। তবে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের
বহিরাগত হিসেবে বাদ দেওয়া হয়।
হিন্দুত্ববাদ হলো একটি রাজনৈতিক আদর্শবাদ যা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রচার করে এবং ভারতকে
একটি হিন্দু-প্রভাবিত রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে চায়। এটি আরএসএস (১৯২৫ সালে গঠিত) এবং
পরবর্তীতে বিজেপির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। হিন্দুত্ববাদের আরো উত্থান হয় ১৯৯২ সালের
বাবরি মসজিদ ভাঙচুর এবং ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির উত্থানের মাধ্যমে।
হিন্দুত্ববাদের প্রভাব
ও আফটারম্যাথ
হিন্দুস্থানে এর প্রভাব দিন দিন
বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে উপমহাদেশ জুড়ে ব্যাপক অস্থিরতা ও নানামুখী পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।
হিন্দুত্ববাদের উত্থানের ফলে সম্ভাব্য পরিণতিগুলো নিয়ে আলোচনা ও এই ব্যাপারে একটি সম্যক
ধারণা থাকা আবশ্যক বলে মনে করি।
১. সাম্প্রদায়িক
বিভাজন বৃদ্ধি:
হিন্দুত্ববাদ প্রচারের
মাধ্যমে মূলত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা লাগিয়ে যাচ্ছে RSS ও বিজেপি। মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা
না দেওয়া, তাদের ইন্ডিয়া থেকে বের করে দেওয়ার প্রচেষ্টা, গরু রাজনীতির মাধ্যমে মুসলিমদের
খুন করা নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।
২. সংস্কৃতিক আগ্রাসন:
হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের
বহুধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে একটি একক মুশরিক সাংস্কৃতিক পরিচয় চাপিয়ে
দিতে চায়, যা আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করছে। পৌত্তলিক মুশরিকরা ছাড়া
বাকীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বিলুপ্ত করার চেষ্টা চলছে। এই আগ্রাসন হিন্দুত্ববাদীরা
শুধু ইন্ডিয়ায় নয়, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও চালিয়ে যাচ্ছে।
৩. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:
হিন্দুত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ এবং সরকারের দমন-পীড়ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীদের
আস্ফালনে শুধু ইন্ডিয়ায় নয়, পুরো উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে।
৪. অর্থনৈতিক বিভাজন:
হিন্দুত্ববাদের পেছনে বৃহৎ
পুঁজি ও কর্পোরেট স্বার্থ জড়িত থাকায় অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিবেশী
রাষ্ট্রগুলোকে দাস বানিয়ে রাখার প্রবণতা বাণিজ্য ও অর্থণীতিতে বিরূপ প্রভাব তৈরি করছে।
৫. গণতন্ত্র বিলুপ্ত
হয়ে যাওয়ার আশংকা
হিন্দুত্ববাদ ভারতকে একটি
কর্তৃত্ববাদী ও অত্যাচারী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছে, যা গণমাধ্যম, আইনের শাসন এবং
সিভিল সোসাইটির স্বাধীনতা কমিয়ে দিয়েছে। শুধু ভারতে নয়, হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনে পুরো
উপমহাদেশে (বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল ও ভূটানে) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থাকে হুমকিতে
ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে হিন্দুত্ববাদ।
৬. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের
উৎপীড়ন
মুসলমান (১৪.২%), খ্রিস্টান
(২.৩%), এবং শিখ (১.৭%) উপর বাড়তি সহিংসতা এবং বৈষম্য, যেমন "বিফ লিঞ্চিং"
এবং আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধাচরণ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্মূল করার চেষ্টা চলছে ইন্ডিয়ায়।
৭. সামাজিক এবং আঞ্চলিক
অস্থিতিশীলতা
প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে,
বিশেষত পাকিস্তানের সাথে, সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়তে পারে, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত
করবে।
৮. মানবাধিকার লঙ্ঘন
অযথা গ্রেফতার, আদালতের
বাইরে হত্যা, এবং এনজিও-এর হস্তক্ষেপ সহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বৃদ্ধি, যা ২০২১ সালের
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রিপোর্টে উল্লেখিত।
৯. মুশরিক ধর্মীয় রাষ্ট্রের
ঝুঁকি
ভারত একটি পৌত্তলিক হিন্দু
ধর্মীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতায়
প্রভাব ফেলবে, বিশেষত যদি যোগি আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রী হন।
১০. ইন্ডিয়া বিচ্ছিন্ন
হয়ে যাওয়ার আশংকা
অর্থনৈতিক অসমতা বাড়তে পারে, যা ১২টি রাজ্যে বিদ্রোহ এবং উত্তর-পূর্বে ৪০টি সশস্ত্র
গ্রুপের উত্থানের সাথে জড়িত ।
১১. গাজওয়ায়ে হিন্দ
হিন্দুত্ববাদের উত্থানের ফলে মুহাম্মদ
সা. কর্তৃক ঘোষিত গাজওয়ায়ে হিন্দ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হতে থাকবে। এই ব্যাপারে নিয়ামত
উল্লাহ কাশ্মিরীর বক্তব্যও প্রণিদানযোগ্য।
এই প্রেক্ষিতে আমাদের
করণীয়
হিন্দুত্ববাদ ঠেকিয়ে আমাদের দেশে
ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা, সামাজিক সম্মতি, এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি
অঙ্গীকার প্রয়োজন। এটি কেবল আইন প্রণয়নের বিষয় নয়, বরং সমাজের সকল স্তরে ইসলামী
নীতির প্রয়োগ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা।
নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:
১. শিক্ষা ও সচেতনতা
বৃদ্ধি
ইসলামী শিক্ষার প্রসার: জনগণের
মধ্যে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য মসজিদ,
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।
নৈতিক শিক্ষা: ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত
করা।
জনসচেতনতা: সেমিনার, ওয়াজ মাহফিল ও সামাজিক মাধ্যমে ইসলামী জীবনধারার গুরুত্ব
তুলে ধরা।
২. ইসলামী শাসনব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠা
শরিয়াহভিত্তিক আইন: যেসব স্থানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান)
এসব অঞ্চলে রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় শরিয়াহর নীতি প্রয়োগ, যেমন- অর্থনৈতিক, পারিবারিক,
ও ফৌজদারি আইন। তবে এটি জনগণের সম্মতি ও পরিস্থিতি বিবেচনায় করতে হবে।
ন্যায়বিচার: ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, যেখানে সবাই সমান ন্যায় পায়
এবং দুর্নীতি দূর করা হয়।
শূরাভিত্তিক (পরামর্শ) শাসন: শাসনব্যবস্থায় শূরার নীতি প্রয়োগ, যেখানে জনগণের
প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়।
৩. অর্থনৈতিক সংস্কার
ইসলামী অর্থনীতি: সুদমুক্ত ব্যাংকিং,
জাকাত ব্যবস্থা, ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন প্রতিষ্ঠা।
দারিদ্র্য দূরীকরণ: জাকাত ও সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা এবং কর্মসংস্থান
সৃষ্টি।
ন্যায্য বাণিজ্য: ব্যবসায় সততা ও ইসলামী নীতি অনুসরণ।
৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
সংস্কার
পরিবার ব্যবস্থা: ইসলামী পারিবারিক
আইন ও মূল্যবোধের প্রচার, যেমন- বিবাহ, তালাক, ও উত্তরাধিকার বিষয়ে শরিয়াহ মেনে চলা।
নৈতিকতা ও পর্দা: সমাজে হায়া (লজ্জা) ও পর্দার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা।
অনৈসলামী প্রথা দূরীকরণ: কুসংস্কার, শিরক, ও বিদআতের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি।
৫. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ও নেতৃত্ব
সৎ নেতৃত্ব: ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহভীরু
ও জ্ঞানী নেতা নির্বাচন।
দুর্নীতি দূরীকরণ: স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা।
জনগণের অংশগ্রহণ: জনগণের মতামত ও সমর্থন নিশ্চিত করা, যাতে ইসলামী ব্যবস্থা
জোরপূর্বক না হয়।
৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: অন্যান্য
রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী নীতি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।
দাওয়াহ: বিশ্বব্যাপী ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা।
৭. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত
সংস্কার
তাকওয়া বৃদ্ধি: ব্যক্তি ও সমাজের
মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি বৃদ্ধি।
ইবাদতের প্রচার: নামাজ, রোজা, জাকাত, ও হজের মতো ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা।
আদর্শ সমাজ: ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী একটি ন্যায়, শান্তি ও সমৃদ্ধিময় সমাজ গঠন।
৮. কিছু বিষয়ে সতর্কতা:
জোরপূর্বক প্রয়োগ নয়: ইসলাম কখনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ধর্ম নয়। জনগণের
হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস জাগাতে হবে।
স্থানীয় সংস্কৃতি বিবেচনা: ইসলামী নীতি প্রয়োগের সময় স্থানীয় সংস্কৃতি ও
ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে, যতক্ষণ তা শরিয়াহবিরোধী নয়।
আধুনিকতার সাথে ভারসাম্য: আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ইসলামী নীতির সমন্বয়
করা।
হিন্দুত্ববাদকে মোকাবিলা
করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভূখণ্ডে শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বরং জনগণের হৃদয়ে ইসলামের
প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা জরুরি। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যেখানে
ধৈর্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর উপর ভরসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

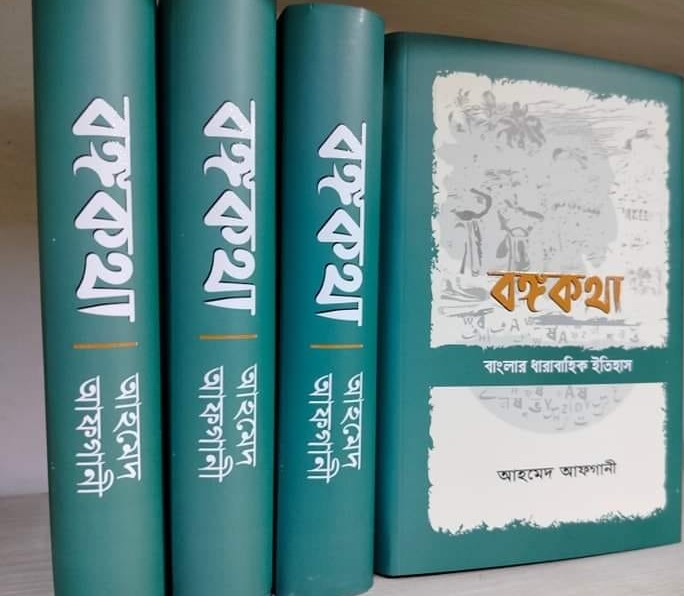




0 comments:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন