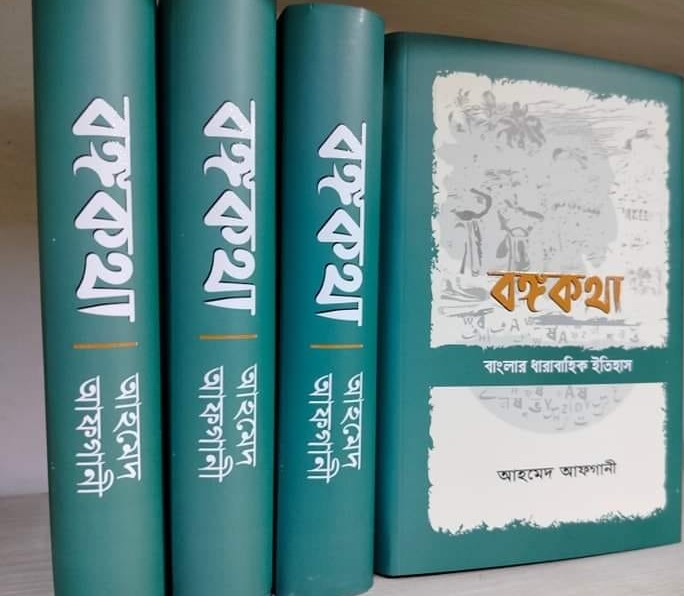ঘটনাটি রাসূল সা. পৃথিবীতে আসার আগেরকার। ইয়েমেনে কিছু লোক খুব ধনী ছিলো। তাদের গ্রাম ছিল যারওয়ান, যা সানাআ হতে ছয় মাইল দূরের অবস্থিত। তারা তাদের বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল বিশাল ফলের বাগান। ফলের চাষ ও ব্যবসা করে তারা বিশাল সম্পদের মালিক হয়। তারা যদিও বিশ্বাসী ছিলো তবে তারা ভালো প্রকৃতির লোক ছিলো না। তারা তাদের সম্পদ থেকে ফকির মিসকিনদের জন্য খরচ করতে চাইতো না। তাদের সম্পদে থাকা গরীবদের হক তারা আত্মসাৎ করতো।
কিন্তু তাদের পিতার নীতি এই ছিলো ভিন্ন। তিনি বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলো আল্লাহর নামে সাদাকা করে দিতেন। তাদের পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বললো, “আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতোগুলো ফল ও শস্য প্রতি বছর এদিক-ওদিক দিয়ে দিতে পারতেন না।
আমরা যদি এগুলো ফকীর মিসকীনদেরকে প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তবে দ্রুতই আমরা আরো ধনী হয়ে যাবো।” তারা মিসকিনদের ফসল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বারংবার নিষেধ করেছিলো এরকম সিদ্ধান্ত নিতে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির করা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি অপরাপর সঙ্গীদের সম্পদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞ থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন যে, তাদের আঙ্গুরের বাগান ছিল। যেহেতু তারা মিসকিনদের কোন ফল দিবে না তাই তারা চেয়েছিলো খুব সকালেই ফল আহরণ করে নিতে। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে তাদের বাগানের দিকে চললো যাতে কেউ শুনতে না পায় এবং গরীব মিসকীনরা কোন টের না পায়। তারা একে অপরকে বলেছিলো, 'তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরীব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবে না।’ এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করলো।
তারা মনে করেছিলো তাদের বাগান চিরদিনই তাদের থাকবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়ীতে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা তাদের বাগানে গিয়ে দেখে সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর কোন মূল্য নেই। গাছগুলো জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে গেছে। পুরো বাগানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
এই দৃশ্য দেখে তারা প্রথমে ভেবেছিলো তারা ভুল করে অন্য কোন বাগানে এসে পড়েছে। আবার দিশেহারা হয়ে তারা বললো, ‘আমাদের বাগান তো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থী ছিল সে তাদেরকে বললো, “দেখো, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং প্রশংসা করছো না? এ কথা শুনে তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি।
যখন শাস্তি পৌঁছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করলো, যখন আযাব এসে পড়লো তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিলো। অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো এবং বলতে থাকলো। আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি।
তারপর তারা সবাই বললো, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে। অতঃপর তারা বললোঃ ‘সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। অর্থাৎ দুনিয়াতেই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।
এই ঘটনার বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সূরা ক্বালামের ১৭ থেকে তেত্রিশ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,
//আমি তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে গিয়ে নিজেদের বাগানের ফল আহরণ করবে। তারা এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রমের সম্ভবনা স্বীকার করেছিলো না। অতঃপর তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি বিপর্যয় এসে সে বাগানে চড়াও হলো। তখন তারা ছিলো নিদ্রিত। বাগানের অবস্থা হয়ে গেলো পোড়া ফসলের মতো। ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ফসলের মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ো।
সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা নীচু গলায় একে অপরকে বলছিলো, আজ যেন কোনো অভাবী লোক বাগানে না আসতে পারে। তারা কিছুই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে এমনভাবে দ্রুত সেখানে গেল যেন তারা (ফল আহরণ করতে) সক্ষম হয়। কিন্তু বাগানের অবস্থা দেখার পর বলে উঠলো, আমরা রাস্তা ভুলে গিয়েছি। তাও না- আমার বরং বঞ্চিত হয়েছি।
তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি? তোমরা তাসবীহ করছো না কেন? তখন তারা বলে উঠলো, সুবহানআল্লাহ। বাস্তবিকই আমরা গোনাহগার ছিলাম।
এরপর তারা সবাই একে অপরকে তিরষ্কার করতে লাগলো। অবশেষে তারা বললো, "আমাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল বাগান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে রুজু করছি।//
মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “তোমরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকো। জেনে রেখো যে, পাপের কারণে বান্দাকে ঐ রিযিক হতে বঞ্চিত রাখা হয় যা তার জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছিল।” অতঃপর তিনি বলেন, ঐ লোকগুলো তাদের পাপের কারণে তাদের বাগানের ফল ও শস্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়েছিল।
১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা "আমি তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে" এখানে তাদের বলতে মক্কাবাসীদের বুঝিয়েছেন এবং উদাহরণ হিসেবে বাগান মালিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষা হয়ে রইলো। আল্লাহর নিয়ামত লাভ করেও তারা সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটির কথাও তারা যথাসময়ে মেনে নিয়নি। অবশেষে তারা সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
যখন তাদের সবকিছুই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে তখনই কেবল তাদের চেতনা ফিরেছে। এ উদাহরণ দ্বারা মক্কীবাসীকে এভাবে সাবধান করা হয়েছে যে, রাসুল সা.-কে রসূল করে পাঠানোর কারণে তোমরাও ঐ বাগান মালিকদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। তোমরা যদি তাকে না মানো তাহলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য আখেরাতে যে শাস্তি ভোগ করবে তাতো এর চেয়েও বেশি কঠোর।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিদায়াতের পথে রাখুন। ঈমানের যে দৌলত দান করেছেন আমরা যেন তার জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের যথাযথ আনুগত্য করি। মানুষের হক প্রদানে যাতে কোন কার্পণ্য না করি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের কবুল করুন। আমীন।