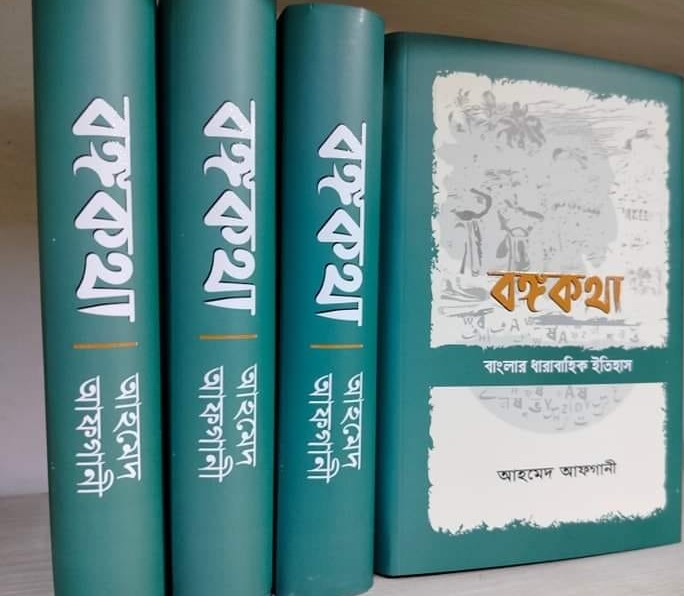৩০ নভে, ২০২১
২৯ নভে, ২০২১
খিলাফত পর্ব-০১ : রাশিদুন খিলাফতের যুগ শুরু হলো যেভাবে
মুহাম্মদ সা.-এর মৃত্যুর পর বনু সাঈদা গোত্রে খাজরাজদের একদল লোক সমবেত হলো। তারা সা'দ বিন উবাদার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাকে আমীর ঘোষণা করলো। আলী রা.-এর ঘরে ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.। তারা এখন এসব ঝামেলায় জড়াতে চাননি। একদল লোক তাদের আনুগত্য করলো। তারা সম্ভবত আলী রা.-কে পরিবারের সদস্য হিসেবে নেতা মানতে চেয়েছিল।
১৯ নভে, ২০২১
শহীদ তিতুমীর ও আমাদের করণীয়
১৭ নভে, ২০২১
মাওলানা ভাসানীর সাতকাহন
১২ নভে, ২০২১
হিরো থেকে যেভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন ইয়াসির আরাফাত
এই আলোচনা শুরু করার জন্য একটু অতীত থেকে শুরু করা দরকার। তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ১৮৮০ সালের দিকে ফিলিস্তিন ছিল তুর্কি সালতানাতের অধীনে। তখন ইউরোপিয়ানরা বিশেষত ব্রিটেন মুসলিমদের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটায়। আরব-অনারব ইস্যু তুলে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। অভিজাত আরবরা নিজেদের সবসময় মুসলিমদের নেতা মনে করতো। এটাকে ব্যবহার করে তারা আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটায়। মুসলিমদের নেতা হিসেবে তারা তুর্কিকে অস্বীকার করতে থাকে।
অন্যদিকে তখন ইহুদীরা বেশি ছিল রাশিয়া, জার্মানী ও পোল্যান্ডে। আর পুরো ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে তাদের অবস্থান ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সব রাষ্ট্রেই কমবেশি তারা নির্যাতিত হতো। তখন পৃথিবীতে সুপার পাওয়ার ছিল ব্রিটেন ও উসমানীয় সালতানাত। নির্যাতিত ইহুদীরা এই দুই রাষ্ট্রে পালিয়ে আসতে থাকে। ব্রিটেন শরনার্থীদের আশ্রয় দিতে না চাইলে সবাই একযোগে তুর্কি অঞ্চলে আসতে থাকে। তুর্কি সালতানাত তখন বিশাল। ইহুদী শরনার্থীরা বিচ্ছিন্নভাবে তুর্কি সালতানাতে প্রবেশ করে এবং যার যেখানে সুবিধা সেখানে বসবাস শুরু করে।
ইহুদীদের এই দুরবস্থা নিয়ে তাদের মধ্যে থাকা পণ্ডিতেরা কাজ শুরু করে। অনেকেই কাজ করেন, তবে এর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন থিয়োডোর হার্জেল। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত তার পুস্তিকা 'ডের জুডেনস্টাটে' তিনি বিংশ শতাব্দীতে একটি ভবিষ্যৎ স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখেন এবং এর জন্য তিনি স্থান নির্ধারণ করেন জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনকে।
তার এই পুস্তক ইহুদীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তবে কিছু ইহুদী এর বিরোধীতা করে। তাদের ধর্মীয় বিবেচনায় তাদের রাষ্ট্রগঠন তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এই গ্রুপ ছোট হলেও তারা এখনো বিদ্যমান। আবার কিছু ইহুদী রাষ্ট্রগঠনের বিরোধী ছিল এই মর্মে যে, তুর্কি খলিফা এই রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াতে রাগান্বিত হয়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে এবং তুর্কি থেকে উচ্ছেদ করবে এই ভয়ে। সেসময় ফিলিস্তিন অঞ্চল তুর্কি সালতানাতের মধ্যে অবস্থিত ছিল।
সব বাধা উপেক্ষা করে হার্জেল তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একনিষ্ঠ ছিল। ১৮৯৭ সে সর্বপ্রথম ইহুদী সমাবেশ করে এবং তার ধারণা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। তার এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা জায়নবাদ নামে পরিচিত হয়। হিব্রু ভাষায় জায়ন মানে জেরুজালেম। শুরুতে শুধু ইহুদীরাই শুধু জায়নবাদী থাকলেও এখন যারা ইহুদী রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান করে তারা সবাই জায়নবাদী হিসেবে পরিচিত। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে চাইলে যারা মনে করে (সে যে ধর্মেরই হোক না কেন) জেরুজালেম ইহুদীদের অধিকারে থাকবে তারাই জায়নবাদী।
এই জায়নবাদীদের একটি কুমিরের সাথে তুলনা করে সাবেক তুর্কি প্রধানমন্ত্রী ড. নাজিমুদ্দিন এরবাকান বলেন, //জায়নবাদ হল একটি কুমিরের মত।এর উপরের চোয়াল হল আমেরিকা আর নিচের চোয়াল হল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এর জিহ্বা আর দাঁত হল ইসরাঈল। এবং এর শরীর সহ অন্যান্য অঙ্গসমূহ হল মুসলিমদেশ সমূহ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী, মিডিয়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংগঠন।//
থিওডোর হার্জেল ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য কলোনী বা আবাসভূমি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে তুর্কি সুলতান আব্দুল হামিদ সানির সাথে দেখা করে। বিনিময়ে উসমানীয় সালতানাতের একটি বড় ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। আব্দুল হামিদ তাতে রাজি হননি এবং তাদের দেশ দখলের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে জেরুজালেম ও তার আশে পাশে জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন।
১৯০৪ সালে হার্জেলের মৃত্যুর পর জায়নবাদকে নেতৃত্ব দেন ইহুদী ধনকুবের ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তক ব্যারন রথচাইল্ড। এদিকে উসমানীয় সালতানাত ভাঙতে মরিয়া ছিল ব্রিটেন। মুসলিমদের ঐক্য নষ্ট করে তারা। সালতানাতের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে। তাদেরকে বুঝানো হয় অনারব তুর্কি ছোট জাত। তাদের অধিকার নেই আরব মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার। আরবদের কাছেই নবী এসেছে তাই আরবরাই মহান। নেতৃত্বের হকদার তারা। ব্রিটেন আরব নেতা শরীফ হুসেইনকে মুসলিম বিশ্বের নেতা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
অন্যদিকে উসমানীয় ভূমি দখলের পর ভাগ বাটোয়ারা করে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে রিভাল চুক্তির মাধ্যমে। আর ইহুদীদের সাথে চুক্তি করে জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে তাদেরকে একটি রাষ্ট্র তৈরিতে সাহায্য করবে। এই বিষয়ে ব্রিটেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলফোর জায়নবাদী নেতা রথচাইল্ডকে একটি পত্র দেন, যা বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত।
মোটকথা ব্রিটেন আরব নিয়ে একইসাথে তিন পক্ষের সাথে তিনটি চুক্তি করে
(ক) বৃটেন আরব নেতাদের আশ্বাস দিল, তারা কুরাইশ বংশের শরীফ হুসেইনের মাধ্যমে আরব রাজ্যের কর্তৃত্ব পাবে।
(খ) ফ্রান্স এবং বৃটেন চুক্তি করলো, ঠিক ঐ এলাকাগুলোই বৃটেন এবং ফ্রান্স ভাগ করে নিবে। সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান পাবে ফ্রান্স অন্যদিকে হেজাজ, ফিলিস্তিন, জেরুজালেমসহ বাকী আরব ব্রিটেন পাবে।
(গ) জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে ইহুদীদের একটি রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ দেওয়া হবে।
১ম বিশ্বযুদ্ধে ফিলিস্তিনের আরব জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা ব্রিটেনকে সাপোর্ট করে। তাদের সহায়তায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স সহজে মধ্যপ্রাচ্য দখল করে। উসমানীয় সৈন্যরা পরাজিত হয়ে চলে যায়। অন্যদিকে ইহুদীরা চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেনকে প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও গোয়েন্দা সুবিধা দেয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি উসমানীয় সরকারে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদী গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিল। এর ফলে রাষ্ট্রীয় তথ্য ব্রিটেনের কাছে চলে যেত। ১ম বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে উসমানীয় সেনাদের পরাজয়ে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা ও ইহুদীরা ভালো ভূমিকা রেখেছে। তাই এই ফ্রন্টে সহজেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সেনারা জয়লাভ করে।
১৯১৭ সালে থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভূমি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইহুদীদের কাছে ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ফিলিস্তিনের জমিতে তাদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ করে দিবে। সেজন্য ইহুদীরা কাজ করতে থাকে। সারাবিশ্ব থেকে চাঁদা তুলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনের গরিব মুসলিমদের থেকে জমি ক্রয় করা শুরু করে। কিছু ক্ষেত্রে জোর করেও দখল নিতে থাকে। সারা পৃথিবীকে উদ্বাস্তু ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আনা হয় ও তাদের পুনর্বাসন করা হয়।
সিরিয়া থেকে আসা উসমানীয় সেনা কমান্ডার ইজেদ্দিন আল কাসসাম ব্রিটেন ও ইহুদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও পরে সশস্ত্র আন্দোলন করেন। তিনি মুসলিমদের জমি বিক্রয়ের ব্যাপারেও সতর্ক করেন।
১৯৩৩ সালের পর থেকে জার্মানির শাসক হিটলার ইহুদিদের প্রতি কঠোর হতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে জাহাজে করে সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার ইহুদি অভিবাসী ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে আসতে থাকে। তখন ফিলিস্তিনী আরবরা বুঝতে পারে যে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে।
ইহুদীবাদীদের তিনটি সন্ত্রাসী সংগঠন ছিল হাগানাহ, ইরগুন ও স্ট্যার্ন গ্যাং। যারা হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ আর ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির মাধ্যমে নিরীহ ফিলিস্তিনদের বাধ্য করে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে। আল কাসসাম তাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৩৫ সালে এক খন্ডযুদ্ধে আল কাসসামকে খুন করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী।
আল কাসসামের শাহদাতের মধ্য দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের টনক নড়ে। ১৯৩৬-১৯৩৯ সালে ফিলিস্তিনী আরবরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিদ্রোহ করে। কিন্তু আরবদের সে বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেছে ব্রিটিশ সৈন্যরা।
বরাবরের মতো ব্রিটেন আরব এবং ইহুদী- দু'পক্ষকেই হাতে রাখতে চেয়েছে। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি ব্রিটেনের সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়েছিল পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পঁচাত্তর হাজার ইহুদি অভিবাসী আসবে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে। অর্থাৎ সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছিল। ব্রিটেনের এ ধরনের পরিকল্পনাকে ভালোভাবে নেয়নি ইহুদীরা। তারা একই সাথে ব্রিটেন এবং আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করে।
১৯৪০ সালে ৩২ হাজার ইহুদি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যুক্ত ছিল। সেই ইহুদি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে ব্রিটেন এবং আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এদিকে ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেন ইহুদীদের সব দাবি মেনে নিয়ে আপাতত বিদ্রোহ থামায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনীর দ্বারা বহু ইহুদি হত্যাকাণ্ডের পর নতুন আরেক বাস্তবতা তৈরি হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যেসব ইহুদি বেঁচে ছিলেন তাদের জন্য জন্য কী করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
তখন ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে ইহুদীদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা আরো জোরালো হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন পৃথিবীতে তার একক কতৃত্ব হারায়। নতুন পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার উত্থান হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ইসরায়েল রাষ্ট্রের পক্ষে জোরালো অবস্থান তুলে ধরেন। ট্রুম্যান চেয়েছিলেন হিটলারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া এক লক্ষ ইহুদিকে অতি দ্রুত ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে জায়গা দেয়া হোক। কিন্তু ব্রিটেন বুঝতে পারছিল যে এতো বিপুল সংখ্যক ইহুদিদের ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে নিয়ে গেলে সেখানে গৃহযুদ্ধ হবে।
ব্রিটেনের গড়িমসি দেখে ইহুদিদের সশস্ত্র দলগুলো ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর ফিলিস্তিনের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানো শুরু করে। তখন ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে জাহাজে বোঝাই হয়ে আসা হাজার-হাজার ইহুদিদের বাধা দেয় ব্রিটিশ বাহিনী। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। ইহুদি সশস্ত্র দলগুলো ব্রিটিশ বাহিনীর উপর তাদের আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পরিস্থিতির তৈরি করা যাতে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের জন্য ব্রিটেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সমাধানের জন্য ব্রিটেনের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। এরপর বাধ্য হয়ে ব্রিটেন বিষয়টিকে জাতিসংঘে নিয়ে যায়।
১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে দু'টি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি আরবদের জন্য। ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। স্বভাবতই আরবরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তারা জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের ভূখণ্ডে তখন ইহুদিরা বিজয় উল্লাস শুরু করে। অবশেষে ইহুদিরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেল। কিন্তু আরবরা অনুধাবন করেছিল যে কূটনীতি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদীরা রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেও মুসলিমরা তা পারেনি। ইহুদিরা সংগঠিত হয়ে গেল। অন্যদিকে মুসলিমদের কোনো কেন্দ্রীয় নেতা ছিল না। শরীফ হুসেইন জর্ডানের নেতৃত্ব পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন।
ইসরাঈল রাষ্ট্র গঠনের পর আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইহুদিদের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল তাদের বিচক্ষণ নেতৃত্ব। এর বিপরীতে আরবদের কোন নেতৃত্ব ছিলনা। ইহুদীরা বুঝতে পেরেছিল যে নতুন রাষ্ট্র গঠনের পর আরবরা তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য আগে থেকেই তৈরি ছিল ইহুদীরা। জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ বেধে যায়। যেহেতু আরবদের মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না সেজন্য ইহুদিরা একের পর এক কৌশলগত জায়গা দখল করে নেয়। ইহুদিদের ক্রমাগত এবং জোরালো হামলার মুখে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে ফিলিস্তিনীরা। তারা বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে থাকে।
তখন ফিলিস্তিনের একজন নেতা আল-হুসেইনি সিরিয়া গিয়েছিলেন অস্ত্র সহায়তার জন্য। কিন্তু তিনি সাহায্য পাননি। এদিকে সিরিয়া, হেজাজ, মিশর, জর্ডান, লেবানন, ইরাক ইত্যাদি আরব অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা আলাদা আলাদা রাষ্ট্রগঠন করে ব্রিটেনের অনুগত হয়েছে। জেরুজালেমে চলা দাঙ্গার মধ্যে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায় ব্রিটেন। একই দিন তৎকালীন ইহুদি নেতারা ঘোষণা করেন যে সেদিন রাতেই ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হবে।
ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের এক ঘন্টার মধ্যেই আরবরা আক্রমণ শুরু করে। একসাথে পাঁচটি আরব দেশ ইসরায়েলকে আক্রমণ করে। মিশর, ইরাক, লেবানন, জর্ডান এবং সিরিয়া। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো। অন্যদিকে ইসরায়েলের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ হাজার। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ইসরায়েলি বাহিনী পিছু হটতে থাকে। তাদের অস্ত্রের মজুত শেষ হয়ে যায়। সম্ভাব্য পরাজয় আঁচ করতে পেরে ইহুদিরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সময় নেয়। আর কিছুদূর অগ্রসর হলেই মিশরীয় বাহিনী তেল আবিবের দিকে অগ্রসর হতে পারতো। তখন আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে।
যুদ্ধবিরতির সময় দু'পক্ষই শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু ইসরায়েল বেশি সুবিধা পেয়েছিল। তখন চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে আধুনিক অস্ত্রের চালান আসে ইসরায়েলের হাতে। যুদ্ধবিরতি শেষ হলে নতুন করে আরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসরাঈলী বাহিনী। একর পর এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নেয় ইহুদীরা। তেল আবিব এবং জেরুজালেমের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। রাষ্ট্র গঠনের সময় জাতিসংঘ ইসরাঈলকে ফিলিস্তিনের ৫০% জমি দিলেও ইহুদীরা ক্রমাগত তাদের জমি বাড়াতে থাকে। যুদ্ধ হলে ভূমি বাড়ানোর প্রক্রিয়া কিছুদিন বন্ধ থাকে। আর পরিস্থিতি শান্ত হলে ভূমি অধিগ্রহণ বাড়াতে থাকে।
ইসরাঈল রাষ্ট্রগঠন করতে সক্ষম হলেও ফিলিস্তিনে কোনো রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। ফিলিস্তিনে কোনো নেতা ছিল না যার মাধ্যমে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গঠন করবে। ১৯৫৯ সালে ৩০ বছর বয়সী ইয়াসির আরাফাত জাতির মুক্তিকামী নেতা হিসেবে আবির্ভাব হন। এই তরুণের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা একত্রিত হয়।
ইয়াসির আরাফাত ছিল তার রাজনৈতিক নাম। তার মূল নাম মুহাম্মদ আবদেল রহমান আব্দেল রউফ আরাফাত আল-কুদওয়া আল-হুসেইনী। ডাক নাম আবু আম্মার। তার জন্ম ও বাড়ি হলো মিশরের কায়রোতে। জেরুজালেম ছিল তার নানার বাড়ি। কায়রোতে পড়াশোনা করার সময় তিনি আরব জাতীয়তাবাদী ধারণা লাভ করেন ও জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। পড়াশোনা শেষে জেরুজালেমে আসেন ও ফিলিস্তিনীদের একত্র করে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।
তার এই সংগঠন কায়েমের আগে তিনি ছাত্রদের নিয়েও কয়েকটি সংগঠন কায়েম করেছিলেন। PLO অল্প সময়ের মধ্যেই আরবদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার নেতৃত্বে মুসলিমরা ঘুরে দাঁড়ায়। মূলত PLO থাকার কারণে ফিলিস্তিন থেকে মুসলিমরা হারিয়ে যায় নি। তারা সংগ্রাম করার একটি অবলম্বন পেয়েছিলো। ইয়াসির আরাফাত হয়ে ওঠেন ফিলিস্তিনীদের প্রাণপ্রিয় নেতা।
১৯৬৭ সালে যুদ্ধে লজ্জাজনকভাবে হারের পর ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী দল ফাতাহর নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে PLO গেরিলা সশস্ত্র সংগঠনে পরিণত হয়। তারা ইসরাঈলীদের সীমানা বাড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জায়নবাদীরা নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করতে গেলে PLO তাদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতো। ১৯৮০ সাল থেকে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে পিএলও এর নেতৃত্বে ইন্তিফাদা শুরু করে। প্রতিষ্ঠা সময় থেকে পিএলও জর্ডানের সাহায্য পেয়ে আসছিল। পশ্চিমা বিশ্বের চাপে জর্ডান পিএলওকে বের করে দেয়। এরপর ইয়াসির আরাফাত লেবানন থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সেখান থেকেও তারা বহিষ্কৃত হন।
১৯৮০ সালের পর থেকে আরবের রাষ্ট্রসমূহ ইসরাঈলকে মেনে নেয় ও জায়নবাদীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে পিএলও-এর সংগ্রাম ব্যর্থ হতে থাকে। এর কারণ PLO-এর বহু নেতা ইসরাঈলী অর্থ, নারী ও সুযোগ সুবিধার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ইহুদী চক্রান্ত ও প্রলোভনে ইয়াসির আরাফাত ও তার দল বার বার পর্যদস্তু হলে ১৯৮৭ সালে হামাস গঠিত হয়। এরা মিশরের ইসলাম্পন্থী মুসলিম ব্রাদারহুড দ্বারা সংগঠিত হয়। হামাস দ্রুতই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইসলামপন্থী হামাসের উত্থান দেখে ইসরাঈল ফাতাহকে সমর্থন দেয়। তাদেরকে সরকার গঠন করার সুযোগ দেয়। প্রায় ৪১ বছর পর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে অস্ত্র সমর্পন করে PLO। বিনিময়ে তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পুনর্গঠনে ইসরাঈল আমেরিকা সহ সকল জায়নবাদীদের থেকে সুবিধা পায়। এভাবে একটি পঙ্গু রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের জন্ম হয়, যার কোনো সার্বভৌমত্ব ছিল না। এটি অসলো চুক্তি নামে পরিচিত।
এই ভাঁওতা চুক্তির জন্য পশ্চিমা বিশ্ব ইয়াসির আরাফাতকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেয়। কিন্তু এর ফলে ইয়াসিরের জনপ্রিয়তা বাড়েনি বরং কমেছে। কারণ রাষ্ট্র গঠনের পর ফিলিস্তিনে বিনা বাধায় ইহুদি বসতি স্থাপন করতে থাকে ইসরাঈল। আগে তো প্রতিরোধ করা যেত। অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনের মুসলিমদের একেবারে নিরাপত্তাহীন করে ফেলেছেন। দ্রুতই মুসলিমরা উচ্ছেদ হতে থাকে তাদের বাড়ি থেকে। ইয়াসির জায়নবাদীদের পাপেটে পরিণত হন।
অন্যদিকে হামাস তার সশস্ত্র প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। ফলে হামাস জনপ্রিয় হতে থাকে। ২০০০ সালে টিকতে না পেতে ফাতাহ (পিএলও-এর পরিবর্তিত নাম) ২য় ইন্তিফাদা শুরু করে। এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফাতাহ আবার অস্ত্র হাতে নেয়। ইয়াসির আরাফাতকে কোণঠাসা করে ফেলে পশিমা বিশ্ব। ইসরাঈল তাকে গৃহবন্দী করে। ২০০৪ সালে বিষ প্রয়োগে খুন করা হয় ইয়াসির আরাফাতকে। ধারণা করা হয় তার খ্রিস্টান স্ত্রী তাকে বিষ প্রয়োগ করেছে জায়নবাদীদের প্ররোচনায়। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনীদের ঐক্যের প্রতীক। তাকে খুন করতে পারলেই ফিলিস্তিনীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
২০০৬ সালের নির্বাচনে ফিলিস্তিনে নিরঙ্কুশ বিজয় পায় হামাস। কিন্তু সরকার গঠন করার পর মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে ফাতাহ হামাসের সাথে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। ফাতাহকে অস্ত্র ও অর্থের যোগান দেয় ইসরাঈল। অবশেষে ২০০৭ সালে হামাস মুসলিমদের রক্তক্ষয় এড়াতে গাজার একক নিয়ন্ত্রণ নেয় ও পশ্চিম তীর ফাতাহকে ছেড়ে দেয়। পশ্চিম তীরে সরাসরি না হলেও গোপনে হামাস সক্রিয় রয়েছে। আন্দোলন ও বিক্ষোভে পশ্চিম তীরের মানুষ হামাসের আনুগত্য করে। এভাবে কার্যত ফিলিস্তিন দুইভাগ হয়ে পড়ে। একইসাথে ফাতাহ, ইয়াসির আরাফাত ও মাহমুদ আব্বাসরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।
আমরা ফিলিস্তিনী যাদেরকে ইট পাথর নিক্ষেপ করতে দেখি তারা মূলত পশ্চিম তীরের জনগণ। তাদের কাছে অস্ত্র নেই। সেই অঞ্চলে প্রায়ই মুসলিমরা উচ্ছেদের শিকার হয়। অন্যদিকে গাজার লোকেরা অবরুদ্ধ হলেও গাজার অভ্যন্তরে ইসরাঈলীদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। তারা সেখানে ভূমি দখল বা বসতি স্থাপন করতে পারে না। হামাস ধীরে ধীরে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ২০১৪ সাল ও ২০২১ সালে তারা সরাসরি যুদ্ধ করে ইসরাঈলকে ভালো জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ইসরাঈলের সীমানা বাড়ানোর প্রচেষ্টা রুখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে হামাস যদি পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোর সহায়তা পায় তবে ইসরাঈলকে দমন করা সহজ হবে।