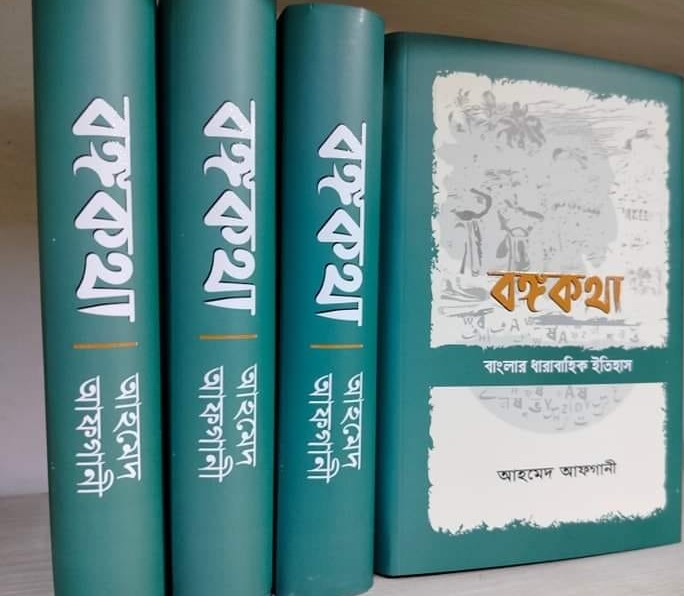বাংলাদেশ এবং উপমহাদেশে ছাত্র রাজনীতির উন্মেষ ঘটে ইংরেজ
শাসনের হাত ধরে। ইংরেজ শাসনের আগে দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা
থাকলেও ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন হয়নি। এর বেসিক কারণ উচ্চশিক্ষা তখন কোনো বৈষয়িক
লাভজনক কাজ ছিল না। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন ও মানবসেবাই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই
উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র খুব এভেইলেবল ছিল না। অর্থনীতি ছিল কৃষি ও ব্যবসাভিত্তিক।
আর এই দুই কাজের জন্যই উচ্চশিক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষেই
সাধারণত ছাত্ররা নিজ নিজ কর্মে আত্মনিয়োগ করতো।[১]
ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজরা উচ্চশিক্ষাকে লাভজনক ও অর্থ
উপার্জনের নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক মর্যাদা, সম্মান, সরকারি চাকুরি, ব্যবসায়িক সুবিধা, ইংল্যান্ডে আত্মপ্রতিষ্ঠার
হাতছানি,
জমিদারি, ভূমির অধিকারসহ প্রতিটি নাগরিক
সুবিধার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণকে শর্ত করে দেওয়া হয়। ফলে উচ্চশিক্ষা তার
লক্ষ্যচ্যুত হয়। এটি আর আগের মতো মানবসেবা বা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের মহান উদ্দেশ্য
সামনে রেখে হয়নি। শিক্ষকরা তাদের স্বার্থের জন্য শিক্ষাদান করতো। ছাত্ররাও তাদের
বৈষয়িক সুবিধা হাসিল করার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকে। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে
টানাপড়েন তৈরি হয়। এর মাধ্যমে ছাত্রদের অধিকার আদায়ের দরকার হয় এবং ছাত্র রাজনীতির
উন্মেষ ঘটে।
বাংলায় ১ম বিশ্ববিদ্যালয় মানের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন শেখ
শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা। তিনি ছিলেন হাদিস বিশেষজ্ঞ ও ইসলামি আইনবিদ। রসায়ন, ভৌতবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। স্বাধীন সুলতানি আমলে
বাংলায় আসেন তিনি। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসনকালে (১২৬৬-৮৭) তিনি দিল্লিতে
পৌঁছেন এবং সেখান থেকে বাংলায় আসেন। [২] এরপর সোনারগাঁতে তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা
করেন। এরকম আরেকটি বড় প্রতিষ্ঠান হলো তৎকালীন গৌড় ও বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জের
দারাসবাড়ি মাদরাসা।
ভারতে মুসলিম শাসনামলে সাড়ে পাঁচশত বছরে উপমহাদেশে লাখো
মাধ্যমিক মাদরাসা ও হাজার খানেক জামেয়া/ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৫৭ সালে
পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের ক্ষত আমাদের এখনো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ইংরেজরা সমস্ত মাধ্যমিক
মাদরাসা ও জামেয়া বন্ধের ঘোষণা দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত নিষ্কর
লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের অধিকারে নিয়ে নেয়। এতে মাদরাসাগুলোর আয় বন্ধ হয়ে যায়।
মাদরাসায় জমি সরকার দখল করে প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেয়। এরপরও কিছু প্রসিদ্ধ শিক্ষক
ব্যক্তিগতভাবে নিজ বাড়িতে শিক্ষা চালু রাখার চেষ্টা করেন। সেসব শিক্ষকদের
নির্মমভাবে খুন করে ইংরেজরা। [৩]
১০ বছরের মধ্যে তারা বাংলাসহ উপমহাদেশের সমস্ত শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে এক মূর্খ সমাজে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। তাদের টার্গেট
ছিল উপমহাদেশের মানুষ কেবল কৃষিকাজ করবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে তাদের কোনো
ভূমিকা থাকবে না। ১৮০০ সাল থেকে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির নামে নতুন ষড়যন্ত্র
শুরু করে। নতুনভাবে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পাঠ্য কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে। এতে
তাদের টার্গেট ছিল ভারতীয়রা যাতে ইংরেজদের প্রতি অনুগত থাকে সেরকম শিক্ষানীতি
প্রণয়ন করা। এজন্য তারা মুসলিম শাসনামলকে অন্ধকারচ্ছন্ন মধ্যযুগ বলে অভিহিত করে।
তাদের পুরাতন সভ্যতাগুলো মহান ও মানবিক সভ্যতা হিসেবে উপস্থাপন করে। ইংরেজরা এদেশ
থেকে মুসলিম শাসকদের হটিয়ে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছে এমন কথা
দ্বারা পাঠ্যক্রম সাজায়। যাতে ভারতীয়রা ইংরেজদের মহান ভাবে। ইংরেজদের অনুসরণ করে
তাদের অনুগত থাকাকে গর্বের বিষয় হিসাবে ভেবে নেয়।
১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মেকলে তাঁর বিখ্যাত পাশ্চাত্য
শিক্ষানীতির প্রস্তাব বড়লাটের কাছে পেশ করেন। এই প্রস্তাবের প্রধান দিকগুলি হল – [৪]
(১) তিনি প্রাচ্যের সভ্যতাকে ‘দুর্নীতি, অপবিত্র ও নির্বুদ্ধিতা’ বলে অভিহিত করে সরাসরি পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ
করেন।
(২) তাঁর মতে প্রাচ্যের শিক্ষায় কোনও 'বৈজ্ঞানিক চেতনা' নেই এবং তা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা অপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে
নিকৃষ্ট (Oriental
learning was completely inferior to European learning”)।
(৩) তাঁর মতে, “ভালো ইউরোপীয়
গ্রন্থাগারের একটি তাক আরব ও ভারতের সমগ্র সাহিত্যের সমকক্ষ। বলা বাহুল্য, মেকলের এই মত ছিল সম্পূর্ণভাবে অহমিকা-প্রসূত ও অজ্ঞানতাপূর্ণ।
(৪) তিনি বলেন যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ইংরেজি
শিক্ষা বিস্তৃত হলে তা ‘ক্রমনিম্ন
পরিস্রুত নীতি’ (Downward Filtration Theory) অনুযায়ী ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।
(৫) মেকলের লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক বিজয়। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এমন এক ভারতীয় গোষ্ঠী তৈরি হবে যারা “রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু
রুচি,
মত, নৈতিকতা এবং বুদ্ধিমত্তায় হবে
ইংরেজ।”
মেকলের এই প্রস্তাবনা অনুসারেই পাশ্চাত্য শিক্ষাক্রম চালু
করে করে ইংরেজরা। একই সাথে ইংরেজরা পাঠ্যক্রমে 'বৈজ্ঞানিক
চেতনা'র নামে সেক্যুলার শিক্ষা চালু করে। যাতে মানুষ জীবন যাত্রায় ধর্মের কোনো
সংযুক্ততা না পায়। ধর্মকে শুধুমাত্র আচার ও রীতিনীতি সর্বস্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।
মুসলিম ও হিন্দুরা যাতে ভেবে নেয় ধর্মই তাদের পিছিয়ে যাওয়া ও পরাজিত হওয়ার মূল
কারণ। যত দ্রুত ধর্মকে ছেড়ে দেবে ততই উন্নতি হবে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় ভারতীয়দের।
ইংরেজদের এই পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে উপমহাদেশে। নির্যাতন, দুর্নীতি ও শোষণ করে দুর্ভিক্ষে ঠেলে দিলেও ইংরেজদের সভ্য ও মহান ভাবতে থাকে
এই অঞ্চলের মানুষরা।
এই ধরণের বস্তুবাদী শিক্ষা চালু করার ফলে এবং ধর্মীয়
শিক্ষার অনুপস্থিতিতে শিক্ষা একটি বস্তুবাদী ও স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।
ছাত্র ও শিক্ষকরা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়। আগে যেভাবে শিক্ষকরাই
ছাত্রদের অভিভাবক ও তাদের সমস্যার সমাধান করতেন। এখন আর সেই ব্যবস্থা থাকে না।
শিক্ষকরা তাদের জীবিকার অংশ হিসেবেই শিক্ষা দান করতেন। জাতি গঠনের মানসিকতা থেকে
তাঁরা সরে আসেন। ছাত্ররা তাদের নিজেদের অধিকার আদায় করতে গিয়েই উপমহাদেশে ছাত্র
রাজনীতির উন্মেষ ঘটে।
সর্বপ্রথম ১৮১৮ সালে হুগলির শ্রীরামপুরে ডেনমার্কের
খ্রিস্টান মিশনারীদের সহায়তায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে 'শ্রীরামপুর কলেজ' প্রতিষ্ঠা হয়।[৫] এরপর ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজসহ অনেক
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ইংরেজরা। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সরকার থেকে
সরাসরি ভাতা পেতেন। তাই সুলতানী আমলের মতো ছাত্রদের প্রতি কেয়ারিং ছিলেন না। নতুন
শহরে নানাবিধ সুবিধা পাওয়ার জন্য একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক
সমিতি করে রাজনীতি শুরু করেন। যেমন নোয়াখালী-কুমিল্লা, হুগলি, বারাসাত,
আসাম, বরিশাল, ঢাকা
ইত্যাদি
১৯২৯ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সংগঠন ‘জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া’ মাদ্রাসা ছাত্রদের অধিকার আদায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রথম
ছাত্র রাজনৈতিক দল যারা বিভিন্ন মাদরাসায় সক্রিয় ছিল। তবে এই ছাত্র রাজনীতি জাতীয়
রাজনীতিতে কোনো প্রভাব রাখতো না। নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধান ও ছাত্র
প্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্যেই এই ছাত্ররাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল।[৬]
১৮৮৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ১ম রাজনৈতিক দল ইন্ডিয়ান
ন্যশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। এটি উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন।
১৮৮৫ সালে থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কিছু সদস্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা হলেন
অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, দাদাভাই নওরোজি, দিনশ এদুলজি ওয়াচা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন প্রমুখ। ভারতের স্বাধীনতা
আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দান করেছিল। এই রাজনৈতিক দল গঠিত হয় যাতে ভারতীয়
এলিট সোসাইটি সরকার থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকার পেতে পারে। এর সাথে অল্প কিছু
মুসলিমরাও যুক্ত ছিল। [৭]
কিন্তু যতই দিন গড়াতে থাকে ততই দেখা যায় কংগ্রেস মূলত
ভারতীয় হিন্দুদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট। মুসলিমদের ব্যাপারে শুধু অনুৎসাহী নয়, মুসলিমদের সাথে বৈরি আচরণ শুরু করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস
মুসলিমদের শত্রু বিবেচনা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কংগ্রেসের বৈরি
আচরণের প্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আহবানে
উপমহাদেশের সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকায় একত্রিত হন। ঢাকায় উপমহাদেশের সকল মুসলিম
নেতাদের সমাবেশ থেকে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ
গঠিত হয়। মুসলিমরা কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকেন।[৮]
উপমহাদেশের মানুষরা দুইটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন।
মুসলিমরা মুসলিম লীগে ও হিন্দুরা কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে রাজনীতি এগিয়ে নেন। ইতোমধ্যে
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু
করে। ১৯৩২ সালে ছাত্রদের জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত করে মুসলিম লীগ। কায়েদে আযম
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নির্দেশে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে
মুসলিম লীগের অধীনে ছাত্রদের একটি সংগঠন 'অল
বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ' গঠন করেন। বাংলায় নাম ছিল নিখিল
বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ। সভাপতি হন ঢাকার আব্দুল ওয়াসেক, সাধারন
সম্পাদক হন যশোরের শামসুর রহমান।
এটি ছিল জাতীয় রাজনীতিভিত্তিক উপমহাদেশের ১ম রাজনৈতিক ছাত্র
সংগঠক। জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ মুসলিমলীগের রাজনীতিকে সহজ করে দেয়।
সাধারণত ছাত্ররা কর্মতৎপর ও অনুগত হয়। মুসলিম লীগ সেই সুবিধাটি গ্রহণ করেছে। অল্প
সময়ের মধ্যে মুসলিম লীগ সমগ্র মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছাত্রদের
অংশগ্রহণের ফলে ও তাদের নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করায় মুসলিম ছাত্ররা দ্রুতই জাতীয়
রাজনীতিতে অংশ নিতে থাকে। 'অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস
লীগের'
মাধ্যমে মুসলিম লীগের সফলতা দেখে ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসপন্থী
হিন্দু ছাত্রদের নিয়ে স্টুডেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া গঠিত হয়।[১০] এভাবেই ১৯৩২ সাল
থেকে মুসলিম লীগের হাত ধরে লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির উত্থান হয় উপমহাদেশে।
তথ্যসূত্র :
১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ
ইসলামিক সেন্টার / পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৪
২. শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা / বাংলাপিডিয়া / মুয়াযযম হুসাইন খান / এশিয়াটিক সোসাইটি
৩. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান /
কামিয়াব প্রকাশন / পৃষ্ঠা ৫৯-৬৩
৪. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ
ইসলামিক সেন্টার / পৃষ্ঠা ১৬০-১৭২
৫. শ্রীরামপুর কলেজ / বাংলাপিডিয়া / প্রফুল্ল চক্রবর্তী / এশিয়াটিক সোসাইটি
৬. জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার ৯৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কাল /
দৈনিক ইনকিলাব / ২৩ নভেম্বর ২০২১
৭. The Nature and Dynamics of Factional Conflict/ P. N.
Rastogi/ Macmillan Company/ p-69
৮. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান /
কামিয়াব প্রকাশন / পৃষ্ঠা ১৪২
৯. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস( ১৮৩০-১৯৭১)/ ড.
মোহাম্মদ হাননান/ আগামী প্রকাশন/ পৃষ্ঠা ৪১
১০. SFI: A Movement of Study, Struggle and Sacrifice For
a Scientific, Secular Education/ Vikram Singh