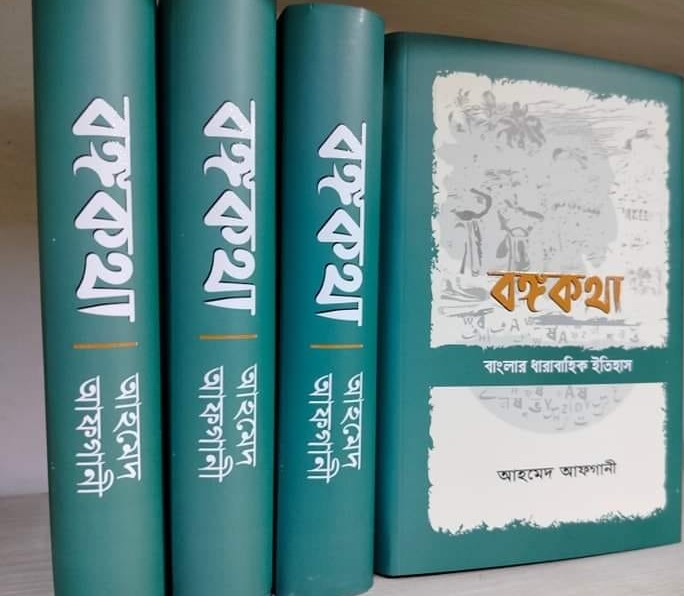বায়তুল মুকাররম মসজিদ। কে না চিনে? বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মসজিদ। আমি নোয়াখালীর মফস্বলে বেড়ে উঠা মানুষ। বায়তুল মুকাররমে নামাজ পড়া ছিল স্বপ্নের মতো। একবার একটি রাজনৈতিক প্রোগ্রামে অনেকের সাথে এলাম পল্টনে। স্কুলছাত্র ছিলাম বলে নিয়ে আসতে চাইছিলো না কেউ। কিন্তু জোর করে চলে এলাম।
পল্টন ময়দানে এসে জানতে পারলাম পাশেই বায়তুল মুকাররম। অনেক ভাইকে বললাম ভাই আমাকে একটু নিয়ে চলেন। মসজিদটা একটু দেখবো। কিন্তু কেউ রাজি হলো না দলছুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। প্রচণ্ড গরম। আইসক্রিম আর তরমুজ বিক্রি হচ্ছে স্থানে স্থানে।
আইসক্রিম খেতে এসে দেখি আমার স্কুলের এক স্যার। সালাম দিলাম। তিনি বললেন ছোট মানুষ তুমি। কেন এলে? আমি কিছু না বলে চুপ করে ছিলাম। তিনি আমাকে আইসক্রিম কিনে দিলেন। বললেন আর কিছু লাগবে কিনা?
আমি বললাম, স্যার বায়তুল মুকাররমে যোহর নামাজ পড়তে চাই। তিনি বললেন বেশ! আমিও তো চিন্তা করে রাখছি যোহর বায়তুল মুকাররমে পড়বো। এরপর স্যারের পিছে লেগে থাকলাম। যাতে এত মানুষের মধ্যে স্যারকে হারিয়ে না ফেলি।
সেই আমার প্রথম বায়তুল মুকাররম দেখা ও নামাজ পড়া। অন্যরকম অনুভূতি কাজ করেছিল। আহা আমি বাংলাদেশের সেরা মসজিদে নামাজ পড়ছি। যে মসজিদকে এতদিন পত্রিকায় ও টিভিতে দেখেছি সেটাতে এখন আমি নিজেই। আহা...। চোখ বন্ধ করে এখনো টের পাই ছেলেবেলার সেই অনুভূতি।
এরকম দুইটা অনুভূতির জন্য অপেক্ষা করছি। এক. সৌদিতে গিয়ে কা'বায় ও নববীতে দাঁড়িয়ে আবেগে আপ্লুত হবো আর চোখের পানি ফেলবো। দুই. জেরুজালেমে গিয়ে অনেক নবীর স্মৃতি বিজড়িত বায়তুল আকসায় সিজদা দিয়ে পড়ে রইবো। জানিনা কবে আল্লাহ তায়ালা আমার ইচ্ছেগুলো কবুল করবেন!
যাই হোক ফিরে আসি বায়তুল মুকাররমে। এটি পল্টনে অবস্থিত। মসজিদটির আয়তন ৬০ হাজার বর্গফুট। এর ধারণ ক্ষমতা ৪০,০০০। মানে একসাথে ৪০ হাজার মানুষ এখানে নামাজ পড়তে পারে। এই সুবিশাল মসজিদ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং ধারণক্ষমতা বিবেচনায় এটি পৃথিবীতে দশম বৃহত্তম মসজিদ।
পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যে ক'জন ব্যক্তি/পরিবার নিজ উদ্যোগে পাকিস্তান গঠনে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে বাওয়ানী, আদমজী, ইস্পাহানী অন্যতম। বাওয়ানী পরিবারের লতিফ বাওয়ানী বাংলাদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৫ টি শিল্পকারখানা স্থাপন করে। বাংলাদেশের পাটকে সোনালী আঁশে পরিণত করে মূলত বাওয়ানী, আদমজী ও ইস্পাহানী পরিবার।
লতিফ বাওয়ানী পূর্ব-পাকিস্তানে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সে জন্য ঢাকার আলেম সমাজ ও গণ্যমান্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন ১৯৫৯ সালে। সেখানে ঠিক হয় এই মসজিদের নাম হবে বায়তুল মুকাররম। কমিটির নাম হয় বায়তুল মুকাররম মসজিদ সোসাইটি। কিন্তু তখনো ঠিক হয়নি মসজিদটি কোথায় স্থাপিত হবে?
বেশিরভাগ লোক বলেছিলো পুরান ঢাকায় করার জন্য। কিছু লোক বললো নতুন ঢাকায় করা ভালো হবে কারণ সেটা হবে পরিকল্পিত ঢাকা। যেহেতু এটা গ্র্যান্ড মসজিদ হবে তাই পুরান ঢাকায় সম্ভব নয় কারণ সেখানে এত জায়গা নেই। তাহলে? পরে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় এটি পুরান ঢাকা ও নতুন ঢাকার সংযোগস্থলেই স্থাপিত হবে। আর সেটা হবে পল্টনে।
ঢাকায় যখন এমন আলোচনা চলছিলো তখন পাকিস্তানের শাসক ছিলেন সেনাশাসক স্বৈরাচারী আইয়ুব খান। স্বৈরাচারীদের একটা ব্যাপার থাকে এমনসব আকর্ষণীয় কিছু করা যাতে তারা মানুষদের কাছে ভালো ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান পায়। যেমন বাংলাদেশে এরশাদ নিজেকে ইসলামিক প্রমাণ করার জন্য অনেক কিছু করেছে। আবার এখন হাসিনা নিজেকে তাহাজ্জুদ্গুজার হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
আসলে এরা সবাই আইযুবের শিষ্য। যাই হোক আইয়ুব খানও এমন একটি মসজিদের কথা ভাবছেন যা পাকিস্তানের ঐতিহ্যকে শাণিত করবে। এটা হবে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এমন সময় লতিফ বাওয়ানীর প্রস্তাব আইয়ুব খানের কাছে পৌঁছলে তা আইয়ুবের জন্য সহজ হয়ে গেলো। একইসাথে আইয়ুব খান ঢাকাকে সেকেন্ড রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো। তাই পাকিস্তানের পার্লামেন্টের জন্য শেরে বাংলা নগরে কাজ শুরু করলো।
জাতীয় সংসদ ভবন ও বায়তুল মুকাররম মসজিদ দুটি মেগা প্রজেক্ট আইয়ুব একইসাথে শুরু করে। লতিফ বাওয়ানী মসজিদের খরচের বড় অংশ বহন করে। সরকার প্রায় সাড়ে আট একর জমি বরাদ্দ দেয় মসজিদের জন্য। মসজিদটি এখন যে স্থানে সেখানে একটি বিশাল পুকুর ছিল, নাম পল্টন পুকুর। সেই পল্টন পুকুর ভরাট করেই মসজিদ স্থাপিত হয়।
বিশিষ্ট স্থপতি আবদুল হুসেন মুহাম্মদ থারিয়ানিকে মসজিদ কমপ্লেক্সটির নকশার জন্য নিযুক্ত করেন লতিফ বাওয়ানী। থারিয়ানীর বাড়ি ছিল মুম্বাইতে। পরে অবশ্য পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। পুরো কমপ্লেক্স নকশার মধ্যে দোকান, অফিস, লাইব্রেরি ও গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারি এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এই মসজিদে একসঙ্গে ৪০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদের প্রধান কক্ষটি তিন দিকে বারান্দা দিয়ে ঘেরা। মিহরাবটি অর্ধ-বৃত্তাকারের পরিবর্তে আয়তাকার।
বাইরে থেকে দেখলে বায়তুল মোকাররম মসজিদকে ‘কাবার’ মডেলের মতো মনে হবে। বায়তুল মোকাররম মসজিদটি প্রধানত ৮তলা। নীচতলায় বিপণী বিতান ও গুদামঘর। বাকীগুলো নামাজের জন্য। আল্লাহর ৯৯টি নামের কথা স্মরণ করে মসজিদটির উচ্চতা ৯৯ ফুট করা হয়েছে।
১৯৬৩ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম পর্বের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ১৯৬৩ সালের ২৫ জানুয়ারি শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রথম জুমআর নামাজ আদায় করা হয়। আর এর পরদিন ২৬ জানুয়ারি শনিবার তারাবীহ নামাজ শুরু হয়।
১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন মুজিব সরকার সমাজতন্ত্রীদের পরামর্শে লতিফ বাওয়ানীর সমস্ত শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয়। বাওয়ানী পরিবার প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় পাকিস্তানে ফিরে যায়। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানেও তাদের ব্যবসা ছিলো। পাকিস্তান গঠনের পর এই বাওয়ানী, আদমজী ও ইস্ফাহানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করার কাজ করেছিলো। এখনকার ব্যবসায়ী মতো শুধু ব্যবসা করেনি তারা। এই বাওয়ানীরা শত শত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, পাঠাগার স্থাপন করেছে। বাংলা শিল্প সাহিত্যের বিকাশে বহু সম্মাননা ও পুরষ্কারের আয়োজন করেছে।
এদেশের কাঁচামাল থেকে যাতে এদেশের মানুষ উপকৃত হয় সেই ব্যবস্থা করেছে। হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এই লতিফ বাওয়ানী। যিনি আমাদের বায়তুল মুকাররমের মতো মসজিদ উপহার দিয়েছেন আমরা তাকে গলাধাক্কা দিয়েছি শুধুমাত্র অবাঙালি হওয়ার অপরাধে। এমন নয় যে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনও নয় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি ভারতের গুজরাট থেকে আসা মুহাজির মুসলিম।
যাই হোক, এবার আসি খতিবদের প্রসঙ্গে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম খতিব ছিলেন মাওলানা আবদুর রহামন বেখুদ (রহ:)। তিনি ১৯৬৩ সালে এই মসজিদের খতিব হন। এরপরে খতিব হন মাওলানা ক্বারী উসমান মাদানী (রহ:)। তিনি এ মসজিদের খতিব ছিলেন (১৯৬৩-১৯৬৪) মাত্র এক বছর। পরবর্তী খতিব ছিলেন মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান। তিনি ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ মসজিদের খতিব হন মুফতী মাওলানা মুইজ (রহ:)।
এদেশের কাঁচামাল থেকে যাতে এদেশের মানুষ উপকৃত হয় সেই ব্যবস্থা করেছে। হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এই লতিফ বাওয়ানী। যিনি আমাদের বায়তুল মুকাররমের মতো মসজিদ উপহার দিয়েছেন আমরা তাকে গলাধাক্কা দিয়েছি শুধুমাত্র অবাঙালি হওয়ার অপরাধে। এমন নয় যে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনও নয় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি ভারতের গুজরাট থেকে আসা মুহাজির মুসলিম।
যাই হোক, এবার আসি খতিবদের প্রসঙ্গে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম খতিব ছিলেন মাওলানা আবদুর রহামন বেখুদ (রহ:)। তিনি ১৯৬৩ সালে এই মসজিদের খতিব হন। এরপরে খতিব হন মাওলানা ক্বারী উসমান মাদানী (রহ:)। তিনি এ মসজিদের খতিব ছিলেন (১৯৬৩-১৯৬৪) মাত্র এক বছর। পরবর্তী খতিব ছিলেন মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান। তিনি ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ মসজিদের খতিব হন মুফতী মাওলানা মুইজ (রহ:)।
তিনি দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭৪-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। এরপরে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দায়িত্ব পালন করেন খতিব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ:)। তিনি ছিলেন দেশ বরেণ্য আলেম। তিনি খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত।
তারপর ২৪ বছর যিনি এখানে ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেই মুফতি মাও: নুরুদ্দীন সাহেব এক বছর ভারপ্রাপ্ত খতিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের দায়িত্বে রয়েছেন প্রফেসর মাওলানা মো: সালাহ্উদ্দিন। তিনি ৫ জানুয়ারি ২০০৯ সালে এ মসজিদের খতিব নিযুক্ত হন।