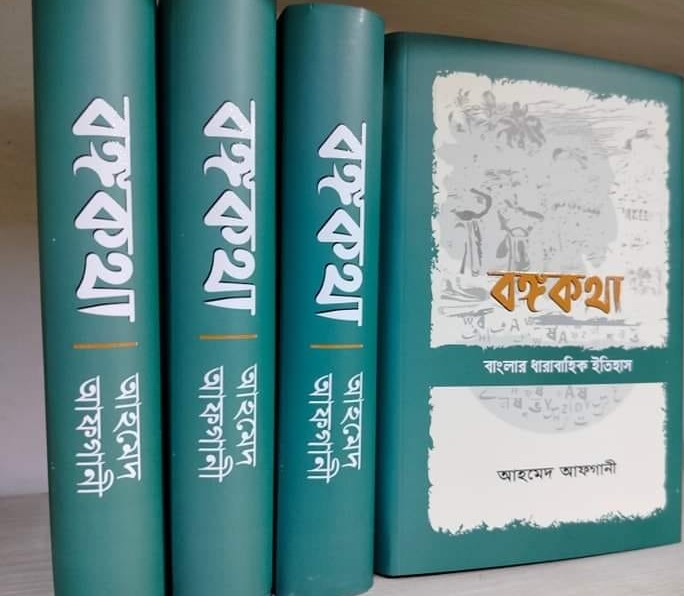বঙ্গভঙ্গের ব্যাপক ঘটনা প্রবাহে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহ্দিু সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের যে দ্বন্দ্ব, তার পটভূমিতে গঠিত হয় মুসলিম লীগ, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দুদের সাথে যে মানসিক বিচ্ছেদ তা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, “যদিও তারা একই দেশের মানুষ ছিল, তবুও এক ভাষা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তারা বিভিন্ন ছিল। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আটশ’ বছর ধরে তারা বাস করেছে যেন দু’টি ভিন্ন পৃথিবীতে”।
মুসলিম শাসনের শুরু থেকে কয়েক শতাব্দী বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ, অভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচরণ পদ্ধতি নিয়ে ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনে আপাতদৃষ্টিতে বড় রকমের কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনকে হিন্দুরা নিছক শাসক-বদলের ঘটনারূপে গ্রহণ করে। ইংরেজদের আস্থা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। রাতারাতি তাদের একটি শ্রেণী বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। তারা এই শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে ‘রানীর বিদ্রোহী প্রজা’ রূপে অভিহিত হয়। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। হিন্দুরা ইংরেজদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। মুসলমানদের সংগ্রামে হিন্দুদের কোন সহানুভূতি ছিল না।
বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষপটে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রয়াদিক স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়। মুসলমানদের শক্ররূপে চিহ্নিত করে তাদের ওপর তারা নানামুখী হামলা পরিচালনা করে। কুড়ি শতকের শুরুতে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে হিন্দুদের মারমুখী সংগ্রাম হিন্দু-মুসলিত জাতি-স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে আরো প্রকটভাবে উপস্থিত করে।
সৈয়দ আমীর আলী সর্বপ্রথম তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় মুসলমানদেরকে একটি ‘স্বতন্ত্র জাতি’ (Nationality, Nation) নামে অভিহিত করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। এর আগে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে ‘কওম’ নামে অভিহিত করলেও আমীর আলীর দাবি ছিল অধিকতর রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত। ১৮৮৩ সালে আমীর আলী ‘মিউনিসিপ্যালিটি বিলে’ সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। এ সময় থেকেই মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন কায়েমের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল। ১৯০১ সালের অক্টোবরে নওয়াব ওয়াকার উল মূলক লাখনৌতে মুসলমানদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯০৩ সালে সাহারানপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৬ সালের ফ্রেরুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে ফযল-ই-হুসাইন ‘মুসলীম লীগ’ নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।
এ সময় ভারত সচিব লর্ড মর্লি পার্লামেন্টে আভাস দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করছেন। এই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দাবি নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলায় বড় লাট মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সিমলা ডেপুটেশনে যোগ দেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও আবুল কাসেম ফজুলল হক। তাঁরা নওয়াব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেসী গঠনের খসড়া পরিকল্পনা সাথে নিয়ে যান। একই বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে বেরিয়ে এসে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের উদাত্ত আহবান জানান।
মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সলীমুল্লাহর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ সিমলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তাঁরা ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা সম্মেলনে কনফেডারেসী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবল আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের এক বিশেষ সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আটশ’ প্রতিনিধির এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবেই ভারতীয় মুসলমানগণ একটি নতুন রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করেন। এ রাজনৈতির ভিত্তি হলো জাতিস্বাতন্ত্রভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ।
সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যাবলি ছিল মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য রেখে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করা, ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলা। একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহর পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য হিন্দুদের শক্তিশালী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এটাই ছিল মূল এবং প্রধান কারণ।
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ একটি দুর্বল সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগকে বাতিল করে দেয়। এসব সংবাদপত্র দ্রুত মুসলিম লীগের বিলুপ্তি ঘটবে বলে প্রচার চালায়। এটা সত্য যে প্রথম দিকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে লীগের গতিশীলতার অভাব ছিল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসা এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তরুণ প্রজন্মের মুসলমানগণ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তারা ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের বিরোধিতা তো করেনই, অধিকন্তু ভারতে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠারও দাবি করতে থাকেন।
১৯১০-এর দশকে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদলে একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি ঘটলে মুসলিম লীগ জড় ও স্থবির অবস্থায় পড়ে। ১৯২০-এর পর থেকে কয়েক বছর খেলাফত সংগঠনই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সকল কাজ পরিচালনা করে।
১৯৩৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেতৃত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সংগঠনটি রাজনৈতিকভাবে খুব বেশি সফলতা পায়নি। অনেক মুসলমান নেতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডন হতে ভারতে ফিরে আসেন এবং মুসলিম লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখাসমূহ পুনর্গঠিত করে নতুন কাঠামো প্রদান করেন। নতুন কমিটিসমূহকে জনসংযোগ এবং আসন্ন নির্বাচনী রাজনীতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। মোট নয়টি প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে লীগ ১০৪টি আসন লাভ করে। মোট প্রাপ্ত আসনের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক (৩৬টি) শুধু বাংলাতেই অর্জিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ আইন সভায় কংগ্রেসের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ধারণা করা হয় যে, বাংলায় মুসলিম লীগের বিজয় ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান পেশাদার ও মুসলমান ভূমি মালিক সম্প্রদায়ের যৌথ সমর্থনের ফল। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো তা হলো আলেম শ্রেণি বিশেষত দেওবন্দি ধারার আলেমরা মুসলিম লীগের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকাতেই আগ্রহী ছিল।
১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর ফলে তার মন্ত্রিসভা কার্যত মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে বাংলাকে মুসলিম লীগের দুর্গে পরিণত করা হয়। বাংলার মুসলমানদের নেতা হিসেবে ফজলুল হক মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভুমি দাবি করে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
গর্ভনর জন হার্বাট-এর পরামর্শে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে খাজা নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে মুসলিম লীগ একটি যথার্থ জাতীয় সংগঠনে পরিণত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের মধ্যে দল ১১০টি আসন অর্জন করে। ফলে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুসলিম লীগই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একক সংগঠন। তখন পর্যন্ত কংগ্রেস প্রভাবাধীন একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য মুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহে লীগের সাফল্য সমভাবে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের নায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক সকল আলোচনা ও চুক্তিতে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জিন্নাহর মতামত গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবের ছয় বছর পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইন সভায় মুসলমান সদস্যদের দিল্লি কনভেনশনে ‘একটি মুসলমান’ রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জিত হলে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলের সংগঠনে পরিণত হয়।