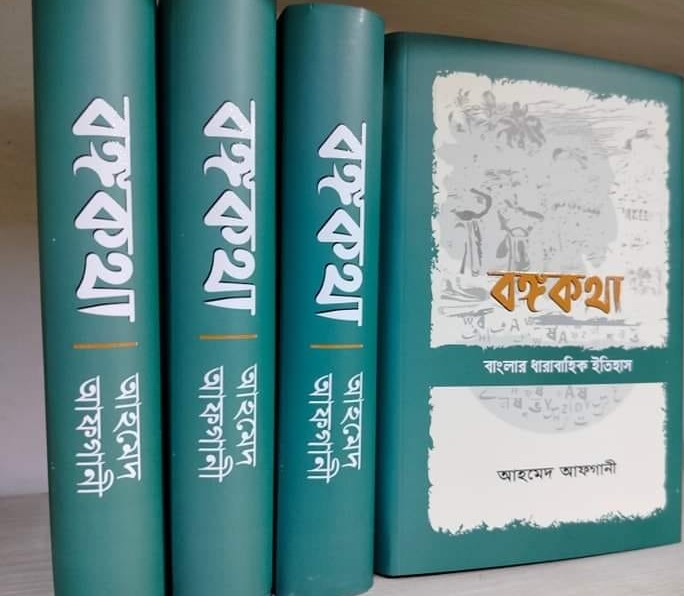শিরোনামে স্বদেশী আন্দোলনের পাশে সন্ত্রাসবাদী শব্দটা লিখার কারণ ইচ্ছেকৃত। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্বদেশী আন্দোলনকে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখানো হয়। সেভাবেই ইতিহাস লিখিত হয়েছে। অথচ এই আন্দোলন ছিলো মুসলিমবিরোধী। ইংরেজরা কেন মুসলিদের উপকার করলো এই ক্ষোভ থেকে এই আন্দোলন চলে।
যাই হোক বাংলার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের ফলে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এটাকে হিন্দুরা প্রথমত ‘জাতীয় ঐক্যের’ প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করে। অতঃপর নানাভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে, যথা তাদের ‘রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার শাস্তি’, ‘মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব’, এবং অবশেষে এটাকে ‘মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা’ নামে অভিহিত করে। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিলেন। ‘জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো’, ‘পবিত্র বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করা হলো’, ‘ব্রিটিশ সরকার এবং দেশদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে এক অশুভ আঁতাত’ প্রভৃতি উত্তেজনাকর উক্তির দ্বারা বাংলার পরিস্থিতি ভয়ংকর করে ফেললো বাংলার হিন্দু সমাজ।
হিন্দু আইনজীবীগণ এর আইনগত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, বাংলা ভাষার সাহিত্যিকগণ প্রচার শুরু করলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হলো। ব্যবসায়িরা জানালের তাদের কীরূপ ক্ষতি হলো। এ ধরনের অসংগত ও অবাস্তব প্রচারণার কারণ কি ছিলো? মুসলমানদের উপরে হঠাৎ এ আক্রমণ ও অশোভন উক্তি শুরু হলো কেন? আব্বাস আলী খান বলেন, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে বংগভংগে কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন ও বেসামাল হয়ে পড়েছিল। যে সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংগালী হিন্দুগণ উভয় বাংলার চাকুরী বাকুরী ও জীবন জীবিকার উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল, তা বংগভংগের ফলে বিনষ্ট হয়ে গেল। নতুন বাংলায় মুসলমানরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বশ্যতা ও পরাভব থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং তাঁদের মনে এ আশার সঞ্চার হলো যে, এখন স্থানীয় সমস্যাদির উপর তাঁদের কথা বলার অধিকার থাকবে। সমসাময়িক লেখম সরদার আলী খান বলেন, “যত সব হৈ হল্লা এবং হঠাৎ রাতারাতি যে দেশপ্রেমের আন্দোলন শুরু হলো মাতৃভূমি অথবা ভারতের কল্যাণের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যে প্রদেশে হিন্দুগণ সুস্পষ্ট সংখ্যালঘু সেখানে তাদের শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা ব্যতীত অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য এ আন্দোলনের নেই।
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অন্যতন নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেন, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায়। যে ১৬ই অক্টোবর নতুন বাংলার (পূর্ব বাংলা ও আসাম) সূচনা হয়, সেদিন কোলকাতায় হিন্দুগণ জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। ঐ দিন তারা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, মাথার ভস্ম মাখেন, পানাহার পরিত্যাগ করে নানারূপ বিক্ষোভ ধ্বনি সহকারে মিছিল করে গঙ্গাস্নান করেন। অপরাহ্নে এক জনসভায় মিলিত হয়ে তাঁরা বঙ্গভঙ্গ রদের শপথ গ্রহণ করেন।
মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর ‘আমাদের মুক্তি সংগ্রাম’ গ্রন্থে বলেন, “যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই লেফটন্যান্ট গভর্নরের শাসনধীন ছিল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় ব্রিটিশ সরকার অনেকদিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গ বিভাগের অনুকূলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। দূর মফঃস্বলেও বংগভংগের বিরোধিতা করিয়া সভাসমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে”।
কিছু মুসলমান হিন্দুদের প্রচার ও তথাকথিত দেশপ্রেম আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, বালগংগাধর তিলক প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ শিবাজীকে আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে উপস্থিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুজাতির সুপ্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগ্রত করতে লাগলেন, তখন তাঁরা বঙ্গভঙ্গের সুদূরপ্রসারী মঙ্গল ও তার বিরোধিতার মূল রহস্য উপলব্ধি করে আন্দোলন পরিত্যাগ করেন। এ প্রসংগে আবদুল মওদূদ তাঁর “মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর” গ্রন্থে বলেন –“কিন্তু এই বংগভংগ বিভাগকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যে তুমুল আন্দোলন করে, তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি ও বেতনভুক্ত সাংবাদিকরা। নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র ও ডিসপ্যাচসমূহে যেসব পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হতে লাগলো ‘দি টাইমস’ ও ‘মানচেষ্টার গার্জেনে’ তাতে ব্রিটিশ জনমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়ে। টাইমস পত্রিকায় বংগভংগকে সমর্থন করে ও কার্জনের কার্যাবলীকে পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে সুন্দর সুন্দর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মানচেষ্টার গার্জেনে বঙ্গভঙ্গকে নিন্দা করে গরম গরম প্রবন্ধ বের হ’তে থাকে, নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে আন্দোলন সম্পর্কে ও বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে। কটন, নেভিন্সন ও হার্ডি বিক্ষোভকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রচার করতে থাকে।
কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের বিক্ষোভকে নতুন মাত্রা দিতে ‘স্বদেশী’ নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। সে আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে বিলাতী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই বাগেরহাটে এক জনসভায় বিলাতি পণ্য বর্জন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যতদিন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হবে, ততদিন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা হোক। পরবর্তী ছয় মাস সব ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। কলকাতার রিপন কলেজে দু’দিনব্যাপী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলাতি পণ্য পোড়ানের আহ্বান জানানো হয় এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।
স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘স্বদেশ বান্ধব সমিতি’ ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সংঘটিত করে। মহারাজা গিরিজা নাথের সভাপতিত্বে দিনাজপুরে এক সভায় বছরব্যাপী জাতীয় শোক পালন এবং জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সকল সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাতে যুদ্ধ-মন্ত্রের মতো ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া হয় এবং বিভক্ত ‘বাংলা-মা’- এর পুনঃসংযোজন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।
১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে মনীন্দ্রনাথ নন্দীর সভাপতিত্বে বাংলার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ৪৬ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, “বঙ্গ বিচ্ছেদ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার হবে না”। বিলাতি পণ্য বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কর্মচারীদের অফিস বর্জন, সরকারের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূটি নেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাবু অন্নদা চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন। এর কয়েক দিন পর বড়লাটের কাছে বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতাদের সর্বাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫), তাঁর সহযোগী ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯০৫), মোমেনশাহীর অনাথবন্দু গুহ, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অশ্বিনা কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), সিলেটের বিপিন চন্দ্র পাল, কলকাতার অরবিন্দু বোস (১৮৭২-১৯৫৯), আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবল বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার প্রথম দিনে ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নর্থব্রুক হলের সভাস্থলে মিলিত হয়ে যখন নতুন প্রদেশের উন্নয়নে তাঁদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কলকাতার চেহারা সেদিন সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেনঃ
“১৬ আক্টোবর এদের কর্মসূটির মধ্যে ছিল ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখী বন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগ-জর্জর আনন্দমোহন বসু ‘মিলন মন্দিরের’ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের জন্য ইংরেজিতে যে ভাষণ লিখে এনেছিলেন তা পড়ে শুনালেন আাশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ”।
হিন্দুদের এইরূপ আন্দোলন ব্রিটিশদের কাছে ছিল অভাবনীয়। তারা চিন্তাও করতে পারেননি সদা অনুগত হিন্দুরা একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এতটা ক্ষেপে যাবে। হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ শুধু একটাই। চিরশত্রু মুসলিমদের উপকার। এই উপকার সহ্য করতে সক্ষম ছিলো না হিন্দুরা। তাদের এই হিংসাত্মক মনোভাব বাংলার শুরু থেকে চলে আসা মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যকার বিভেদকে জাগিয়ে তুলে। রাজনীতিতে উদাসীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমগণও হিন্দুদের মানসিকতার সাথে পরিচিত হয়।
ক্রমেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বর্ণহিন্দু চরমপন্হি নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯০৬ সালে এসে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। চিত্তরঞ্জন দাসের ইঙ্গিতে অনুশীলত সমিতি এ সময় পুরাপুরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। চিত্তরঞ্জন দাসকে এসময় হিন্দুরা দেশবন্ধু উপাধি দেয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস আর স্বামী বিবেকান্দের ‘নব্য হিন্দুবাদের’ দীক্ষাপ্রাপ্ত বর্ণহিন্দুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন এবং কালী মন্দিরকে ঘিরে শক্তি সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। হিন্দুদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে উগ্রমূর্তি নিয়ে হামলা চালাতে থাকে। চরমপন্হিরা ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে নরমপন্হিদের সাথে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্ম-রাজ্যে বিশ্বাসী মারাঠা ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে ১৯০৭ সলে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে মারামারি হয়।
১৯০৭ সাল ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চরম পর্যায়। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৯১০ সালে এসে এই আন্দোলনের উম্মত্ততা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বর্ণহিন্দু লেখক, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক রচনা ও প্রচারণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সরকার বিরোধীতার সাথে সাথে মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রাখী বন্ধন, কালী মন্দীরে শপথগ্রহণ, বন্দে মাতরম স্লোগান, এমনি অসংখ্য হিন্দু আচার এই আন্দোলনের সাতে জুড়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। রাস্তাঘা্টে সর্বত্র বিদ্বেষেরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের সহপাঠি মুসলমান ছাত্রদের মুখ থেকে ‘পিয়াজের গন্ধ আসে’ বলে অভিযোগ তুলে তাদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে। ক্লাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়।
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে মুসলমাদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিল। ঐ বছরই অক্টোবরে আগা খানের নেতৃত্বে নেতৃস্থানীয় ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল বড়োলাটের সাথে সাক্ষাত করে মুসলমানের জন্যে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানান। বড়োলাট সম্মত হন এবং তারপরও বহু চাপ সৃষ্টির ফলে এবং সৈয়দ আমীর আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ‘মুসলিম লীগ’ এবং মুসলমানদেরজ জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা –এ দুটি অর্জন সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে সন্ত্রাসবাদী ও ‘স্বদেশী’ আন্দোলন একসাথেই সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
সন্ত্রাসীদের প্রথম লক্ষ্য ছিলো বঙ্গভঙ্গ বানচাল করা। দ্বিখন্ডিত ‘বাংলা মা’কে পুনর্জীবিত ও সন্তুষ্ট করার জন্যে মানুষের মারণাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। বোমা বিস্ফোরণে সরকারি অফিস আদালত ধ্বংস করা, সভা সমিতি বানচাল করা, খুন জখম, লুটতরাজ প্রভৃতি চলতে থাকলো পূর্ণ উদ্যমে। মেনিদীপুরের ক্ষুদিরাম ও বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ডে আত্মনিয়োগ করলো। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কেউ সমর্থন না করলে তার আর রক্ষা ছিল না। গুন্ডামী ও হত্যাকান্ডের সমালোচনা করলেও তার মুণ্ডুপাত করা হতো। এ কারণে জনৈক হিন্দু সরকারী উকিলকে ১৯০৯ সালে গুলী করে হত্যা করা হয়। ১৯১০ সালে ডিএসপি শামসুল আলমকেও হত্যা করা হয়। বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নরকে চারবার আক্রমণ করা হয়। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেনের উপর হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়।
বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসবাদীরা ছিল খড়গহস্ত। আবার নিরীহ ও সরলপ্রকৃতির কিছু মুসলমানদেরকে তাদের আন্দোলনে ভিড়াবার জন্যে হিন্দুরা অন্যপথ অবলম্বন করলো। ‘বংগভংগের ইতিকথায়’ ইবনে রায়হান বলেন, হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হিন্দু মুসলিম দুটি প্রাণ তথা দুই বাংলার মিলনের প্রতীক রাখী বন্ধনী পরিয়ে দিত মুসলমানদের হাতে, তাদের হৃদয় মন জয় করার জন্যে চারদিকে হতে ভেসে আসতো সুললিত কন্ঠের সুমধুর সুর-
বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।
এভাবেও কিছু মুসলিম বিভ্রান্ত হয়েছিল। তবে যখন কালী মন্দিরে শপথ নেয়া শুরু হয়েছে এবং মুসলিম ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা শুরু হয়েছে তখন ফিরে এসেছে। বোমা হামলা করার জন্য সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়া হয়। অথচ এই ক্ষুদিরামকে বাংলাদেশের পাঠ্যবইসহ মূলধারার ইতিহাসে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী হিসেবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।
সন্ত্রাসবাদ, নাগরিকদের বিশেষ করে ইংরেজদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা যতোটা ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল, সম্ভবত তার চেয়ে অধিক বিব্রত করেছিল –বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জন নীতি। ম্যানচেষ্টারের কলকারখানাগুলি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ম্যানচেষ্টার চ্যাম্বার অব কমার্সের কাছে হিন্দু বণিক সমিতির পক্ষ থেকে অনবরত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল, ‘যদি এ দেশে তোমাদের বস্ত্রাদি চালাতে চাও, তবে বঙ্গভঙ্গ রদ করো’।
বঙ্গভঙ্গ রদ ঠেকাবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে খাজা সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে উক্তি করেন তাতে বাংলার মুসলমানদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে অনুন্নত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে চরম আঘাত লেগেছে এবং তাদের ঘরে ঘরে বিষাদের সঞ্চার হয়েছে। বংগভংগের ফলে অনুন্নত পূর্ব বাংলা ও আসামের অবহেলিত অধিবাসীগণ যে সুযোগ পেয়েছিল এবং বিশেষ করে মুসলমানদের উন্নতির যে সুযোগ পেয়েছিল তা সহ্য করতে না পেরে বিভাগ বিরোধীরা বঙ্গভঙ্গ বানচাল করার জন্যে রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের আশ্রায় গ্রহণ করে। এতে করে ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। নবাব সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন “এতদিন সমগ্র প্রাচ্যে মনে করা হতো যে যাই ঘটুক না কেন ব্রিটিশ সরকার কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যদি কোনো কারণে এ বিশ্বাস খর্ব হয়, তাহলে ভারতে ও প্রাচ্যে ব্রিটিশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে”।