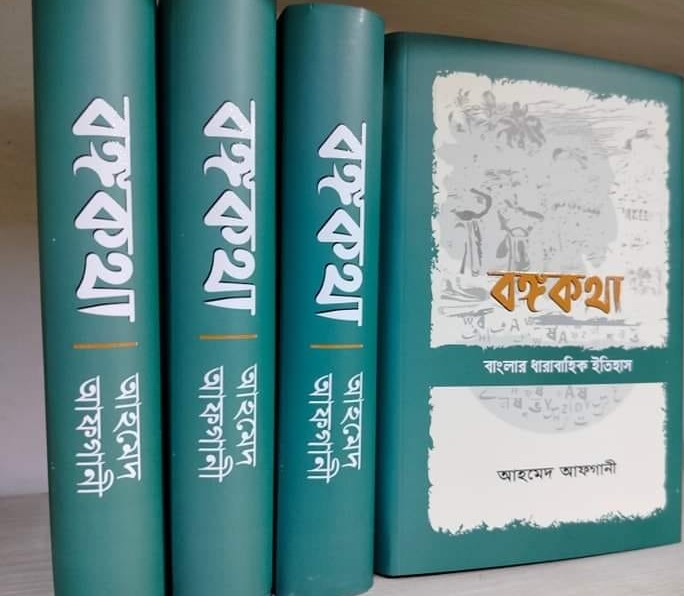খারেজি মানসিকতার কিছু মানুষের অব্যাহত প্রচারণার কারণে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফসহ কিছু আলিম বলতে চাইছেন কাউকে শহীদ বলা যাবে না। আমরা যখন শহীদ ড. হাফেয মুহাম্মদ মুরসির শাহাদাতের ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম তখন তিনি তার একটি ভিডিও বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং সেখানে বলতে চেয়েছেন শহীদ বলা যাবে না কারণ আমরা জানি না তিনি সত্যিই শহীদ হয়েছেন কিনা। এই জাতীয় আরো কিছু বক্তব্য আমরা পেয়েছি যখন এদেশের মুসলিমদের নেতা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের জালিম সরকার অন্যায়ভাবে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে খুন করেছিলো।
আসুন আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করি শহীদ মানে কী?
‘শহীদ’ আরবি শব্দ। এটি ‘শাহাদত’ শব্দ থেকে এসেছে। ‘শাহাদত’ অর্থ হলো, সাক্ষ্য, সনদ, সার্টিফিকেট, প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি। ‘শহীদের’ পারিভাষিক অর্থ হলো, ‘শহীদ ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সফলতায় তার জীবন কুরবানীর মাধ্যমে তার ঈমানের দাবি পূরণের সত্যতার সাক্ষ্য, সনদ, সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন প্রদান করলো।’
কারা শহীদ?
এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-এর থেকে জানতে থেকে জানতে পারি।
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যকার কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? তারা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয় সেই তো শহীদ। " তিনি বললেনঃ তবে তো আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হবে। তখন তারা বললেন, তা হলে তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ রাহে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ যে ব্যক্তি উদরাময়ে মারা যায় সেও শহীদ। ইব্ন মিকসাম (রাঃ) বলেন, আমি তোমার পিতার উপর এ হাদীসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আরও বলেছেন, এবং পানিতে ডুবে মারা যায় এমন ব্যক্তিও শহীদ। (মুসলিম ৪৮৩৫)
আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। (বুখারি ২৪৮০)
সাহ্ল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা’আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় ইন্তিকাল করে। (মুসলিম ৪৮২৪)
শহীদ বলার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?
আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তাদের তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেয়া হয়। (সূরা ইমরান ১৬৯)
আল্লাহ্ তায়ালা অযথা কোনো কথা বলেন না। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে জীবন দেন তখন তাঁকে মৃত মনে করা ও বলা যাবে না। এটা আমাদের প্রতি নির্দেশ। তাহলে কী বলতে হবে? এর উত্তর আমরা পাই আল্লাহর রাসুল সা. ও সাহাবীদের আমল থেকে।
সাহাবারা ও আল্লাহর রাসূল সা. যখন কোনো আল্লাহর পথে জীবন দেয়া ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলতেন তখন তাদের শহীদ হিসেবে সম্বোধন করতেন। সিহাহ সিত্তাহ'র হাদীসগুলোতে 'শহীদ' শব্দটি এসেছে প্রায় ৪০০ বারের কাছাকাছি। এর মধ্যে তিন শতাধিকবার এসেছে ঘটনা বর্ণনায়। যখনই সাহাবারা আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার ঘটনা বা যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ তখন সেখানে শহীদ হিসেবে উল্লেখ করতেন। এই থেকে আমরা সহজে বুঝতে আল্লাহর পথে জীবন দেয়া ব্যক্তিকে বলতে হবে শহীদ। যেমন ড. মুরসি শহীদ হয়েছেন। কেউ যদি বলেন ড. মুরসি মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি মৃত, তাহলে তিনি আল্লাহর প্রেরিত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক আচরণ করেছেন।
অনেকেই প্রশ্ন তুলেন তার শাহদাত কি কবুল হয়েছে? অথবা আমরা কীভাবে বলতে পারি কোন ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন? আমাদের কাছে তো ওহী নাযিল হয়নি কারো ব্যাপারে।
আমাদের করণীয় নির্ধারিত হবে আমরা যা দেখি তার উপরে। আমরা গায়েব জানিনা। কারো অন্তরের খবর জানি না। আমরা যখন দেখবো কোন ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন তখন আমরা তাকে শহীদ বলবো। আল্লাহর রাসুলের শিক্ষাই তাই। বাকী তার অন্তরের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ্ করবেন। ওটা আমাদের বিষয় নয়। যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিবেন তিনি আমাদের কাছে সাক্ষ্য হয়ে থাকবেন সেজন্যই তিনি শহীদ। তার শাহদাত কবুলিয়্যতের বিষয় আল্লাহর। আমরা সেজন্য দোয়া করতে পারি।
যারা শহীদ বলার ব্যাপারে বিরোধীতা করেন তারা কীসের ভিত্তিতে করেন?
একটি হাদীসকে পুঁজি করে তারা এসব কথা বলেন। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ওমর (রা.) আমাকে বললেন, ‘খায়বারের যুদ্ধের দিন সাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় সাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে সাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কখনো নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৩৪; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৮৫৭)।
এই হাদিসকে সামনে এনে তারা বলতে চান আপনিই বললেই কেউ শহীদ হয়ে যাবে না। এটা আমরাও মনে করি। কিন্তু রাসুল সা. আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহর পথে জীবন দেয়া লোকদের শহীদ বলতে। তাহলে এই হাদিসের কথা কেন এসেছে? এটা দ্বারা আল্লাহর রাসূল আমাদের জানাতে চেয়েছেন কোনো ব্যক্তি যদি কারো হক নষ্ট করে তবে তিনি আল্লাহর পথে জীবন দিলেও তাকে ক্ষমা করা হবে না।
এখানে দ্রষ্টব্য যে আল্লাহর রাসুল সা. শুধু একজনের ব্যপারে না করেছেন যিনি আত্মসাৎকারী। বাকীরা সবাই ঢালাওভাবে শহীদ।
এই প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস এসেছে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনু ‘আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম ৪৭৭৭)। এর মানে কোনো শহীদের কাছে যদি কারো হক থাকে তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন না। হাদীসে কয়েকটি ঘটনা এমন এসেছে কোনো ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন আল্লাহর রাসূল সা. তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন তার ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য।
আরেকটি হাদিস নিয়েও তারা কথা বলেন সেটা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামত রাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তাঁর সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ তা’আলা বলবেন, এর বিনিময়ে কি আমল করেছিলে?
সে বলবে, আমি আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য যুদ্ধ করেছি এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে তুমি বীর। তা তো বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
এই হাদিসেও স্বীকার করা হয়েছে আল্লাহর পথে জীবন দেয়া ব্যক্তি শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এটাই নিয়ম। এখানে ব্যক্তি তার অন্তরের রোগের কারণে জাহান্নামী হবে। এই হাদীস উল্লেখ করে তারা কোনো ব্যক্তিকে শহীদ বলা থেকে বিরত থাকতে বলেন অথচ একই হাদীসে আলিম ও দানশীল ব্যক্তির ব্যাপারেও সেইম কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের বলতে শুনিনি কাউকে আলিম বলা যাবে না বা দানশীল বলা যাবে না।
আবু বকর জাকারিয়াসহ কিছু আলিম বলেছেন, তাকে শহীদ বলা যাবে যার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তাকে আল্লাহ শহীদের মর্যাদা দিয়েছেন। যেহেতু আমরা কেউ নিশ্চিতভাবে জানি না তাই আমরা এভাবে বলবো আল্লাহ্ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন, ইনশাআল্লাহ তিনি শহীদ, আল্লাহ চাইলে তিনি শহীদ। এই যে কথাগুলো তিনি বললেন, এগুলো শুনতে ভালোই মনে হয়, খারাপ কথা না। তবে এগুলো মনগড়া কথা। সহীহ হাদিসে শহীদ সম্পর্কে শত শত হাদিস এসেছে, সেখানে এই জাতীয় কথার কোনো অস্তিত্ব নেই। এসব মনগড়া কথা থেকে দূরে থাকা উচিত সবার।
সাহাবার অবলীলায় বলতেন, আমার ভাই শহীদ হয়েছেন, আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। অমুন যুদ্ধে অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। সাহাবাদের কেউ নিশ্চিত জানতেন না কে শহীদ আর কে শহীদ না। এমনকি আল্লাহর রাসূল সা.-এর ওফাত পরবর্তী ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও তারা শহীদ শব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন আলী রা.-এর সাথে খারেজীদের যুদ্ধ, আলী রা. সাথে মুয়াবিয়া রা.-এর যুদ্ধ, আলী রা. এর সাথে আয়েশা রা.-এর যুদ্ধ ইত্যাদি।
শুধু সাহাবারা নন, ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুগেই আল্লাহর পথে জীবন দানকারীকে অবলীলায় নিঃসংকোচে শহীদ বলা হয়েছে। অতএব এই নিয়ে বিভ্রান্তির কিছু নেই। যিনি আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তাকেই আমরা শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করবো, স্বীকৃতি দেব যদি তিনি কারো হক আত্মসাৎ না করেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।