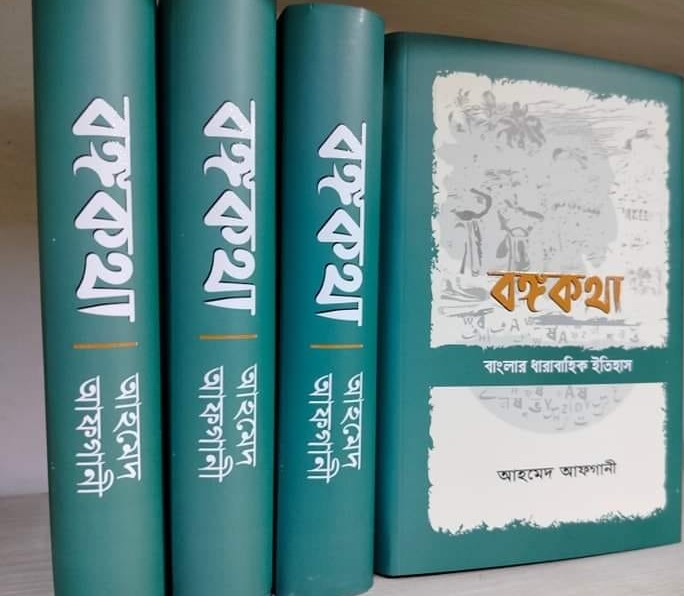১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক ভারত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটি স্থায়ী ছিল ১৭ দিন। কাশ্মীরসহ নানা ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারতের বন্ধু রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং একটা চুক্তি হয়, যা তাসখন্দের চুক্তি বলে অভিহিত। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ও সাধারণ জনগণ এই চুক্তি মানে নি। এটা ছিল সূবর্ণ সুযোগ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের। কিন্তু আইয়ুবের কূটনৈতিক ব্যর্থতায় তা হলো না। ক্ষেপে উঠে রাজনীতিবিদেরা ও পাকিস্তানী জেনারেলরা। আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো জোট গঠনের চেষ্টা করে। এতে নেতৃত্ব দেয় মুসলিম লীগ। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী লাহোরে সেই মিটিঙে আরো অংশগ্রহন করে আওয়ামীলীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী। আওয়ামীলীগের পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারী মুজিবকে সেই সম্মেলনে এটেইন করার জন্য বলেন নিখিল আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান।
মুজিব প্রথমে নিজে সেই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে চান নি। কারণ তিনি কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কনসার্ন ছিলেন না। তিনি শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলকে প্রস্তুত করেন। কিন্তু হঠাত কোনো কথাবার্তা ছাড়া শেখ মুজিব নিজেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই। শাহ আজিজের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে নয়, নিজের ইচ্ছেমতো কয়েকজনকে নিয়ে যান লাহোরে তাসখন্দ চুক্তি ও কাশ্মীর নিয়ে পর্যালোচনার জন্য।
সেই সম্মেলনের এজেন্ডায় মুজিব ৬ দফা ঘোষনার বিষয়টি যুক্ত করার আহ্বান জানান। কিন্তু অন্যান্য বিরোধী দল তা মেনে নেন নি। তারা বলেন, আমরা আজ একত্রিত হয়েছি কাশ্মীর, তাসখন্দ ও আইয়ুব খান কে নিয়ে। ফলে মিটিঙের কার্যসূচী থেকে ছয় দফা বাদ পড়ে। মুজিব সভাস্থল ত্যাগ করে। মজার বিষয় হল নিখিল পাকিস্তানের আ. লীগ প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এতে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এই ছয় দফা নিয়ে আ. লীগে ভাঙ্গন দেখা দেয়। শুধু তাই নয় যারা সেই মিটিঙে আ. লীগের অন্যান্য নেতা যারা মুজিবের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তারাও আগে থেকে কিছুই জানতেন না ৬ দফার ব্যাপারে।
দুঃখজনক ও বিস্ময়কর হলেও সত্য মূলত এই ছয় দফার কারিগর ছিলেন আইয়ুব খান। কারণ তিনি চেয়েছিলেন সেনা অফিসার ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি তাসখন্দ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে। এবং ৬ দফার বিরোধী হয়ে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বজায় রাখতে সবাই যেন তার হাতকেই শক্তিশালী করে। পরিশেষে কিন্তু তাই হয়েছিলো। আইয়ুব ৬ দফাকে হাতিয়ার করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আইয়ুব তথ্য সচিব আলতাফ গওহরকে দিয়ে ৬ দফা প্রনয়ন করেন। আলতাফ সাহেব কর্মসূচীটি রুহুল কুদ্দুসকে দেন। রুহুল কুদ্দুস ছিলেন মুজিবের ইনার সার্কেল। তিনি সেটা কৃষি ব্যংকের এম ডি খায়রুল বাশারকে দিয়ে টাইপ করিয়ে বিমানে উঠার আগ মুহুর্তে মুজিবের হাতে গুঁজে দেন।
বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে এই কারণে যে, আলতাফ গওহর পাকিস্তানের সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে নির্দেশ দেন এই মর্মে যেন তারা ৬ দফার বহুল প্রচার করে। এভাবেই ছয় দফা আলোচিত হয়। নতুবা বিরোধীদের মিটিঙে যেই ছয় দফা নিয়ে কোন আলোচনাই হয় নি সেই ছয় দফা নিয়ে মাতামাতি করার কোন কারণ নেই। লাহোরে ৫ তারিখ ৬ দফা উত্থাপন না করতে পেরে মুজিব ১০ ফেব্রুয়ারী সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে পত্রিকাগুলো আরো রসদ পায়। মানুষ ভুলে যায় তাসখন্দ কিংবা কাশ্মীর সমস্যা। রাজনীতিবিদ ও সামরিক অফিসারদের মাথা ব্যাথার কারণ হয় ৬ দফা। একবার আইয়ুব ভারত বিরোধীতাকে পুঁজি করে যুদ্ধ লাগিয়ে সবার সমর্থন নিজের দিকে নিতে চেয়েছিলেন। কূটনীতিক ব্যর্থতায় সবার সমর্থন হারিয়ে এবার ছয় দফাকে পুঁজি করে আবার পরিস্থিতি তার দিকে নিতে চেয়েছিলেন।
এদিকে মুজিবের অবস্থাও ভালো নয়। আওয়ামী লীগের অধিকাংশই ৬ দফা মানে নি। দফা গুলোর সাথে তাদের বিরোধ না হলেও তাদের মূল বিরোধ মুজিবকে নিয়ে। মুজিবের কারো সাথে পরামর্শ না করে এরকম স্বৈরাচারী টাইপের ঘোষণা কেউ মেনে নিতে পারে নি। ১৯৬৬ সালের ১৮-১৯ মার্চ ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয়। এতে অন্যান্য মেম্বার সহ লীগ সভাপতি আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের প্রবল আপত্তির মুখে মুজিব ছয় দফা পাশ করাতে ব্যর্থ হয়। এর মাধ্যমে ছয় দফার সাথে আ. লীগের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। হতাশ মুজিব তার শেষ অস্ত্র ছাত্রলীগকে ব্যবহার করেন।
এই প্রসঙ্গে সাবেক মন্ত্রী ও তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন। দুঃখভরা মন নিয়ে শেখ মুজিব আমাদের(ছাত্রলীগ) ডাকলেন। বললেন, আমি তো বিপদে পড়ে গেছি। আমারে তোরা কি সাহায্য করবি না? ছয় দফা বলার পর থেকেই বিভিন্ন দিক থেকে আমার অপর এটাক আসছে। আমার তো এখন ঘরে বাইরে শত্রু। আমরা তখন বললাম নিশ্চয়ই আপনার পাশে থাকবো। যাই হোক ফ্যসিবাদী মুজিব ছাত্রলীগের গুন্ডাদের সহযোগিতায় সভাপতি তর্কবাগীশকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। এরপর মুজিব নিজের পক্ষের লোকদের নিয়ে কাউন্সিল করেন। এবারের কাউন্সিল সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি করা হয় শেখ মুজিবকে। এরপর শেখ মুজিব ছয় দফার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান। অন্যদিকে আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আরেকটি ধারা চালু থাকে। তবে যেহেতু সেই আওয়ামী লীগের আলাদা কোনো কর্মসূচী ছিল না, তাই তারা তৃণমূলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি।
এভাবেই আইয়ুব-মুজিব ষড়যন্ত্রে নষ্ট হয়ে যায় কাশ্মীরের মুসলমানদের ভাগ্য। হয়তো তখন পাকিস্তানী জেনারেলরা তাসখন্দ চুক্তিকে বাতিল করে ভারতকে চাপ দিয়ে কাশ্মীর নিয়ে আরেকটি সমাধানে পৌঁছাতে পারতো। কিন্তু ছয় দফাকে সরকার গুরুত্বপূর্ণ করে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখাকে জোর দেয়। পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে ইচ্ছেকৃত সমস্যা তৈরি করে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য বিনষ্ট করার মাধ্যমে নিজের হাতকেই শক্তিশালী করে আইয়ুব। অন্যদিকে চোখের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায় কাশ্মীর ইস্যু।
ড: আনিসুজ্জামান এই প্রসঙ্গে বলেন,
"ছয় দফার প্রণেতা কে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন সিভিল সার্ভিসের কয়েকজন সদস্য এটা তৈরি করে শেখ মুজিবকে দিয়েছিলেন, কেউ কেউ সে কৃতিত্ব কিংবা দোষ দিয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিককে। তাদের পেছনে কোন শক্তি কাজ করছিল, সে বিচারও হয়েছিল। প্রথমে উঠেছিল ভারতের নাম। কিন্তু পাকিস্তান হওয়া অবধি তো দেশের বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ভারতের প্ররোচনা বলে। পরে বড়ো করে যে নাম উঠলো, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব এবং ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্টের বন্ধুত্বের কারণে পাকিস্তান ভাঙার উদযোগ নিচ্ছে মার্কিনরা, এমন একটা ধারণা খুব প্রচলিত হয়েছিল।
আমরা যারা একটু বামঘেঁষা ছিলাম, তারা এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলাম। ফলে, ফেডারেল পদ্ধতি ও স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষপাতী হলেও ছয় দফাকে আমরা তখন গ্রহণ করিনি। আমরা আরো শুনেছিলাম যে, পাকিস্তান ভাঙতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি করতে দেওয়া হবে; সুতরাং এ কাজে মার্কিনদের উৎসাহ তো থাকবেই। যদি প্রশ্ন উঠতো যে, পাকিস্তান তো সেনটো-সিয়াটোর সদস্য, তাহলে জবাব পাওয়া যেতো যে, পাক-ভারত যুদ্ধের পরপ্রেক্ষিতে ওসব জোটের অসারতা প্রমাণ হয়ে গেছে এবং পাকিস্তান যে কোন সময় তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। পাকিস্তান কখনোই এসব সামরিক জোট ছাড়েনি, তবে আইয়ুব খানের ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্সে’র প্রচারিত নীতি কিছুটা এ ধারণাকে পুষ্ট করেছিল।”
আওয়ামী লীগ নেতা ও শেখ মুজিবের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা আতাউর রহমান খান (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) ছয় দফা নিয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত বলেন। তার ভাষ্যমতে,
//(তাসখন্দে) কয়দিন আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী একটি যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সিদ্বান্ত হল, শান্তিপূর্ণভাবে উভয় পক্ষ নিজেদের ছোট বড় সমস্যার সমাধান করবে। আশ্চর্যের কথা, যা নিয়ে যুদ্ধ, অর্থাৎ কাশ্মীর, তার নামগন্ধও এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রইল না। এত কান্ড করে, এত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, সারা পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত হল, ওম্ শান্তি।
পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য শহর বাজার গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেরা সৈনিক নিহত হয়েছেন। পৃথিবীর কোন যুদ্ধে নাকি এত অল্প সময়ে এত অফিসার নিহত হয় নাই। তাদের স্থান পূরণ সম্ভব হবে না। তাই, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিরুপ ছিল। এত ক্ষয়ক্ষতির পর আয়ুব খাঁ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে অপমান-জনক একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এই চুক্তি অপরাধ স্বীকৃতির শামিল বলে তারা মনে করে।
যে সব সৈনিক কর্মচারী শহীদ হয়েছেন তাদের বিধবা স্ত্রী ও পরিবারবর্গ এক মিছিল বার করল লাহোর শহরে। ধ্বনি তুলল, আমাদের স্বামী পুত্র ফেরত দাও। তারা শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নাই। অনর্থক আপনি তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন। অকারণে তাদের অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। যদি দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য হতো, তা হলে আপনি এমন চুক্তি কেন স্বাক্ষর করলেন? ইত্যাদি –
পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ-ছয় তারিখে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করলেন। এই উপলক্ষে চৌধুরী মহম্মদ আলি ও নবাবজাদা নসরুল্লাহ খাঁ ঢাকা এসে সব দলের সাথে আলাপ আলোচনা করে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। বললেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক এই মূহুর্তে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।
জামাত, নিজামে ইসলামীও কাউন্সিল লীগ যোগদানে সম্মতি দিল। আওয়ামী লীগেরও দোমনাভাব। শেখ মুজিবের মতামতই দলের মত। প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন অভিমত নাই। শেখ মুজিব কনফারেন্সে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এন-ডি-এফ সভা করে মত প্রকাশ করল যে, কনফারেন্সের পক্ষে আমাদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে, তবে বর্তমান অবস্থায় কোন সদস্য এতে যোগদান করতে পারছেনা। শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোনে বললেন, আপনারা ঠিকই করেছেন। আমরাও যাবনা।
পরদিন সংবাদপত্রে দেখি, শেখ মুজিব সদলবলে লাহোর যাচ্ছেন। প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন এক দলে। ব্যাপার কি? হঠাৎ মত পরিবর্তন। মতলবটা কি?
লাহোর কনফারেন্স শুরু হল গভীর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে।
অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ একটি বোমা নিক্ষেপ করলেন – ‘ছয় দফা’। প্রস্তাব বা দাবীর আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হল। কোন বক্তৃতা বা প্রস্তাব নাই, কোন উপলক্ষ নাই, শুধু কাগজ বিতরণ। পড়ে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয় কনফারেন্সে এই দাবী নিক্ষেপ করার কি অর্থ হতে পারে? কনফারেন্স ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে। এই দাবী যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, এই সম্মেলন ও এই সময় তার উপযোগী নয় – সম্পূর্ণ অবান্তর।
তারপর দলবলসহ শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে এসে মহাসমারোহে ‘ছয় দফা’ প্রচার করলেন সংবাদপত্রে। শেখ মুজিবের দাবী ও নিজস্ব প্রণীত বলে ছয়-দফার অভিযান শুরু হয়ে গেল।
ছয় দফার জন্মবৃত্তান্ত নিম্নরুপ : কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল লোক দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরাবস্থার কথা আলাপ আলোচনা করেন। আমাদের ইঙ্গিত ও ইশারা পেয়ে তারা একটা খসড়া দাবী প্রস্তুত করলেন। তারা রাজনীতিক নয় এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টও নয়। তারা ‘সাতদফার’ একটা খসড়া আমাদের দিলেন। উদ্দেশ্য, এটা স্মারকলিপি হিসাবে আয়ুব খাঁর হাতে দেওয়া, কিংবা জাতীয় পরিষদে প্রস্তাবাকারে পেশ করার ব্যবস্থা করা।
এই খসড়ার নকল বিরোধীদলীয় প্রত্যেক নেতাকেই দেওয়া হয়। শেখ মুজিবকেও দেয়া হয়। খসড়া রচনার শেষ বা সপ্তম দফা আমরাও সমর্থন করি নাই। শেখ মুজিব সেই দফা কেটে দিয়ে ছয়দফা তারই প্রণীত বলে চালায়ে দিল। তারপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ছয় দফার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক মর্ম ও তাৎপর্য লেখায়ে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজী ও বাংলায় মুদ্রিত হয়ে পুস্ত্কাকারে প্রচারিত হয় সারা দেশব্যাপী।
লাহোর কনফারেন্স বানচাল হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকেই এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেন। তারা অভিযোগ করেন, শেখ মুজিব সরকার পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে এই কর্ম করেছেন। লাহোরে পৌঁছার সাথে সাথে আয়ুব খাঁর একান্ত বশংবদ এক কর্মচারী শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে কি মন্ত্র তার কানে ঢেলে দেয় যার ফলেই শেখ মুজিব সব উলটপালট করে দেয়। তারা এও বলে যে আওয়ামী লীগের বিরাট বাহিনীর লাহোর যাতায়াতের ব্যয় সরকারের নির্দেশে কোন একটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহন করে। আল্লাহ আলীমূল গায়েব।//
ছয় দফায় করা দাবিসমূহ নিম্নরূপ :
১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;
২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;
৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;
৪. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে;
৫. দুই অংশের মধ্যে দেশিয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যেকোন বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে।
৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।
১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ ঢাকায় আইয়ুব খান ছয় দফাকে উদ্দেশ করে বলেন, দেশের অখণ্ডতাবিরোধী কোনো কিছু সহ্য করা হবে না। প্রয়োজনে অস্ত্রের মুখে তার জবাব দেওয়া হবে। এর মধ্যে আইয়ুব কয়েকবার শেখ মুজিবকে এরেস্ট করেন এবং ছেড়ে দেন। আইয়ুব ও শেখ মুজিবের মধ্যে পারস্পরিক হুমকি ও উত্তপ্ত কথাবার্তা ছয় দফাকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। এদিকে তর্কবাগীশের নেতৃত্বে থাকা আওয়ামীলীগ দিন দিন জনপ্রিয়তা হারায়। অন্যান্য বিরোধীদলগুলোও কোনো ভালো কর্মসূচি দিতে পারে নি।
এদিকে মুজিবের ছয় দফাকে কেন্দ্র করে নতুন করে স্বপ্ন দেখে আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা গোপন সংগঠন নিউক্লিয়াস ও বামপন্থী দলগুলো। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে যতগুলো কর্মসূচি (হরতাল, বিক্ষোভ, জ্বালাও-পোড়াও, ও অবরোধ) হয়েছে তাতে নিউক্লিয়াস সদস্য ও কম্যুনিস্টদের খুবই একটিভ দেখা গিয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম কায়েম করা। এক্ষেত্রে তারা মুজিবের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও ছয় দফাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলো। এভাবে আইয়ুব-মুজিব ষড়যন্ত্রে রাজনৈতিক দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয়া ছয় দফার পক্ষে জনমত তৈরি হয়েছিল।